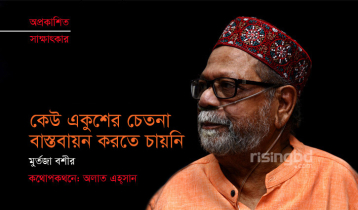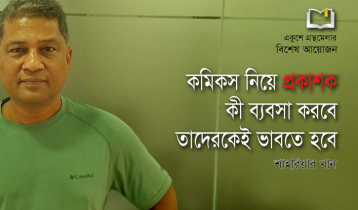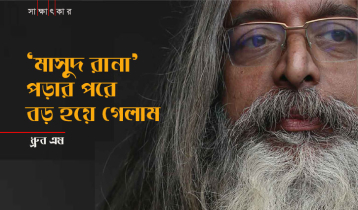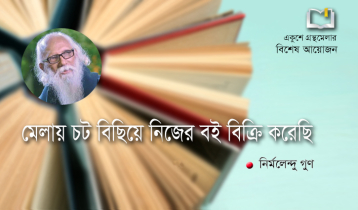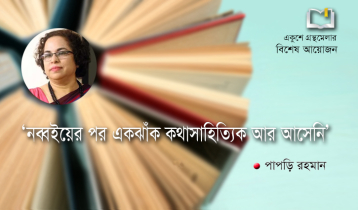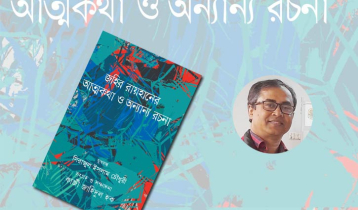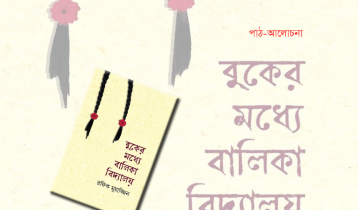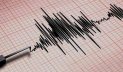পরিচয় || আফসানা বেগম

অলংকরণ : অপূর্ব খন্দকার
মাঠের শেষ প্রান্তে ফ্যাকাশে ধূসর সিমেন্টের দেয়ালে একটি মেয়ে গোবরের বৃত্ত বসিয়ে দেয়ায় ব্যস্ত। এলোমেলো বেড়ে ওঠা ঝোঁপের পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখে আরিয়ান। ডালা থেকে গোবর নেয়ার সময়ে কিছুটা সময় নেয় সে। প্রতিটা বৃত্তকে মনমতো সমান আকৃতি দিতে গিয়ে হয়তো তাকে কিছুটা ভাবতে হয়, হাত দিয়ে দাঁড়িপাল্লার মতো খানিক ওজনও নিতে হয়। তারপর একসময় থপ করে একটা শব্দ হয় আর দেয়ালের গায়ে গোবরের বৃত্তটি মাধ্যাকর্ষণের সূত্রকে অবজ্ঞা করে আটকে থাকে। ভালো করে তাকালে দেখা যায় তরতাজা বৃত্তের তলে অতীতের বৃত্তের চিহ্ন, জলপাই রঙের ছোপের নিচের ছোপগুলো ক্রমশ কালচে। একের ওপরে আরেক বৃত্তের ছাপ দেয়ালজুড়ে, যেন অলিম্পিকের অসংখ্য মনোগ্রাম।
আরিয়ান কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে তার কাজ দেখে। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বলে মেয়েটি আরিয়ানের উপস্থিতির কথা জানতে পারে না। তারপর কিছু একটা নিতে বা কাউকে ডাকতে মেয়েটি ফিরে তাকায়। তার চিরচেনা গ্রাম্য পরিবেশের মাঝখানে আপাদমস্তক অন্য চেহারা আর অভূতপূর্ব পোশাকে আরিয়ানকে দেখে তার মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। হাতে একতাল গোবর নিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে থাকে। কেউ একটানা সরাসরি তাকিয়ে থাকলে বিব্রত হওয়াই স্বাভাবিক। আরিয়ান যেখান থেকে এসেছে, সেই সিডনি শহরে কেউ কারো দিকে সরাসরি তাকায় না। সরাসরি তাকিয়ে কাউকে লক্ষ্য করা খুবই অভদ্রতা সেখানে। সোজাসুজি চোখ পড়ে গেলে হাসিমুখে ‘হ্যালো’ বলার নিয়ম হলেও, এমনিতে কারো চোখে চোখ না ফেলে আশপাশে তাকানোই ভদ্রতা। একবার শপিং মলের ফুড কোর্টে তীব্র এক চড়ের শব্দে আরিয়ান খাবার মুখে নিয়ে চমকে তাকিয়েছিল শব্দের উৎসের দিকে। এক লোক তার বউ কিংবা সঙ্গীর গালে কষেছিল এক চড়। ঘটনা বুঝতে হয়তো দু-তিন সেকেন্ড সময় লেগে গিয়েছিল আরিয়ানের। তারই মধ্যে বিশালাকৃতির লোকটি সামনের মেয়েটির ওপর থেকে রাগি চোখ সরিয়ে আঙুল উঁচিয়ে আরিয়ানের ওপরে চড়াও হয়েছিল, ‘হেই মাইট, হোয়াটস ইয়োর প্রবলেম?’ আরিয়ান না শোনার ভান করে শক্ত ফ্রেঞ্চ রুটিতে যত্ন করে কামড় বসিয়েছিল তখন।
গোবর মাখানো হাত ঝুলতে থাকা মেয়েটির স্থির চোখ আরিয়ানের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাগপ্যাকের বেল্টটা ঘাড়ের ওপরে খানিকটা ভালোমতো বসিয়ে ঘুরে যেতে চায় সে। আবার ভাবে এই মেয়েকেই তো জিজ্ঞাসা করা যায়। তবে পথে মানুষের মুখে মুখে দিকনিশানা যতটুকু জানা হয়েছে, তা এই জায়গাটিই হবার কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার আগমুহূর্তে তার চোখ পড়ে গোবর বৃত্তের ছাপ পড়া দেয়ালটার ওপরের দিকে, যেখানে হয়তো মেয়েটির হাত পৌঁছে না বলে বৃত্তের ছাপ পড়েনি। জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট খসা দেয়ালটায় নামটা ঠিকঠাক লেখা আছে, ঠিক যে নকশায় আরিয়ান ওই নামটা দেখেছে আগে। বর্ণগুলো তার অচেনা, তাই ওসব পড়া অসম্ভব তার জন্য। তবে বাবার ড্রয়ার থেকে আনা ডায়রিতে ঠিক এভাবেই লেখা ছিল নামটা; একই নকশা। আরিয়ান মেয়েটির তীক্ষ্ম দৃষ্টির কথা বেমালুম ভুলে সেখানেই মাটিতে নামায় ঘাড়ের ব্যাগটা। দ্রুত হাতে চেইন খুলে বের করে আনে বাবার পুরোনো ডায়রি। তারপর প্রথম পাতাটা খুলে এগিয়ে যায় দেয়ালের দিকে। হ্যাঁ, হুবহু এক নকশা, একই হরফ পাশাপাশি। নামের আগে বসানো দুটো শব্দ বাদ দিয়ে আরিয়ান পড়ার ভঙ্গি করে স্মৃতি থেকে বলে, ‘মতলুব খন্দকার’! গোবরের ডালাটা আরিয়ানের পায়ের পাশ থেকে সামান্য সরিয়ে মেয়েটি অবাক হয়ে তাকায়, ‘হ, মতলুব খন্দকার, তাত কী হইছে?’
‘কী হইছে মানে? এটা কি তার মন্যুমেন্ট না?’
কিশোরী মেয়েটি আরিয়ানের চেয়ে ছোটই হবে। আরিয়ানের অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণঘেঁষা বাংলা সে বুঝতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু আরিয়ান মেয়েটির উত্তরবঙ্গীয় টান মোটামুটি বুঝে ফেলে। ছেলেবেলায় বাবা আরিয়ানকে কাঁধে তুলে বাসার লনে হেঁটে বেড়াত আর আরিয়ানের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলতে থাকত। আরিয়ান নিজে কখনো চেষ্টা করেনি কিন্তু দিনের পর দিন শুনতে শুনতে ভাষাটার ব্যাপারে একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই।
‘কী মেন্ট কন জানো না। এইটা মোর নানার দেয়াল আর মুই অ্যাটে ঘসি বানাইতেছোঁ।’
‘ঘসি মানে?’
‘চুলা ধরাই হামরা উয়্যাক দিয়া।’
স্কুলে গরু এনে দেখানো হয়েছিল বলে আরিয়ান গোবরের সঙ্গে পরিচিত। বলা হয়েছিল তা একরকম জ্বালানি। তখন আরিয়ানের মাথায় বায়োগ্যাসের ভাবনা এসেছিল ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে গোবর মাখামাখি করে দেয়ালে বৃত্ত সাঁটানোর বিষয়টা তার মাথায় ঢোকে না। সে সেটা নিয়ে ভাবতেও চায় না, বরং এগিয়ে গিয়ে দেয়ালটার উঁচু অংশে কী লেখা থাকতে পারে সেটা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়। মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। ডায়েরির সঙ্গে নাম মেলানো দেখে বলে, ‘কাক খোঁজেন তোরা? মোর নানা মতলুব খন্দকার সেই কোন দিনত মলছে। মুই দ্যাখোয় নাই তাক।’ আরিয়ান মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে আবারো ডায়রি দেখে কিছু মেলাতে চেষ্টা করে। মেয়েটি তখন আরিয়ানের পড়ার চেষ্টা বুঝতে পারে। কাছে এসে প্রায় মুখস্থের মতো করে বলতে থাকে, ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা মতলুব খন্দকার। জন্ম: ৬ আগস্ট ১৯৩০, মৃত্যু: ১০ সেপ্টেম্বর ২০০১, রংপুরের পীরগঞ্জ এলাকায় তিনি বীরত্বের সঙ্গে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভ... আচ্ছা, তোমরা কারা, বাহে? অ্যাটে আলছেন ক্যান?’ গম্ভীর স্বরে আর অশুদ্ধ উচ্চারণে লেখাগুলো পড়তে গিয়ে মেয়েটি থামে। তার কৌতূহল হয়তো তাকে থামিয়ে দেয়। নিশ্চিত হওয়ার পরে আরিয়ানও ঘুরে দাঁড়ায়, ‘মে আই আস্ক হোয়াই আর ইউ মেসিং আপ মাই গ্র্যান্ডপা’স মন্যুমেন্ট?’
মেয়েটি বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থাকে। প্রায় পচা গোবরের গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তও লাগে আরিয়ানের। তাই গলায় খানিকটা রাগ উঠে আসে, ‘আরে, বলছি যে তুমি আমার দাদার মন্যুমেন্টে কাউ ডাং লাগাও কেন?’
মেয়েটি বিস্ময় থেকে বেরিয়ে এসে একটু হাসে। এতক্ষণে হয়তো আরিয়ানের প্রশ্নটা পরিষ্কার হয় তার কাছে। হাজার হলেও ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়া আছে তার। কাউ ডাং যে গোবর, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। লজ্জিত হয়ে বলে, ‘কী করিম, ভাইজান, অ্যাটে হামার আর দেয়াল নাই যে!’ কথা বলতে বলতে তার সামনের দিকের বাড়িতে ইশারা করে মেয়েটি। স্তম্ভের পেছনের দিকের বাড়িটাতে চোখ যায় তখন আরিয়ানের। টিন আর বাঁশের বেড়া দিয়ে বানানো কিছু ঘরসহ উঠোন দেখা যায়। টিনগুলো জায়গায় জায়গায় জং ধরা আর বেড়াগুলো কালচে আর জীর্ণ। আসার পথে এরকম আরো কিছু বাড়ি না দেখলে তার পক্ষে বোঝা কঠিন হতো যে এই বাড়িটা কী দিয়ে তৈরি। মেয়েটি বলতে থাকে, ‘আর দেখেন না ক্যান, ক্যাঙ্কা চনমনা রউদ আলছে অ্যাটে? সূয্য ডুববার আগোতে ঘসিগুলা কড়কড়া হয়া যাইবে অ্যালা।’ আরিয়ান মেয়েটির যুক্তিতে সম্মত হয়; এটা ঠিক, গোবরের ঘসি বানানোর জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা তাদের বাড়ির আশপাশে আর নেই। তাই বোদ্ধার মতো কেবল ‘হুমম’ বলে। মেয়েটি কৌতূহল রাখতে পারে না আর, ‘এইবার কন, তোমরা কেটা, বাহে? আমার নানাক দাদা কইতোঁছেন ক্যান?
আরিয়ান সেই গোবরমাখা দেয়ালটার দিকেই তাকিয়ে থাকে। যেন যা খুঁজতে এসেছিল তা পাওয়া হয়ে গেছে। দেয়ালটা ছয়-সাত ফুট উঁচু, একদিকে সোজা উঠে গেছে, আরেকদিকে কিছু ইট না দিয়ে এখানে ওখানে ফোকর তৈরি করা হয়েছে, জানালার মতো। আরিয়ানের মনে পড়ে বাবাকে বারকয়েক গুনগুনাতে শুনেছিল, সবকটা জানালা খুলে দাও না... মার্চ আর ডিসেম্বর মাস এলে বাবার এই গান গাওয়া বেড়ে যেত। অথচ এই গান বা মার্চ কি ডিসেম্বর, কিছু নিয়েই বাবা কখনো কোনো গল্প বলেননি আরিয়ানকে এই মাত্র দুবছর আগে পর্যন্তও।
মেয়েটির কৌতূহল আবার মাথাচাড়া দেয়, ‘তোমরা কি সাহেব নেকি? কথা কন না ক্যান? মুই ফির ইংরাজি কবার পারোঁ না, মহা যন্ত্রণা হইল্!’
আরিয়ানের সাদাটে চামড়া মেয়েটিকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে হয়তো। ঢাকা এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে, বিশেষ করে রংপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত সে এমনিতেও খেয়াল করেছে যে আশপাশের মানুষ স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি সময় ধরে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবার কাছে শুনেছে তামাটে রঙের মানুষদের সাদা চামড়ার প্রতি দারুণ দুর্বলতা থাকে। কথা ঠিক। আরিয়ানের অতি সাধারণ চেহারা থেকে তাদের চোখ ফেরে না। এয়ারপোর্টের সব সারিতেও অতিরিক্ত খাতির।
প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো ঝুলে থাকা মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় আরিয়ান। এই মেয়েটিও তার সঙ্গে কথা বলতে না পারার ঝামেলায় ভুগছে। এত বেশি মনোযোগ আরিয়ানের পছন্দ নয়। উত্তরে সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে। আপাতত আর কোনো কথা না বাড়িয়ে কিছুক্ষণ সে চুপচাপ থাকতে চায়। তাই মেয়েটির কৌতূহল উড়িয়ে দিয়ে আশপাশে তাকিয়ে নেয় খানিক। মাঠের আরেক প্রান্তে একাকী একটা ঘর। সেদিকে কোনো মানুষ দেখা যায় না। ঘরের সামনের বারান্দায় একটা সাইনবোর্ড লাগানো, বাংলায় কী লেখা সেখানে, আরিয়ানের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু নির্জন দেখে সেখানে গিয়ে একটু বসার কথাই ভাবে সে। ক্লান্তও লাগছে খুব। ঢাকা থেকে বাসে রংপুর আর তারপর আরেক বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে মিঠাপুকুর পর্যন্ত পৌঁছাতেই অনেক ধকল গেছে। এরপর মিঠাপুকুর পেরোতে কেবলই ধুলো। রাস্তাগুলো ঠিক রাস্তা নাকি পানি শুকিয়ে যাওয়া নদী, বোঝার উপায় নেই। বড় বড় গর্ত পেরোতে গিয়ে যতবার রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করেছে চৌপথি কোনদিকে, সে-ই সহজভাবে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলেছে, ‘বগলোতে’। বাবা একবার এক গল্প বলেছিল আরিয়ানকে। এই এলাকায় একজনের বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দুই ঘণ্টা ধরে বাবা কেবল শুনেছিল, ‘বগলোতে’। তাই ঘণ্টা দেড়েক সেটা শুনে সে বিরক্ত বা বিস্মিত হয়নি। তার কেবল মনে হয়েছে, মিঠাপুকুরের শুধু বগল কেন, হাত বা হাঁটুও ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে।
নির্জন ঘরটির বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসার পরে শান্তিমতো শ্বাস ফেলতে পারে আরিয়ান। শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের ওপরে ব্যাগপ্যাকটা নামিয়ে পানির বোতল বের করে। ঢক ঢক করে পানি খেয়ে ভালো করে চারদিকে তাকায়। মাঠের একদিকে বাড়িঘর, আরেকদিকে আখের খেত, আর দূরে চৌপথীর মোড়টা দেখা যায়। চারটা পথ এসে ওই মোড়ে মিলেছে, যার একটা পথ ধরে আরিয়ান এসে পৌঁছেছে ওখানে। মোড়ের পাশে একটা স্কুল, স্কুলের সামনে সাইনবোর্ডে দাদার নাম সে আগেই দেখে মিলিয়ে নিয়েছে। মানুষকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছে, মুক্তিযোদ্ধা মতলুব খন্দকার হাইস্কুল। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে সকাল সকাল বাচ্চারা বুকের ওপরে বই চেপে ধরে লম্বাটে স্কুলঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। নানা রকমের চেঁচামেচিতে স্কুলের সামনের সাদা ধবধবে মাটির মাঠমতো জায়গাটা তখন ঠাসা। সবার গায়ে একই রকমের জামাকাপড় আর চোখেমুখে একই উজ্জ্বলতা। আরিয়ান তখন নিজের কথা ভাবার চেষ্টা করেছে, তিন বছর হলো স্কুল ছেড়েছে সে, তখন কি তার মুখও এমন চকচক করত? খুব ভোরে শহর থেকে দেড় ঘণ্টা দূরের এলাকা থেকে বাবার সঙ্গে স্কুলের জন্য রওনা দিতে হতো তাকে। স্কুল যাওয়া-আসার পথে গাড়িতে বসে সে খাওয়া, হোমওয়ার্ক করা থেকে শুরু করে ঘুমিয়েও নিত। স্কুলের দিকে আরিয়ান কখনোই এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে যায়নি যেমনটা যাচ্ছে এই বাচ্চাগুলো। কেন, এরা কি আরিয়ানের চেয়ে অনেক বেশি সুখী? এদের কারো কি আরিয়ানের মতো দক্ষিণ সিডনির সমুদ্রের ধারে বিশাল ম্যানশন আছে? ভাবতে ভাবতে প্রচ্ছন্ন একটা ঈর্ষাবোধ তাকে দখল করে ফেলে। তাই হঠাৎ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় সামান্য আগে দেখা চঞ্চল মুখগুলো। অথচ বারবার উঁকি দেয় স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে একজন আরেকজনকে ধাওয়া করতে করতে ছুটে আসা দুটো বাচ্চার মুখ। ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় দৌড়ের দমকে দুজনেই বুকে চেপে রাখা বইগুলো সামলাতে ব্যস্ত। স্কুলে আসা এত মজার! স্কুলে আরিয়ানেরও কখনো ভালো লাগত অবশ্য, যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে দেখত বাবা চারটি গাড়ি থেকে বেছে তার প্রিয় বিএমডব্লিউ গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আরিয়ান বলত, ‘ওহ্ ইউ হ্যাভ ব্রট মাই ফেভারিট কার!’ অথচ সেই আনন্দের মুহূর্তও কেন বাচ্চাগুলোর কলকাকলির কাছে হেরে যাচ্ছে, আরিয়ানের মাথায় ঢোকে না। যা হোক, এ রকম কোনো হতাশা আবিষ্কার করতে সে ওই চৌপথী গ্রামে আসেনি।
কিন্তু সে আসলে কী করতে এসেছে, এখানে তা-ও তার নিজের কাছে এক ধাঁধা। কী দেখতে চায়, কেন দেখতে চায়, এসব প্রশ্ন সে নিজেকেও খুব একটা ভালোমতো করেনি। কেবল একটি জিনিস তার মাথায় আসত, ফ্ল্যাশ ব্যাক। যেন এইখানে এসে দাঁড়ালেই ফ্ল্যাশ ব্যাক দেখা যাবে। কিছুদিন আগেও এ রকম কিছু দেখার কথা সে ভাবেনি, আসার উপলক্ষই তৈরি হয়নি। উপলক্ষটা শেষ পর্যন্ত এভাবে তৈরি হওয়ার দরকারই-বা কী ছিল আরিয়ান ভেবে পায় না।
...নাহ্, ওই দৌড়োতে থাকা বাচ্চাগুলোর উচ্ছলতা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না! আরিয়ান যখন ঠিক অতটুকু ছিল, মাকে শেষ দেখেছিল। শেষের দিন আর আগের দিনে অবশ্য তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। ক্রমাগত লড়তে থাকা একজন বাবা আর একজন মাকে দেখে অভ্যস্ত ছিল সে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে মনে হতো, বাড়ির ছোট ছেলেটি নয়, যেন বিরতি নিয়ে লড়াই-মঞ্চের দর্শক ফিরে এসেছে। আর বাবা তাকে নিয়ে ফিরলে ঠিক সেই বাক্য থেকেই তাদের যুদ্ধ শুরু হতো সকালে স্কুল যাবার মুখে শেষ যে বাক্য আরিয়ানের কানে এসেছিল। ছোট্ট আরিয়ানের তখন মনে হতো, যেন দুজনের হাতেই দুটো অস্ত্র তাক করা ছিল, যুদ্ধবিরতির পরে মুখোমুখি হতেই... ঠাই ঠাই ঠাই! তবে সে সময়ের যে কোনো ভালো স্মৃতিই নেই, তা নয়। কালেভদ্রে হলেও, স্বল্পায়ু গ্রীষ্মের অপ্রত্যাশিত কোনো বিকেলে দুজন মানুষ বাইরের ঝোলানো বারান্দায় বসে কফি খেত। তারপর তারা যার যার কফির মগ ধুয়ে রেখে বসার ঘরে এসে বসত। ছাদ থেকে মেঝে ছোঁয়া ভারী পরদা সরিয়ে দিলে সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া এসে পড়ত বিস্তৃত ঘরটির ঠিক মাঝখানে রাখা কালো কুচকুচে গ্র্যান্ড পিয়ানোর ওপরে। পিয়ানোর সামনের লম্বাটে টুলটাতে বসতেন মা, আরিয়ান যাকে ডাকত মামা। তারপর দক্ষ হাতের অদ্ভুত সুরের ঝংকারে ঘরটির আনাচকানাচে বাতাসের ছুটোছুটি লেগে যেত। কার্পেটের ওপরে বসে আরিয়ান লাল রঙের ফায়ার ট্রাক দিয়ে খেলত। কোনোদিন বাজনা শেষে মামা ‘হাউ ডিড ইউ লাইক ইট?’ বলে বাবার দিকে তাকাতেন। বাবা বোকা বোকা চোখ পিটপিট করে বলতেন, ‘নাইস!’
‘ওনলি নাইস?’
‘আই মিন, ভেরি নাইস!’
‘ওহ্ আই শুড নট হ্যাভ আস্কড ইউ। হোয়াট উড ইউ ফিল অ্যাবাউট ফার এলিস ফ্রম বিঠোভেন অর মুনলাইট সোনাটা ফ্রম ম্যোৎজার্ট!’ খানিক আগে ভরে থাকা সুরের ওপরে অসুরের প্রলেপের মতো মায়ের হতাশ আর রাগি কণ্ঠস্বর ঝনঝন করে বাজত ঘরটায়। বাবা আমতা আমতা করে বলতেন, ‘হোয়াই? আই হার্ড দেম সো মেনি টাইমস!’
মা তখন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বুঝিয়ে দিতেন যে এসব হুট করে শুধু শুনলেই তো আর হয় না, ছোটকাল থেকে এর মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়। না-হলে এসবের মাহাত্ম বোঝা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। বাবা যেহেতু এশিয়ার গরিব কোনো দেশের গরিব একটা পরিবার থেকে এসেছেন, তাহলে বাবা কী করে এসবের মূল্য বুঝবেন? তিনি তার মাকে ছোটবেলাতেই হারিয়েছেন, বাবা ছিল অশিক্ষিত। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে বসে কাদা ঘেঁটে তিনি বড় হয়েছেন। তাই তার পক্ষে তো এসব উচ্চমার্গের শিল্প সম্পর্কে মন্তব্য করার যোগ্যতা অর্জন করা অসম্ভব! শুনতে শুনতে বাবারও একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত। চিৎকার করে মাকে বলতেন যে তারাইবা এমন কী উচ্চবংশীয়! ইউরোপ থেকে আসা চোর-ছ্যাঁচড়ের বংশধর। এখন চোর-ডাকাতদের কাছে তাকে সংস্কৃতি শিখতে হবে নাকি! আবার উচ্চমার্গের শিল্প না বোঝার অপবাদও শুনতে হবে তাদের মুখ থেকে?
‘হোয়াট ডিড ইউ সে অ্যাবাউট মাই অ্যানসেস্টর?’
‘আই সেড দে ওয়ার এ গ্রুপ অফ থিভস।’।
মায়ের বিস্ময় আর ক্রোধ যত বাড়ত, বাবার নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরও তত গভীর হতো। আরিয়ান ফায়ার ট্রাকের চাকা ঘোরানো বাদ দিয়ে মেঝেতে বসে ব্যাটমিন্টন খেলার দর্শকের মতো যখন যে কথা বলত তার দিকে তাকাত, যেন পালকের কর্ক এ ছুঁড়ছে ওর দিকে, আবার সে প্রতিপক্ষের দিকে। এই দেখতে দেখতেই আরিয়ান বড় হচ্ছিল। তবে বেশি দিন দেখতে হয়নি। একদিন জানা গেল মামা চলে যাচ্ছেন। আরিয়ানকে কার মতো করে বড় করা হবে, এ নিয়ে দিনের পর দিন বিবাদ চলল তারপর। বাবা কী করে যেন জিতে গেল। মা বলল, ‘ফাইন! আই অ্যাম ফ্রি টু রিস্টার্ট মাই লাইফ।’ বাবা ঠোঁট উলটে জানিয়ে দিলেন এতে যে মা খুশি হবেন তা তার আগেই জানা ছিল। বাবার শেষ চিৎকার শোনা গেল, ‘গো অ্যান্ড হ্যাভ ফান।’ মা-ও ছাড়েননি। যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন যে তার জানা আছে বাবা আরিয়ানকে কেমন করে মানুষ করবেন। এশিয়ার এক গেঁয়ো মানুষের মতো রসুন দিয়ে রান্না করা তরকারি খাইয়ে আর কেবল তথাকথিত মূল্যবোধ ভালোবাসতে শিখিয়ে। যাবার আগে মা আক্ষেপও করে গিয়েছিলেন যে কদিন বাদেই আরিয়ানের শরীর আর নিঃশ্বাস থেকেও ভুকভুক করে রসুনের গন্ধ বেরোতে থাকবে।
মা চলে যাবার পরে আরিয়ানকে জড়িয়ে ধরে বাবা বারবার বলে যাচ্ছিলেন, ‘এই মহিলাকে আমি এত ভালোবাসলাম কী করে? কী ভুলে তাকে বিয়ে করেছিলাম!’ এই ঘটনার বছর তিনেক পরে বাবা নিজের গল্প শুনিয়েছিলেন আরিয়ানকে। সামান্য পড়াশোনা করার পরেই তার চোখ খুলে গিয়েছিল। কোথাও কোনো ভালো চাকরি পাচ্ছিলেন না। আরো বেশি পড়ার জন্য যথেষ্ট পয়সাও ছিল না। গ্রামে পড়ে থাকা আর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের গৌরবের ভার মাথায় নিয়ে না-খেয়ে থাকা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। কারণ তার বাবা ঘোষণা দিয়েছিলেন কোথাও তার পরিচয়ে সুবিধা নেওয়া যাবে না। চাকরি থেকে শুরু করে জীবনে যাই করুক না কেন, নিজ যোগ্যতায় করতে হবে। যে দেশে যুদ্ধের ৪৬ বছর পরেও আসল আর নকল মুক্তিযোদ্ধার নামের নিবন্ধন হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধা কোটার অধীনে হুরহুর করে মানুষ ভালো ভালো জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে, সেখানে কিনা তার বাবা সত্যিকারের আহত মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও সে সেই সুবিধা ভোগ করেননি। যুদ্ধে জয় হয়েছে সেটাই নাকি তার প্রাপ্য ছিল, তিনি তার প্রাপ্য পেয়ে গেছেন। তাই সরকারের পক্ষ থেকে অন্য কোনো সাহায্য নেবেন না। আবার ওদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই, ওই ছোট্ট জমিটুকুও কোনো প্রয়োজনে বিক্রি করা যাবে না। এই সমস্ত ফালতু আলাপের মাঝখানে আরিয়ানের বাবাকে দেশ ছেড়ে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবতে হয়েছে। কারণ বাবা জীবনে যত ওপরে উঠতে চেয়েছিলেন তা নাকি বাংলাদেশে থাকলে তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। বিশেষ করে সম্ভব হতো না প্রাচীরের মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজেরই পিতার জন্য, যা-ই করতে যাও সেখানেই বাগড়া। এই লাইনে অসততা, ওই লাইনে বিপদ, নানা রকমের সতর্কতার বিধানসহ কথায় কথায় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া আর ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণার হুমকি। এসবের মাঝখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে শখের ফটোগ্রাফি করার সুবাদে পেয়ে গেলেন এক বিরাট দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি সফরের সুযোগ। আর যায় কোথায়, পাঁচ দিনের সফর হলেও বাবাকে তিনি আগেই জানিয়ে দিলেন যে এই যাওয়াই শেষ, এই পোড়া দেশে তার কোনো দরকার নেই আর। বাবাও জবাব দিয়ে দিলেন, দেশ ছেড়ে যদি তার ছেলে যায়ই তবে যেন চিরকালের জন্য যায়। তিনি ভাববেন তার কোনো ছেলে ছিল না। জীবনের প্রয়োজনের কাছে পিতার এই মতামত থোড়াই কেয়ার করেছিলেন বাবা। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে যদি জীবনটাকে গুছিয়ে নেওয়া যায়, যত খুশি আয় করা যায়, তবে ওই ধুলোর মধ্যে ডুবে থাকা একচিলতে বাড়ি আর একরোখা পিতাকে তারইবা কী প্রয়োজন! তিনি-ও ভাববে যে তার পেছনে কিছুই ছিল না।
সিডনি শহরে পাঁচ দিনের সফর শেষ হলে দলটি দেশে ফেরত এল। বাবা ভিড়ের মধ্যে কোথাও মিলে গেলেন, কেউ জানতে পারল না। সিডনিতে আগে থেকে থাকা কিছু বাঙালির সঙ্গে সহজেই আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। লুকিয়ে থেকে এটাসেটা কাজ করে কোনো রকম চলার উপায় বাতলে দিল তারা। সেই সময়ে প্রতিনিয়ত পুলিশের ধাওয়া আর বন্দি হবার ভয় মাথায় নিয়ে রুজি-রোজগার করা কত দুঃসহ কষ্টের ছিল, বলতে গিয়ে বাবার চোখে পানি চলে এসেছিল। গ্যাস স্টেশন বা হোটেলে ঝাড়– দেওয়া থেকে শুরু করে, শপিংমলের টয়লেট পরিষ্কার করা পর্যন্ত, কোন কাজটা তিনি করেননি! অবৈধভাবে থাকার কারণে বেশি বেতনের কোনো কাজের চেষ্টাও করতে পারতেন না। আজ এটা কাল ওটা করতে করতে বাড়ি বানানোর এক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তার অধীনে কাজে লেগে গেলেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে এসে পড়া অবৈধ মানুষদের যখন বৈধতা দেওয়া হয়েছিল, সেই সুযোগে তিনিও বৈধ কাগজপত্র পেয়ে গেছেন। এই কথাটা বলতে গিয়ে বাবা ফিক করে হেসে ফেলেছিলেন। হাসি সামলে বললেন একটা ছোট্ট গল্প। বছরের পর বছর অবৈধ থাকার সময়ে রাস্তায় পুলিশ দেখলেই দূরে পালিয়ে যাওয়া বাবার নীতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন বৈধতা পেয়ে পকেটে ট্যাক্স নম্বরের কার্ড নিয়ে চলাফেরা করতেন, তখনকার কথা বলছিলেন তিনি। হাতে হটডগ নিয়ে ফুটপাতের ওপরে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাবা দেখলেন কিছুদূরে বিশাল শরীরের এক অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ সন্দেহজনকভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তাকে দেখতেই বাবা মুখের ভেতরে হটডগের টুকরোয় কামড় বসাতে ভুলে গেলেন। যেই ভাবা সেই কাজ, সত্তর কিলোমিটার গতিবেগের ব্যস্ত রাস্তা আড়াআড়ি পেরোনোর জন্য তিনি দিলেন এক ছুট। চলন্ত অবস্থায় অসংখ্য গাড়ি হর্ন বাজিয়ে রাস্তার নির্দিষ্ট গাতিপথ ছেড়ে আঁকাবাঁকা হয়ে প্রায় থেমেই গেল। তবে বাবা থামেননি, তাদের মাঝখান দিয়ে কোনো রকমে রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সেখান থেকে পুলিশকে আর দেখা যায় কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন এক পরিচিত বাঙালির সঙ্গে। অবৈধ হিসেবে থাকার সময়ে ওই বড় ভাই গোছের লোকটি দীর্ঘদিন বাবাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কলার ধরে ফুটপাত থেকে বাবাকে উঠিয়ে বললেন, ‘কী রে, এত্ত টেনশন কিয়ের?’ বাবা কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ‘ওই যে ওই দিকে পুলিশ ছিল।’
‘তো?’
‘তো আবার কী, ধরলে কী হইত কন?’
‘আরে ব্যাটা, তর তো কাগজ হইয়া গেছে গা, তুই দৌড়াস ক্যা?’
বাবা তখন পকেটের ট্যাক্স কার্ডের ওপরে হাত রেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন বড় ভাইয়ের দিকে, কোনোরকমে বলেছিলেন, ‘অভ্যাস, ভাই, অভ্যাস আর কী।’
যা হোক, বাড়ি বানানোর কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে থাকতে থাকতে সব কাজ শেখা হয়ে গেল বাবার। কিছু ট্রেনিং কোর্সও করে নিলেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে। টাকাপয়সা ধার করে নিজেই একসময় ব্যবসা শুরু করলেন। অল্প মানুষ শহরটায় তখন আর শহরের সামান্য বাইরে গেলে ছোট ছোট টিলা আর কারো হাত না-পড়া বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড়। সরকার উদার, অন্য দেশ থেকে মানুষ নিয়েই চলেছে, জন্মহার নাকি শূন্যের নিচে নেমে গেছে। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মানুষ আমদানি। অনেক বাড়ি দরকার তখন, শহরের বাইরে বহু আবাসিক প্রকল্প। বাবার জন্য কাজ পাওয়া সহজ হয়ে গেল, একের পর এক। ব্যবসার বুদ্ধি তার ভালোই ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে নিজের টাকায় বিশাল এক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি খুলে বসলেন। ধারদেনা শোধ করে একের পর এক বড় অঙ্কের ব্যবসা তখন তার হাতে। আরিয়ানের মায়ের পরিবারের নিজস্ব জায়গায় বাড়ি বানাতে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের শুরু থেকেই একটা কিছু হয়ে গিয়েছিল তাদের। তত দিনে অস্ট্রেলিয়ান কায়দার ইংরেজি আয়ত্তে চলে এসেছিল আরিয়ানের বাবার। ভাষাটা আগে জানা না থাকাতে আরো সুবিধা হয়েছিল, যা শিখেছিল তা-ই শিখেছিল অস্ট্রেলিয়ানদের মতো করে। তাই পরিচয়ের পর অল্প দিনেই বিয়ের সিদ্ধান্ত। তখন কে কাকে জানত, না আরিয়ানের মা জানত বাবার রসুনের তরকারি খেয়ে বেড়ার ঘরে কু-লী পাকিয়ে ঘুমানোর কথা, আর না তার বাবা জানত শিল্পচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ পরিবারের আদরের কন্যার শুদ্ধ জীবনধারার কথা। বছরের পর বছর সামান্য খেয়ে জীবন ধারণই যে আরিয়ানের বাবার জীবনের একমাত্র সংগ্রাম ছিল, টাই-স্যুট পরা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীকে দেখে তা কী করেইবা কেউ বুঝত। আর জ্ঞান হবার পর থেকে দামি গাড়িতে চড়ে পিয়ানোর ক্লাসে যাওয়া মেয়ের মানসিকতা ধরার সাধ্যইবা কী ছিল আরিয়ানের বাবার।
তারপরে আরো অনেক গল্প বাবা বলেছিলেন। সেসব গল্প সবই বোঝা হয়েছিল আরিয়ানের। বিশেষ করে দিনের পর দিন তুমুল ঝগড়া শোনার পরে যা হয়েছিল, তা হলো, তথ্যগুলো কেবল স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। কিশোর আরিয়ানের কাছে তা বেশ সহজ ছিল বইকি। তবে কেবল একটি বিষয় তার কাছে পরিষ্কার হয়নি, তা হলো, মুক্তিযোদ্ধা। কঠিন এ শব্দটার মানে জানতে চাইলে বাবা হেসে বলেছিলেন, ‘আরেকটু বড় হও, তারপর বুঝিয়ে বলব।’
তারপর বহু সময় পেরিয়ে গেছে। আরিয়ান যথারীতি বড়ও হয়েছে। কিন্তু বাবার আর সময় হয়নি। সেবারে মা চলে যাবার সময়ে আইন অনুযায়ী এত সম্পত্তি তাকে ধরিয়ে দিতে হয়েছিল যে আরিয়ানের বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বসেছিলেন। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে তাকে অনেক বেশি খাটতে হয়েছিল। দক্ষিণ সিডনির বিশাল বাড়ি বিক্রি করে তাদের চলে আসতে হয়েছিল উত্তর দিকের সস্তা উপশহরে। সেখানে আসাতে পরে অবশ্য ভালোই হয়েছিল। দলে দলে বাঙালি আর ভারতীয় তখন সিডনি শহরে স্রোতের মতো চলে এসে ওই দিকে সস্তায় জায়গা কিনছিল। উপশহরের বহর লম্বা হতে লাগল। একের পর এক ঝোপঝাড় বাড়িঘরের জন্য নির্ধারিত হতে লাগল। আরিয়ানের বাবার তখন গ্ল্যানফিল্ড, ইংগেলবার্ন হয়ে ম্যাকার্থার পর্যন্ত রমরমা ব্যবসা। এত ব্যস্ততার মধ্যে আরিয়ানের সঙ্গে সময় পার করা হলো কোথায়! তার জন্য কেবল তিনি যা করলেন, তা হলো, আবার দক্ষিণ সিডনির সমুদ্র উপকূলে জাহাজের ডেকের মতো বিশাল এক বাড়ি কিনে ফেললেন। আগের চেয়ে যেন আরো ভালো থাকে আরিয়ান।
ভালো সময় ফিরতেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ নিলেন। বাঙালিদের সাপ্তাহিক দাওয়াত লেগেই থাকত, বিরিয়ানি থেকে রসমালাই পর্যন্ত নিজ হাতে বানিয়ে খাওয়ানোর প্রতিযোগিতা। যাব না যাব না করেও যেতেই হতো কখনো কখনো। সে রকম এক দাওয়াতে একজনের সঙ্গে পরিচয় হতেই যন্ত্রের মতো কাজ করা মানুষটি আবেগের নদীতে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। সাদা চামড়া তো অনেক দেখা হলো, জানা হয়ে গেছে তার। বাঙালি মেয়েই আদর্শ স্ত্রী হতে পারে নিশ্চয়। মনে মনে ভাবলেন আরিয়ানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেক সম্পত্তি তো করা হলো, এখন নিজের কথা খানিকটা ভাবলে ক্ষতি কী? বিয়ের প্রস্তাব দিতে তিনি মোটেও দেরি করলেন না যেই শুনলেন মেয়েটি বিবাহবিচ্ছেদের পরে মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য কিশোরী কন্যাকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। প্রস্তাব পেয়ে পরিবারটিও ভাবার জন্য কোনো সময় নেয়নি। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে! মেয়েটি তার জীবনের দুঃসময় থেকে বেরিয়ে এল, রাতারাতি এত বড় ব্যবসায়ী আর টাকাওলার স্ত্রী হয়ে গেল আবার অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্বও পেয়ে গেল, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে নাকি? পরিবারটি আরিয়ানের বাবার আগ্রহের কাছে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল। জানাল যে এর পরে এ নিয়ে দেরি করার কিছু থাকতে পারে না।
হয়ে গেল বিয়ে। মা-মেয়েকে আর দেশে ফিরতে হলো না। ভালোই কাটল মাস দুই-তিনেক কিন্তু তারপর সেই মেয়েকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল অশান্তি। নতুন পরিবেশে মেয়েকে কিছুতেই মনমতো করে গুছিয়ে রাখতে পারলেন না তার মা। মেয়ের উটকো বন্ধুবান্ধব, মেয়ের দেরি করে বাড়ি ফেরা বা কোনোদিন না ফেরা, মুখে মুখে তর্ক করা সবই তার চোখে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মেয়ের প্রতি আরিয়ানের বাবার পক্ষপাতিত্ব তাকে আরো জ্বালিয়ে মারল। কখনো আবার তাকে মেয়ের ইচ্ছের বিরোধিতা করতে দেখলে সৎ মেয়ে বলে অনাদরের অভিযোগ আনতেও দেরি করলেন না তিনি। আরিয়ানের বাবা বুঝলেন, না তার শাসনের অধিকার আছে, না ভালোবাসার। এই সমস্তকিছুর মাঝখানে আরিয়ান কখন প্রাইমারি আর হাইস্কুল পেরিয়ে যাচ্ছিল, বাবা হয়তো খেয়ালই করতে পারলেন না।
একদিন সারা রাত বাড়ি না ফিরে তারপর দুপুর নাগাদ চুলে চার রকমের রং লাগিয়ে যখন সেই মেয়েটি বাসায় ফিরল, মেয়ের মা পরদিন তাকে নিয়ে গিয়ে ইসলামি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। হিজাব আর বোরকাই হয়ে গেল তখন মেয়েটির সব সময়ের পোশাক। ওরকম বখে যাওয়া মেয়েকে কী করে সোজা রাস্তায় আনতে হয়, তার মায়ের খুব ভালো জানা ছিল। কোনোভাবেই যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করবে কে? আর তাই, হিজাবে রংবেরঙের চুল ঢেকে মেয়েটি যখন ইসলামি স্কুলের জেলখানার মতো উঁচু দেয়ালঘেরা ইমারতে ঢুকে যেত, মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন, যাক্, এত দিনে সিডনিতে থেকে যাওয়া সার্থক হলো তার।
অথচ আরিয়ানের বাবা এই সুন্দর সমাধানটিতেও বাগড়া দিতে শুরু করলেন। ওইটুকু মেয়েকে এভাবে বোরকায় ঢেকে থাকতে হবে? কী লাভ চাপিয়ে দেওয়া ইসলামি শিক্ষায়? বড় হলে নিজেই কি সে ভালোমন্দ বুঝে নিত না? ছোট্ট মনে এত চাপ দেওয়ার কোনো মানে হয়? মেয়ের মা কয়েকবার এসব যুক্তি শুনে তুমুল রেগে গেলেন। তার উচ্চশিক্ষা আছে, দেশে বড় কোম্পানিতে চাকরির অভিজ্ঞতা আছে, নারীর অধিকার নিয়ে তিনি বরাবর সচেতন। তাই তিনি কেন নিজের মেয়ে সম্পর্কে অন্য কারো রায় মেনে নেবেন? সহজেই বলে ফেললেন, ‘আমার মেয়েকে কীভাবে লাইনে আনতে হবে তা কি আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে? আমি তো আর তোমার সাদা বউয়ের মতো ছেলে ফেলে চলে যাওয়ার মানুষ না। আমার দায়িত্বজ্ঞান আছে। আর ছেলেপেলে কী করে মানুষ করতে হয় তা তুমি কী করে জানবে? ওরকম হাভাতে পরিবারে জন্ম হলে এসব শেখার সুযোগ হয় নাকি? ওরকম গ্রামগঞ্জে তো বাপ-মায়েরা জন্ম দেওয়ার মেশিনের মতো সন্তান জন্ম দিয়েই খালাস।’
আরিয়ানের বাবার সমস্যা সেই যেখানে ছিল, সেখানেই এসে দাঁড়াল আবার। তবে আগেরবার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও, এবারে আর পারলেন না। সোজা গিয়ে স্ত্রীর গালে ঠাস করে বসিয়ে দিলেন এক চড়।
‘এত্ত বড় সাহস! আমি এখনই নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করব। পুলিশ ডাকব।’
‘পারলে পুলিশ ডাক দেখি তুই। হারামি মেয়েছেলে!’
তিনি অবশ্য পুলিশ ডাকেননি। বিবাহ সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট পেতে তখনো মাস কয়েক দেরি ছিল। এই সময়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদ জাতীয় সমস্যা ডেকে এনে নিজের আর মেয়ের জীবনটা পানিতে ফেলতে চাননি। তবে মনে মনে বলেছেন, পাসপোর্টটা হাতে পাওয়ার পরে এই বাড়িতে আর এক মুহূর্তও নয়। বিয়ে করতে চাইলে হাজার মানুষ পাওয়া যাবে। না করলেইবা কী! সরকারের দেওয়া টাকা দিয়ে বেশ চলে যাবে মা-মেয়ের। নিজেও না-হয় একটা কাজ জুটিয়ে নেবেন। এই ছোটলোকের সঙ্গে আর নয় যে কথায় কথায় তার স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। আসল কথা হলো, যতই আয়রোজগার হোক আর যতই সম্পত্তি হয়ে যাক, ছোটলোক চিরকাল ছোটলোকই থাকে। তবে সে যাই হোক, পাসপোর্টের লোভে মাটি কামড়ে ছোটলোকের সঙ্গে পড়ে থাকাই তার সিদ্ধান্ত ছিল তখন।
বড়সড় ধাক্কা খেয়ে সে রাতে আরিয়ানের বাবা স্ত্রীর কাছে থেকে মানসিকভাবে বিদায় নিয়ে আরিয়ানের ঘরে ফিরে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবলেন, ছেলেটার হয়েছে তার মায়ের মতো সঙ্গীতপ্রিয় স্বভাব। রাতবিরাতে গিটার নিয়ে টুংটাং করছে। নিঃশব্দে হেঁটে পাশে এসে বসলেন তিনি। বহুদিন পরে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষার আর কত দিন বাকি? প্রিপারেশন কেমন রে, বাবা?’
আরিয়ান সামান্য হাসল উত্তরে। বাবা বললেন, ‘তা, পরে কোন সাবজেক্টে পড়বে, সেসব কিছু ভেবেছ?’
‘হিস্ট্রি পড়ব, বাবা’
‘ইতিহাস!’ আরিয়ানের বাবার চোখে পানি চলে এল।
‘কেন, বাবা, ইজ দেয়ার এনিথিং রং ইন স্টাডিইং হিস্ট্রি?’
আরিয়ানের বাবা চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর চোখের পানি চোখের মধ্যেই শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, ‘আমার বাবা কোনো শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না। কিন্তু আমি যখন বললাম বড় শহরে পড়তে যাব, বাবা ডেকে বললেন, এমন পড়া পড়বি যেন তুই হামার পিছের দিনগুলানের কথা কবার পারোস।’
‘ডিড হি মিন হিস্ট্রি?’ আরিয়ানের চোখ চকচক করে উঠল। বাবা বুকের দিকে মাথা দুলিয়ে স্বীকার করলেন। তারপর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘কিন্তু আমি তা করিনি। আমার মনে হলো ইতিহাস জেনে কী হবে? আমার দরকার টাকা। এত অভাব দেখেছি জীবনে, ইতিহাস ধুয়ে পানি খাব? আমি তাই অ্যাকাউন্টিং পড়তে গেলাম।’
‘এত অভাব ছিল কেন, বাবা?’
‘অভাব থাকবে না, ওই যে মুক্তিযুদ্ধ?’
আরিয়ান চুপ করে থাকল। হয়তো উত্তর শুনে কিছু বুঝতে পারল না আবার জানতেও ইচ্ছে করল না।
‘হ্যাঁ, রে আরিয়ান, তোকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলব বলেছিলাম না?’
‘বলেছিলে।’
‘আর বলা হয়নি, না?’
‘নো প্রবলেম। আমি অলরেডি গুগলে এ নিয়ে অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি।’
‘তাই নাকি! তোর তো মনে হয় সত্যিই ইতিহাসে ইন্টারেস্ট আছে। যা, পড় তাহলে।’
‘আচ্ছা, বাবা, মুক্তিযোদ্ধারা তো দেশটা স্বাধীন করল, তাহলে তোমাকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হলো কেন?’
‘তোর দাদার জন্য। আমি পড়াশুনায় ভালো ছিলাম না, এটা কি আমার দোষ? এক টুকরা জমিতে হালচাষ করে আমি জীবন কাটাতে চাইনি, এটা কি এত বড় অন্যায়? যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকে তিনি অথর্ব হয়ে পড়ে থাকলেন, সংসার কীভাবে চলবে তার কোনো চিন্তা ছিল না। নিজে কাজ করতে পারছেন না, কিন্তু আহত মুক্তিযোদ্ধার ছেলে হিসেবে বাবা আমাকে সুবিধাগুলো তো দিতে পারতেন, পারতেন না?’
‘কিসের সুবিধা?’
‘আরে আছে নানা রকম সুবিধা। সার্টিফিকেট থাকলে এখন বলতে গেলে মাসে প্রায় আধা লাখ টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি কখনো নেননি। তিনি যদি টাকা নেন আর বিভিন্ন অফিস-আদালতে আমাকে সুবিধা ভোগের লাইসেন্স দেন, তাহলে নাকি অনেকের প্রতি খুব অন্যায় হবে।’
‘কার প্রতি? কিসের অন্যায়, বাবা?’
‘শোন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সামান্য কিছু রাজাকার, আলবদর আর আলশামস ছাড়া সারা দেশের সব মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিল। বাবার মতে তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। বাবার কথা হলো, যে কৃষক তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল, যে বুড়ি মহিলা তাকে ঘরের মাচার ওপরে লুকিয়ে রেখে পাকিস্তানি সেনার হাতে প্রাণ দিয়েছে তবু তার উপস্থিতির কথা স্বীকার করেনি, যে গরিব লোকটি নিজে না খেয়ে কয়েকদিন বাবাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। বাবা বলতেন, কই তারা তো সার্টিফিকেট দাবি করছে না? সরকার দিতে চাইলে তো সবাইকেই দিতে হবে সার্টিফিকেট! সবাইকে দিতে হবে টাকা আর চাকরিতে অগ্রাধিকার।’
‘ওয়াউ! মাই গ্র্যান্ড-পা ওয়াজ এ গ্রেট ম্যান!’
‘হ্যাঁ, বাইরের মানুষেরাও তাই বলত। আর আমাকে তার অযোগ্য ছেলে বলতেও ছাড়ত না। ওরকম বড় বৃক্ষের তলে সব চারাগাছ তুচ্ছ, কোনো দিন বাড়তে পারে না। বাইরের মানুষেরা তার নামে স্কুল-কলেজ করবে, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে মার্চ আর ডিসেম্বর এলে বাড়ি বয়ে এসে ফুলের মালা দিয়ে যাবে, আর বড়জোর মরার পরে কবরের ওপরে একটা মিনার তৈরি করে দেবে, ব্যস।’
আরিয়ান উত্তেজনা থামিয়ে চুপ করে থাকল। বাবার মতামতটা বোঝার চেষ্টা করল। হয়তো কিছু বুঝল আবার হয়তো অনেক কিছু বুঝল না। বাবা কেন যেন শীত শীত আবহাওয়ার মধ্যে বিছানায় বসে কিছুটা ঘামলেন আবার হাঁফাতেও লাগলেন। তারপর আরিয়ানের মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘ঘুমা, রাত হলো।’ আরো কোনো কথা যেন মুখ থেকে বেরিয়ে না আসে, সেটা নিশ্চিত করতেই যেন তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বাবার কথামতো আরিয়ান ঘুমিয়ে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। অঘোরে ঘুমিয়েছিল যতক্ষণ না ঝাঁঝালো শব্দে ফোনটা বেজে ওঠে। ঘুমজড়ানো কণ্ঠে ‘হ্যালো’ বলতেই ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, ‘দিস ইজ সিডনি পুলিশ। আর ইউ মিস্টার আরিয়ান?’
‘ইয়েস আই অ্যাম।’
‘ইয়োর ফাদার মিস্টার কেশেম ইজ ডেড। হিজ কার গট ক্র্যাশড সামহোয়ার নিয়ার বন্ডাই বিচ অ্যান্ড বাই দ্যা ওয়ে, হি ওয়াজ ড্রাঙ্ক।’
ঘুমের ঘোরে কথাগুলো বুঝতে আরিয়ানের সময় লাগল। ঘড়িতে দেখল ভোর চারটা প্রায়। এ রকম সময়ে যার বেডরুমে ঘুমিয়ে থাকার কথা ছিল, সে বন্ডাই বিচের রাস্তায় কী করছিল, আরিয়ানের মাথায় ঢুকল না। একেই কি বলে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাওয়া, যা বাবা কোনো কোনো রাগের মুহূর্তে চিৎকার করে বলতেন? কিছুটা অবিশ্বাসের মধ্যেই ওপরতলায় বাবার স্ত্রীকে খবরটা দিতে গেল সে। বহুক্ষণ দরজায় টোকা দেয়ার পরে দরজাটা সামান্য খুলল, বড় হাই তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘এত রাতে কী?’ আরিয়ান তার বাবার মৃত্যুর খবর জানাতেই দরজাটা পুরো খুলে গেল। স্বচ্ছ রাতের পোশাক ভেদ করে তার শরীর থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল,‘ওহ্ মাই গড! আমার সিটিজেনশিপের কী হবে? অ্যাপ্লিকিশনটা কি তাহলে ঝুলে গেল?’
বাবার কুলখানির আয়োজন হলো। রিয়েল এস্টেট অফিসের লোকেরাই আয়োজন করলেন। পরিচিত বাঙালিরাও এলেন। গম্ভীর পরিবেশে আলাপ-আলোচনা চলল; তিনি কেমন ছিলেন, তার আত্মত্যাগ, তার পরিশ্রমের নেশা, তার হতাশা, তার লক্ষ্য, আর জীবনের শেষ রাতে কেনইবা গাড়ি চালিয়ে মধ্যরাতে তিনি বন্ডাই বিচের কাছে চলে গিয়েছিলেন। অনেক কিছুই রহস্যে মোড়া থাকল, থাকল কিছু আফসোস। আরিয়ানের বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী ‘মাঝখান থেকে আমি তো কিছুই পেলাম না’ বলতে বলতে কেঁদেই ফেললেন। বাবার বাঙালি বন্ধুরা বাঁধনহারা স্মৃতিচারণা করলেন। তাদের মুখে মুহুর্মুহু উচ্চারিত বাবার ‘কেশেম’ নামটা আরিয়ানের কানে খট খট করে বাজল। কারণ, কে না জানত, বাবার নাম ছিল কাশেম খন্দকার। সিডনিতে গিয়ে কাশেম খন্দকার হয়ে গিয়েছিল কেবলই কেশেম। খন্দকার উচ্চারণ নিঃসন্দেহে আরো কঠিন ছিল। কুলখানির ভাবগম্ভীর আলাপ-আলোচনা শেষে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে কাজ করা অস্ট্রেলিয়ান লোকেরা জানতে চাইল, ‘হোয়াই নো প্যারেন্টস? নো রিলেটিভস? ডিডন্ট হি হ্যাভ এনিওয়ান?’ আরিয়ান এর উত্তরে কিছু বলতে পারল না। কেউ নেই, এতে বলারও কিছু নেই। কিন্তু বাবার কুলখানির পরে কয়েক মাসব্যাপী ওই কথাটাই তার কানে বাজতে থাকল, নো প্যারেন্টস? নো রিলেটিভস?
এইচএসসি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিতে না দিতেই ক্রিস্টিনের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল আরিয়ানের। কিছুদিন কেবল নিজেদের দিকে তাকিয়ে থাকতেই কেটে গেল। সামান্য কদিন আগের অনেক কিছু তখন জোর করে মনে না করিয়ে দিলে আরিয়ানের আর মনেও পড়ত না। বাঙালি কেউ কখনো বাড়ি বয়ে এসে মায়া দেখাতেন, ‘আহা, এতটুকু বয়সে মা চলে গেছে, তারপর এরকম দরকারের সময়ে বাবাও চলে গেল। কিছু লাগলে আমাদের জানিও, বাবা।’ কখনো বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী ফোন করে শক্ত গলায় বলতেন, ‘আরিয়ান, আমার এ মাসের খরচটা কিন্তু এখনো ব্যাংকে জমা হয়নি, অফিসের অ্যাকাউনটেন্টকে একবার মনে করিয়ে দিও।’ এই সমস্ত থেকে আবার ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া যেত ক্রিস্টিনকে দেখলেই। কিন্তু একবার দিনব্যাপী একসঙ্গে বসে অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে ক্রিস্টিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘হোয়াট ইজ ইয়োর ন্যাশনালিটি?’
‘আই অ্যাম অ্যান অস্ট্রেলিয়ান অফ কোর্স। বাই বর্ন।’ আরিয়ান উত্তর দিল।
‘নো আই মিন, হোয়ার ডিড ইউ কাম ফ্রম?’
‘মাই ফাদার কেম ফ্রম বাংলাদেশ।’
আরিয়ানের বাবার মৃত্যুর কথা আগেই জানা ছিল ক্রিস্টিনের। তাই হুট করে জানতে চাইল, ‘ইউ হ্যাভ রিলেটিভস, ডোন্ট ইউ?’
‘নো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনিওয়ান।’
‘আই মিন, নো রিলেটিভস ইন ব্যাংলাডেশ?
‘আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি।’
বলতে গিয়ে উদাস ভাব চেপে ধরল আরিয়ানকে। ক্রিস্টিন আরো বেশি উদগ্রীব হলো, কিছুটা জেদি কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল, ‘হোয়াট ডু ইউ মিন ইউ ডোন্ট নো? ডোন্ট ইউ নো ইয়োর অ্যানসের্স্টাস?’
‘আই ডোন্ট নো ইফ দেয়ার ইজ এনিবডি। আই নেভার ওয়েন্ট টু বাংলাদেশ।’
‘আই মিন ইউ রিয়েলি হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট হু ইউ আর! ভেরি স্ট্রেঞ্জ, ইউ নো, মাইট?’
নর্থ সিডনির বিশাল বাড়ির ডেকের মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরিয়ান তখন কেবল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত। নো রিলেটিভস? নো অ্যানসের্স্টাস? ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আরিয়ান সমুদ্রের শত ঢেউকে ভাঙতে দেখত আর নিজের ভেতরে ভাঙনের শব্দ শুনত। কেন যেন নিরাপদ আর নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চয়তায় ভরা জীবনটা ধীরে ধীরে ফাঁপা হয়ে পড়ছিল। কেন যেন সুলভ সমস্ত কিছু অর্থহীন মনে হতো। ক্রিস্টিনের গলা না চাইতেও কানে বাজত, ইউ ডোন্ট নো হু ইউ আর! কিছুতেই বুঝতে পারত না আরিয়ান, যে দেশে তার জন্ম আর বড় হওয়া, কেন বুক ফুলিয়ে বলতে পারছে না যে আমি কেবল এখানকারই? আমি অস্ট্রেলিয়ান? কেন পেছনে একটা যোগাযোগ থেকেই যাচ্ছে, যা আরিয়ান না পারে ফিরিয়ে আনতে, না পারে ভুলতে। আবার সেই অতীত নিয়ে কষ্টও বাড়ছে যার সম্পর্কে সত্যি সত্যি তার কোনো ধারণা নেই। মাঝে মাঝে চোখ বুজলে পেছনের দিকে কেবল ধোঁয়া মনে হতো। আরিয়ান সেদিকে মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করত, কিছুই দেখতে পেত না। বাবা কখনো বাংলাদেশে যাবার কথা বলেননি। তবে একবার না-যাবার কারণ বলেছিলেন; বলেছিলেন, ‘একসময় যাবার জন্য অস্থির লাগত। সারা দিনের খাটুনির মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ মনে হতো মনটা চলে গেছে, কেবল শরীরটাই এই অচেনা জায়গায় পড়ে আছে। কখনো মনে হতো বৈধতার কাগজটা হলেই পরেরদিনের টিকিট কাটব। কিন্তু তখন বাবার কথা মনে পড়ত, একবার গেইলে তুঁই আর মোর সামনত আসপু না। যাওয়ার ইচ্ছাটা মেরে ফেলার চেষ্টা করতাম তখন। তারপর বছরের পর বছর পাসপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একদিন পাসপোর্ট আর অস্ট্রেলিয়ান সরকারের দেওয়া উপহারের চারাগাছটা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। দেখলাম, সত্যি, এতদিনে দেশে যাবার ইচ্ছেটা মরেছে। খবর পেলাম বাবাও তত দিনে নেই। চারাগাছটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, এখানেই না-হয় শুরু থেকে বেড়ে উঠি। নতুন জন্ম হোক...’
‘কিন্তু জন্মের পেছনের সত্য যে ছাড়ে না, বাবা!’ বাবার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে আরিয়ান, যেন মৃত বাবার সঙ্গে কথোপকথন চলছে। নিজের মুখের উচ্চারণ নিজের কানেই অস্বাভাবিক শোনায়। আকস্মিক মনে হয় পেছনের সেই ছবিটা না দেখলে যেন আর সামনে এগোতে পারবে না। কিছুতেই না। কিন্তু কোথায় যাবে? কার কাছে খোঁজ করবে? তার কাছে না ছিল কোনো ঠিকানা, না কোনো ফোন নম্বর। আরিয়ান বাবাকে কোনোদিন বাংলাদেশে কারো সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেখেনি। কোনো বাঙালির সঙ্গে ফেলে আসা পরিবার নিয়ে আলাপ করতেও শোনেনি। সেভাবে ভাবতে গেলে, আরিয়ানের চোখে বাবা ছিল আকাশ থেকে টুপ করে মাটিতে পড়া মানুষ; যেন সত্যিই বাবার আগে-পিছে কেউ ছিল না, না কোনো আত্মীয়, না পূর্বপুরুষ।
তখন থেকে আরিয়ান কিছুটা গোয়েন্দার মতো আচরণ করতে শুরু করল। হাতে সময় থাকলেই বাবার পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি। এই করতে করতে সুফলও পেল একদিন। একটা পুরোনো ডায়রিমতো নোটবুক পাওয়া গেল। প্রথম পৃষ্ঠায় ফাদার’স নেমের ফাঁকা লাইনটির নিচে অচেনা হরফে কিছু লেখা। আরিয়ান ইংরেজি লেখে লাইনের ওপরে আর এই ভাষা লাইনের নিচে। বাবার ডায়রি যখন, বাংলাই হবে। কাউকে দেখিয়ে জানতে চাইলেই হতো। কিন্তু ইচ্ছা করল না। বোঝাই গেল, নাম-ঠিকানা সব লেখা আছে বায়োডাটার মতো। একেবারে বাংলাদেশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। যেই ভাবা সেই কাজ, আরিয়ান পেছনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিঠাপুকুরের চৌপথীতে এসে উপস্থিত। এ হতে পারে না যে সে জানে না সে কে! ঠিক যেমনটা ক্রিস্টিন ভেবে অবাক হয়।
চৌপথী মোড়ের উল্টোদিকের মাঠটাতে ঠায় বসে থাকে আরিয়ান। হুট করে আসা এলোমেলো বাতাসে তার রেশমের মতো মেহগনি রঙের ঝরঝরে চুলগুলো উড়তে থাকে। জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া ঘাসগুলোর গায়ে সে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়। এই মাঠেই বুঝি একদিন তার বাবা খেলাধুলা করে দিন পার করেছে, এই মাটিতেই একদিন তার দাদা গম্ভীর পা ফেলে হেঁটেছে। আরিয়ানের বিস্ময় লাগে, সেইসব মিলিয়ে যাওয়া পদক্ষেপ স্পর্শ করা এত সহজ! যেন যা দেখতে চেয়েছিল, সব দেখা হয়ে গেছে।
আকস্মিক সেই কিশোরীর কণ্ঠস্বরে ধ্যান ভাঙে আরিয়ানের। মাঠের মাঝামাঝি রোদের দিকে চোখ কুঁচকে সে বয়স্ক একজন নারীকে বলছে, ‘ওই যে, ওই মানুষটা আলছে। নানাক ক্যান জানি দাদা কবার নাগছে।’ কিশোরীর আঙুল আরিয়ানের দিকেই উদ্যত। দুজনে দ্রুত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। বয়স্ক নারী মাথার ঘোমটা ভালোমতো টেনে বলেন, ‘ক্যা বাহে, মতলুব খন্দকার তোমার দাদা হয় নেকি? তোমরা কি হামার কাশেম ভাইয়ের ছাওয়াল?’
এই প্রথম সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন। এই প্রথম বলার সুযোগ সে আরিয়ান সম্পর্কে কারো কিছু হয়! ক্রিস্টিনের ধারণা, মিথ্যে ঘোষণা করার এটাই মোক্ষম সময়। তাই লাফিয়ে উঠে বুক ফুলিয়ে আরিয়ান বলে, ‘হ্যাঁ, আমি কাশেম খন্দকারের ছেলে, মতলুব খন্দকারের গ্র্যান্ড সান’। বলে নিয়ে আরিয়ান ভাবতে থাকে গ্র্যান্ড সানকে কী বললে তারা বুঝবে তার জানা নেই। আবার ভাবে তারা হয়তো তার বাংলাটাই ঠিকমতো বুঝতে পারছে না, তাই অত ভেবে কী লাভ। নিজের ওপরে ভারি বিরক্ত লাগে তখন। কিশোরীটির মুখ হাঁ হয়ে যায় আরিয়ানের কথা শুনে। বয়স্ক নারী কী ভাবেন বোঝা যায় না। ঘোমটাটা আরেকটু ঠিক করে নিয়ে হতাশা আর বিরক্তিভরা গলায় মাটির দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘ক্যা বাহে, এত্ত বচ্ছর বিদ্যাশ থাকিয়্যাও তোমরা অটে বাড়িঘর কিছুই কইরবার পারেন নাই? অ্যাদ্দিন পর হামার খুপরিটাত ভাগ বসাইবার আলছেন?’
‘না না, আমি তো কিছু নিতে আসিনি!’ চমকে বলে আরিয়ান।
এবারে কিশোরীটি এগিয়ে আসে সামনে, ‘তাইলে তোমরা আলছেন ক্যান অ্যাটে?’
‘দেখতে।’
কিশোরী আর তার সঙ্গের নারী খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আরিয়ানের দিকে। কিশোরী ঠোঁট উলটে বলে, ‘দ্যাখেন। কিন্তুক এইখানত দ্যাখার কী হইল্?’ আরিয়ানের কথায় নিশ্চিন্ত নারীটি তখন তাকে থামায়, বলে, ‘আইসো, বাবা। বাড়িত চলো। মুই তোমার ফুফু হঁও। আর এঁই হইল্ তোমার ফুফাতো বইন। ভরদিন তোঁরা খান নাই বুঝি কিছু? আইসো।’
আরিয়ান তাদের পেছনে পেছনে হাঁটে। মাঠের পাশের ঝোপের কাঁটা জাতীয় গাছ থেকে একটা বেগুনি ফুল ছিঁড়ে নেয়। গোবরলেপা দেয়ালের পাশে দাদার কবরের ওপরে গভীর মমতায় রাখে ফুলটা। দুই নারী চোখেমুখে খানিকটা বিস্ময় কিংবা কৌতুক নিয়ে আরিয়ানকে দেখে।
ঢোকার মুখে ঝুড়ি নামা বটগাছওলা সেই বাড়িতে দুদিন থাকার পরে কিশোরী আবারও আরিয়ানের কাছে জানতে চায়, ‘তোমরা সত্যিই কিছু নিবার আইসেন নাই, বাহে?’
‘নিলাম তো।’
‘কী নিছেন?’
‘পরিচয়।’
কিশোরী ভুরু কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু এ যেন তার বোঝাবুঝির বাইরে। সে বরং দৌড় দিয়ে গিয়ে একটা বই নিয়ে আসে। বইটা খুলে তিনটা শুকিয়ে যাওয়া বটের পাতা কাঁপা কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দেয় আরিয়ানের দিকে। উন্মুক্ত বাদামি শিরা-উপশিরাগুলোর দিকে তাকিয়ে আরিয়ান কিছ্ইু বুঝতে পারে না, শুধু হাত বাড়িয়ে নেয়। কিশোরীটি লাজুক মুখ করে বলে, ‘তোমাক দিনু। মোর উপহার।’
কৃতজ্ঞ চোখে পানি চলে আসে আরিয়ানের। যাত্রাপথে পড়বে বলে সিডনি এয়ারপোর্ট থেকে নিকোলাস স্পার্কের যে উপন্যাস কিনেছিল, পাতাগুলো তার মধ্যে সাবধানে ভরে রাখে। মেয়েটি খুশি হয়। তার হাসিমুখ দেখে আরিয়ানেরও ভালো লাগে। ফিরে যাবার পথে চৌপথী মোড়ে দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভালো করে দেখে নেয় সে। কেন যেন মনে হয় সে তার বাবার চোখ দিয়ে দেখছে। বটের পাতাগুলো ধরে রাখা উপন্যাসটা বুকে চেপে ধরে আরিয়ান মনে মনে বলে, ‘তোমার দেশ থেকে তিনটা শুকনো পাতা নিয়ে যাচ্ছি, বাবা। এরা আমার পরিচয়ের কথা বলবে।’
রাইজিংবিডি/ঢাকা/৭ জুন ২০১৬/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন