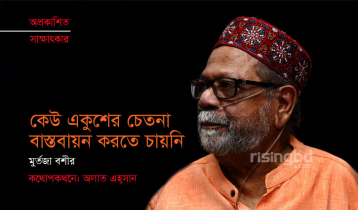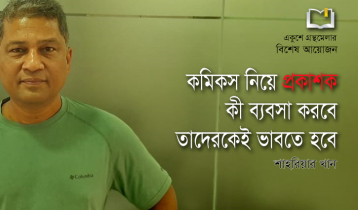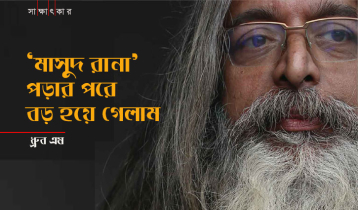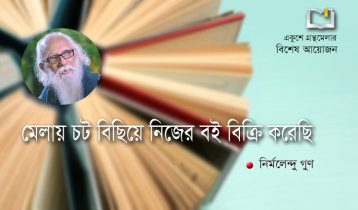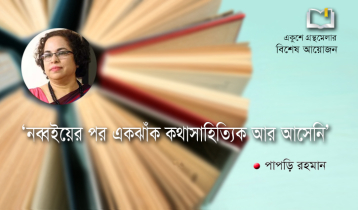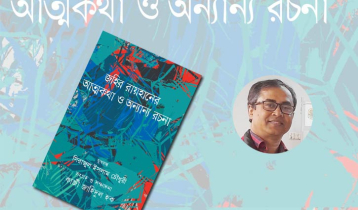একচক্ষু হরিণীরা : পঞ্চম পর্ব
রাসেল রায়হান || রাইজিংবিডি.কম
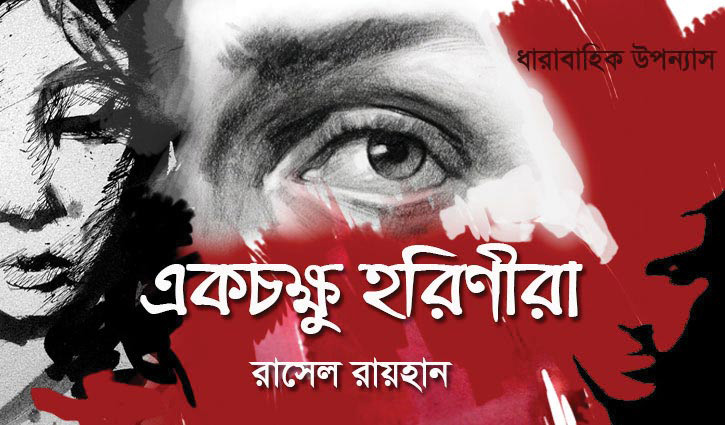
যেদিন আমরা ময়মনসিংহ পালিয়ে যাই, সেদিন আমার বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়ার কথা। আর রেজাল্ট জানা যায়নি। পরে মা খোঁজ লাগিয়েছিলেন অনেক, জানা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে মায়ের বড় আক্ষেপ ছিল। একুশ বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠানোর সময় মা বারবার বলে দিয়েছিলেন, বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্টটা জেনে আসিস পারলে। প্রাইমারি স্কুলে গেলেই জানতে পারার কথা। যাস কিন্তু বাবা।
বয়স কত আমার সেসময়! নয় বছর। নয়-ই তো? নাকি আট? পাঁচ বছরে ভর্তি হয়েছিলাম টুতে। ছয়ে থ্রি, সাতে ফোর, আটে ফাইভ। হ্যাঁ, আট শেষ হয়ে নয়ে পড়বে। এমন একদিন ভোররাতে দেনার দায়ে পালিয়ে আসতে হয় মা-বাবাকে।
ভালোই চলছিল বাবার পানসিগারেটের দোকান। হঠাৎ তার ব্যবসা করার শখ জাগে। কে যেন তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, দোকানদারি আর ব্যবসা এক না। পুরনো দোকান বেচে আর কিছু ধার করে মুদির ব্যবসা শুরু করেন বাবা। কর্মচারী রেখে নেন দুজন।
তেল, ডাল, মরিচ, হলুদ, লবণ—এসব বিক্রি করতেন। নৌকায় করে একেকদিন নিয়ে যেতেন একেক জায়গায়। যে জায়গায় যেদিন বাজার বসতো, সেদিন সে জায়গায় যেতেন। নৌকা কিনে ফেলেছিলেন বাবা একটা। কর্মচারীরাই বাইত সে নৌকা। বাবা চুপচাপ বসে থাকতেন নৌকায়। বসে বসে হিন্দি গান শুনতেন: দিদি তেরা দিবার দিওয়ানা, কিংবা তু চিজ বাড়ি হে মাস্ত মাস্ত...। গান শুনতেন আর আস্তে আস্তে মাথা দোলাতেন।
কর্মচারীদের মধ্যে মিজান সার্বক্ষণিক দেখভাল করত বাবাকে। বাবা অন্ধ ছিলেন। কিন্তু মোটামুটি অন্ধত্বকে জয় করেছিলেন তিনি। তার এক চোখ ছিল আমার মা, দ্বিতীয় চোখ ছিল নিজের মনের জোর।
রাতে ঘরে ফিরে হাত-মুখ ধুয়েই বাবা তার কোমরের থলে খুলে টাকা গুনতে বসতেন মাকে নিয়ে। আমি তখন বাবার পাশে বসে থাকতাম। টাকা গোনা শেষ হলেই মা কখন দু টাকার একটা নোট দেবেন—সেই লোভ বড় তীব্র ছিল আমার। কোনো কোনোদিন বাবা পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে বলতেন আজে বাজে কিছু খেও না কিন্তু, বাবা।
রোজ বেলুন কিনতাম—এক টাকার চারটা। তারপর এগুলো নিয়ে খেলতাম। বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিতাম, কে কত বেশি বড় করতে পারে। সমস্ত দম একত্র করে বেলুন ফোলাতাম। পাতলা সব বেলুন, সেগুলি ফোলাতেই দম আটকে যেত।
মা বারবার বারণ করতেন এসব বেলুন কিনতে। তবু কিনতাম। বেলুনের ব্যাপারটা বুঝতে পারি আরও বড় হওয়ার পর। লজ্জায় তখন মাটিতে মিশে যাওয়ার জোগাড়।
সেদিনের ঘটনা আজও স্পষ্ট মনে আছে আমার। কদিন জ্বরে ভুগছিলেন আব্বা। বারান্দায় বসেছিলেন, এমন সময় মিজান ভাই কাঁদতে কাঁদতে এসে জানান যে নৌকা ডুবে গেছে। লঞ্চের সাথে ধাক্কা লেগেছিল। আব্বাকে তখন দেখেছি বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে। আমি আব্বার পাশে বসা। আব্বা কাঁদছেন আর বাচ্চা ছেলের মতো বুক চাপড়াচ্ছেন। মা একটা তালপাখা এনে বাতাস করতে থাকেন। এই দৃশ্যটিও আমি কখনো ভুলতেই পারিনি। আমার দেখা পৃথিবীর সবচে’ কুৎসিত দৃশ্য। চা-অলা কাকির সেই বাচ্চা প্রসবের দৃশ্যের চেয়েও কুৎসিত।
বাবা আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে। আর পারেননি। মাঝখান দিয়ে অনেক ধারদেনা জমে গেল। এক সময় পাওনাদারেরা বাড়িতে আসতে শুরু করল। বাসায় এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত তারা। শুধু বসে থাকত। কোনো গালিগালাজ করত না। হয়তো আব্বা অন্ধ ছিলেন বলে। কিংবা অন্য কোনো কারণ। আব্বা সাধ্যমতো আপ্যায়ন করতেন তাদের। তারা কাপের পর কাপ চা গিলত। আর গিলত আম্মাকে। একটু পরপরই আড়চোখে তাকিয়ে থাকত আম্মার দিকে। ভয়ংকর সে দৃষ্টি! কী নোংরা।
আব্বা কিছুই বুঝতেন না হয়তো। কিংবা না বোঝার ভান করে থাকতেন।
অবশেষে একদিন তিনি পালাতে বাধ্য হন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে। ব্যাপারটা মূলত এমন, তার স্ত্রী পালাতে বাধ্য হন স্বামী-সন্তান নিয়ে। ভোরবেলার প্রথম ট্রেনে। আমার তলপেটে তখন প্রবল চাপ। আমার এক হাত বাবার হাতে। অপর হাত চেপে ধরে আছেন মা। দুজনেই কাঁদছেন। তাদের চোখের জল ট্রেনের হু হু বাতাসেই শুকিয়ে যায়।
বারো বছর পরে আমাকে দেখেও বারোটি মুহূর্তেই চিনে ফেলেন চা-অলা কাকি। এটা কীভাবে সম্ভব, কে জানে! এই বারো বছরে আমার চেহারা কি একটুও পাল্টায়নি? সামান্য সন্দেহও হয়নি কাকির। দরজা খুলে আমাকে দেখেই চিলের মতো চিৎকার দিয়ে ওঠেন তিনি। হুড়মুড় করে নামতে গিয়ে শাড়িতে পা বেঁধে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তার। কোনোমতে এসে শীর্ণহাতে জড়িয়ে ধরেন আমায়। কাঁদতে কাঁদতে কথা জড়িয়ে যায় তার। এক কথাই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তার, আব্বা। মুকুল আব্বা, তুমি আসছ? আমি জানতাম তুমি আসবা। আব্বা...
কাকি আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে রাখেন। কিছু বলার মতো কথা আমার মুখে আসে না। এ অবস্থায় কী বলতে হয় আমার জানা নেই। বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অশ্রু মোছাই বুদ্ধিমানের কাজ।
কাকি বেজায় কালো ছিলেন তখন। এখনো আছেন। শুধু কুচকুচে কালো চুলগুলিতে চুনের পরত লেগেছে মনে হয়। ধবধবে সাদা।
সেই পুরনো দৃশ্য আবার ফিরে এলো। করুণাময় কি পুনরাবৃত্তি খুব পছন্দ করেন? সেই একইভাবে একুশ বছরের মুকুল ছোট্ট শিশু হয়ে চুকচুক করে চা খাচ্ছে। কাকি পাশে বসে টুকটুক করে গল্প করেছেন। বাবার কথা জিজ্ঞেস করছেন, মায়ের কথা, মুকুল চা খেতে খেতে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। কাকি গ্লাসটা নিয়ে আবার একটু কনডেন্সড মিল্ক ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়তে থাকেন।
হঠাৎ মইদুল কাকার কথা মনে পড়ল আমার।
কাকি, কাকা কোথায়?
স্টেশনে গেছে। আর একটু পরে আসব। আইসা আবার ফ্ল্যাক্স ভইরা নিব।
কই, আমি তো ট্রেন থেকে নেমেই খুঁজলাম। পাইনি।
আছে কোথাও।
আর নূরী...?
প্রশ্নটা করেই আমার একটা পুরনো দৃশ্য মনে পড়ে যায়। আমি যখন রান্নাঘরে এসে বসতাম, তখন পাশে বেণীবাঁধা এক বালিকা এসে বসে থাকত। আমার চুকচুক করে চা খাওয়া দেখতে দেখতে মাকে হঠাৎ বলত, আম্মা, আমারে একটু চা দিবা না?
কাকি ধমকে উঠতেন, যা যা, তুই তো সব সময় চা খাইস। ছ্যাড়াটা একটু খায় তাও লোভ দেওন লাগব। যা এইখানে থেইকা। ছেমড়ি !
আমার চেয়ে বয়সে সামান্য বড় নূরী যেত না। একভাবে তাকিয়ে আমার চা খাওয়া দেখত। সে দৃষ্টিতে দ্বিধাহীন লোভ। অথচ আমারও কোনোদিন মন চায়নি তাকে একটু চা দেওয়ার জন্য। আরেকদিকে তাকিয়ে চা খেতে খেতে শুনতাম, নূরী টেনে টেনে বলছে, অ মা, এট্টু চা দেও না। দুধ চা তো দেও না, খালি লাল চা। লাল চা আমার এট্টুও ভালো লাগে না।
কাকি দিতেন না। সামান্য চা বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। এক কাপ চা এক টাকা, আর দুধ চা দুই টাকা কাপ। এক টাকার দুইটা বিস্কুট। এই বিক্রির টাকায় তাদের সংসার চলে। কীভাবে চলত—কে জানে!
আমার চোখে ভেসে উঠে সেই পুরনো বুভুক্ষু দৃষ্টি। আজকের রান্নাঘরটা অসম্পূর্ণ লাগে। ইশ, বালিকাটি যদি আবার বেণী দুলিয়ে আসত! পাটকাঠির মতো শুকনো কালো মেয়েটি, যার ছোটো বোনের জন্মপ্রক্রিয়া এক মুহূর্ত দেখে ফেলেছিলাম আমি।
একবার নূরীর গাল কিংবা ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিলাম। রক্ত পড়ে-টড়ে বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়েছিল। কী নিয়ে মারামরি লেগেছিল, ঠিক মনে নেই। কত কিছু মনে আছে, অথচ এটা মনে নেই। স্মৃতি মাঝে মাঝেই প্রতারণা করে। সে দাগ কি এখনো আছে নুরীর গালে কিংবা ঠোঁটে? নাকি মিলিয়ে গেছে?
কাশতে কাশতে মুখে তৃপ্তির একটা ভাব নিয়ে কাকি বলেন, নূরীর বিয়া হয়া গেছে। নতুন এক স্টেশন মাস্টার আইছে। খুব ভালো পোলা। হ্যায়ই প্রস্তাব দিছিল। পোলার আব্বা আম্মা বাঁইচ্যা নাই। পোলা অনেক ভালো। আব্বা, তোমাগো জানাইতাম অর বিয়ার খবর। কিন্তু তোমাগো ঠিকানা তো জানি না। নূরীর আব্বায়ও জানে না। তাও খোঁজ করছিলাম অনেক। পাই নাই।
নূরীর বিয়ের খবরটা শুনে আমার বুকের মধ্যে অমন জ্যান্ত মৃগেল মাছের মতো ঘাঁই দিয়ে উঠল কেন? আমি তো কোনোদিনই নূরীকে আকাঙ্ক্ষা করিনি। তখন তো সে বয়সই ছিল না। বড় হয়েও কখনো আলাদা করে নূরীর কথা ভাবিনি। তবে? বুকটা মৃগেল মাছ ভর্তি পুকুর হয়ে ওঠে কেন? চোখ কেন ভিজে উঠতে চাইবে! তাড়াতাড়ি কাকিকে বললাম, কাকি, জ্বালটা বাড়িয়ে দিন। চোখ জ্বলছে। অ্যাত্ত ধোঁয়া।
কাকি ত্রস্ত হয়ে কাঠগুলো আরও ভিতরে ঠেলে দেন। বলেন, তুমি বাইরে গিয়া বসো না হয়।
সমস্যা নেই কাকি।
আহা, বসোই না বাইরে। চুলার কাছে ছেলে মানুষের না বসাই ভালো।
এক মূহূর্তের জন্য কাকিকে আমার শক্র মনে হয়। কাকি কাঠগুলো ভিতরে ঠেলে দেন। আগের কথার খেই ধরে বলতে থাকেন, পোলাডা অনেক ভালো... আব্বা, তুমি দুপুরে খাওয়া দাওয়া কর, আমি নূরীরে খবর পাডাই। জামাইও আইব নে। কতা কইলেই বুঝবা, কত ভালো পোলা!
তাড়াতাড়ি বলে উঠি, দুপুরে খেতে পারব না কাকি। আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। মা আপনাকে একটা জিনিস দিয়েছেন। ওটা দিতে এসেছি।
কী জিনিস, আব্বা?
আমি জানি না, কাকি।
কী জিনিস, সেটা আমি ভালো করেই জানি। একটা গহনা সেট পাঠিয়েছেন মা। বারো বছর আগে যখন এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই, তখন মা শুধুমাত্র বাবার জন্য একটা অন্যায় কাজ করেন। বাবার হাতে একটা পয়সা নেই সে-সময়। অথচ রাতের মধ্যে এখান থেকে পালিয়ে যেতেই হবে। মা তখন চা-অলা কাকির একমাত্র সোনার হারটি চুরি করেন। কাকি কোথায় কী রাখেন, মা জানতেন। সোনার হার চুরির সেই অপরাধবোধ মাকে রোজ তাড়া করে বেড়িয়েছে।
কাকির এখানে আসার আগে পুরনো সব দেনা পরিশোধ করে এসেছি। শেষ ঋণটুকু পরিশোধ করে নিজেকে বড় হালকা বোধ হতে লাগে আমার।
কাকি না খেয়ে আসতেই দেবে না। তবুও থাকিনি। নূরীর সামনে পড়া সম্ভব না। ওর বোনটার সাথেও দেখা হয়নি। তারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে।
ট্রেনে ওঠার আগে আমার চোখ চলে গিয়েছিল পেছনে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনটি প্রাণী কাঁদছিল। চা-অলা কাকি, কৃষ্ণচূড়া গাছ আর শ্যামলা বর্ণের একটি মেয়ে। অত দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম তাদের। সম্ভবত তৃতীয় মেয়েটির নাম নূরী।
নূরীর সাথে আমার দ্বিতীয় এবং শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ঢাকায়। না হওয়াই ভালো ছিল।
সাত
সুবিদ আলী পারুলকে পাখিপড়ার মতো মুখস্থ করাতে লাগলেন, মাহমুদ আমার স্বামী, মাহমুদ আমার স্বামী। পারুলও মুখস্থ করে ফেলেছিল। যদিও স্বামী শব্দটি বোঝার মতো বয়স তখন তার হয়নি। বরং পারুল আর মাহমুদ আলী বেড়ে উঠছিল আসলে ভাইবোনের মতন। সুবিদ আলীর সম্ভবত এমন কোনো ধারণা ছিল যে, মুখস্থ হলে আত্মস্থ হতে সময় লাগবে না।
পারুলকে তিনি ঘরকন্যা শেখাতে লাগলেন। আগে রান্নাবান্নাসহ ঘরের প্রয়োজনীয় সব কাজ সুবিদ আলী একা করতেন, পারুলকে এবার তিনি ঘর গোছানোসহ ছোটখাট সব কাজ শিক্ষা দিতে লাগলেন।
স্কুল থেকে এসে পারুল দোকানে বসতো মাহমুদের সাথে। বসে বসে মাহমুদের মুখস্থ পান বানানো, সিগারেট দেওয়া দেখতে তার ভালো লাগে। তবে দোকানের কোনো কাজ সে করে না। সুবিদ আলী বারণ করে দিয়েছেন। তাও মাঝেমধ্যে মাহমুদকে সাহায্য করতে যেত পারুল। ক্রেতাকে পান বানিয়ে দেওয়া, সিগারেট দেওয়া। একদিন সুবিদ আলীর চোখে পড়ায় তিনি পারুলকে দোকানে আসতেই বারণ করলেন। তারপর থেকে পারুল আর দোকানে আসে না।
একদিন একটা ব্যাপার ঘটল। হাটের দিন। খুব ভিড়। শনি আর মঙ্গল—সপ্তাহে দুদিন হাট হয় এখানে। লোকজন নৌকায় করে নানাকিছু নিয়ে বাজারে বসে। লোকে লোকারণ্য থাকে তখন। এই দিনগুলোতে সুবিদ আলী দোকানে এসে বসেন। মাহমুদ আলী একা সামলাতে পারে না। ভুলভাল করে ফেলে। তিনজনকে তিনটা সিগারেট দিয়ে দুজনের কাছ থেকে বিল রাখে। যে জর্দা চাইল না, তাকেও জর্দা দিয়ে দেয়, কাঁচা সুপারি চাওয়া লোকটাকে শুকনো সুপারি দিয়ে পান বানিয়ে দেয়। এলাকার কেউ ঠকায় না মাহমুদকে, তবে দূর থেকে আসা অনেকে সুযোগ নেয়।
সেদিন বিকেলে এক লোক দোকানে এসে মাহমুদকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাপে কই? সুবিদ আলী পাশের দোকানে ছিলেন। মাহমুদ আলীর গলা শুনতে পেয়ে তিনি দোকানে আসেন। দোকানে ঢুকতেই আগন্তুক লোকটি সরাসরি দাবি করে বসে, পারুল তার মেয়ে। বিশাল ভুড়িঅলা, মাথায় টাক পড়া এক লোক। কুচুটে ধরনের চেহারা লোকটার। প্রথম দর্শনেই সুবিদ আলী তাকে অপছন্দ করে ফেলেন। লোকটার দাবি, পারুল তার মেয়ে। বছরখানেক আগে সিঁদুরবাজারের মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি তাকে নিতে চান। ভালোয় ভালোয় দিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। নইলে তিনি থানাপুলিশে যাবেন।
সুবিদ আলীর প্রায় অজ্ঞান হওয়ার দশা। তিনি লোকটাকে মারতে যান পারলে। সোজা বলে দেন, থানাপুলিশ যা খুশি সে করুক। সুবিদ আলী পারুলকে দেবেন না। কিন্তু একসময় মাহমুদ আলীর গলার জোর আর থাকে না। তিনি অসহায় বোধ করতে থাকেন, যখন দেখেন যে আশেপাশের সবাই লোকটাকে সাপোর্ট করছে। তারা সবাই বলছে, পারুলকে তো কুড়িয়ে পাওয়া। দিবা না কেন? এখন তার বাবা তাকে নিয়ে যেতে আসছে, রেখে দিবা কোন যুক্তিতে?
রেখে দেওয়ার কোনো যুক্তি সুবিদ আলী দেখাতে পারেন না। তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন।
পারুল স্কুলে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে আসা হলো স্কুল থেকে। পারুল এসেই লোকটাকে চিনতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। সুবিদ আলীও ধড়ে প্রাণ ফিরে পান। তার গলা আবার উচ্চ থেকে উচ্চকিত হতে থাকে। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। আশেপাশের লোকজনও তার পক্ষে। তারা বলছে, পারুল ছোট মানুষ। এতদিনে নিশ্চয়ই সে তার আসল বাবা-মাকে ভুলে গেছে। লোকটাও জোর ফিরে পায়। সে পারুলকে নিয়ে যাবেই। না নিয়ে গেলে তার স্ত্রী আর বাঁচবে না। মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর তার পাগলপ্রায় দশা। সারাদিন শুধু পারুল পারুল করে কাঁদে।
তখন সুবিদ আলীর মাথায় একটা জিনিস খেলে যায়। সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, কী নাম বললেন মেয়ের?
লোকটা চরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, কেন, পারুল!
সুবিদ আলী বলল, আবার বলেন। কী নাম?
পারুল।
তখন সুবিদ আলী লোকটির কলার ধরেন শক্ত করে। পাশের দু দোকানের লোকদের ডেকে আনেন, শুনছেন, সে বলতেছে যে তার মেয়ের নাম পারুল! আপনাদের মনে আছে, এই মেয়ে যখন আসছিল, তখন তার নাম কী বলছিল?
জুতার দোকানদার মিজান বলল, তাই তো, এই মেয়ের নাম তো পারুল ছিল না। এর তো অন্য নাম ছিল। যদিও সে সেই নাম মনে করতে পারল না।
ভিড়ের মধ্য থেকে অন্য একজন বলল, আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই মেয়ে তার নাম বলছিল চম্পা। এর নাম তো পারুল রাখছে সুবিদ আলীই।
তখন ভুড়িঅলা লোকটা আমতা আমতা করতে থাকে। এরপর ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির বুঝতে সমস্যা হয়নি যে এই লোকটা ঠগ। সবাই মিলে বেদম মার দেয় লোকটাকে। মরার মতো দশা হয়েছিল লোকটার। সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সত্যি সত্যি মারা না যায়। তাহলে পুলিশ কেসে পড়বে। শেষে সবাই মিলে লোকটাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। দুদিন পর লোকটা হাসপাতাল থেকে পালিয়েছিল। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তার। (চলবে)
রাইজিংবিডি/ঢাকা/১৮ আগস্ট ২০১৭/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন