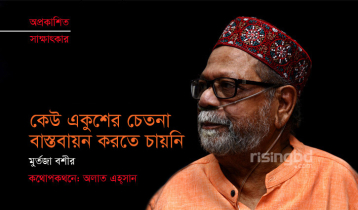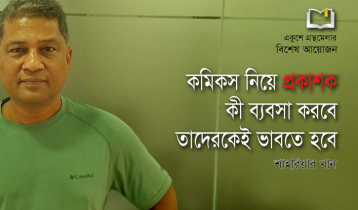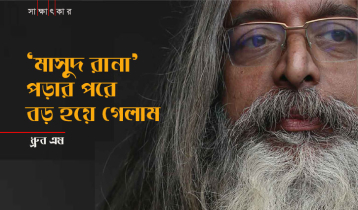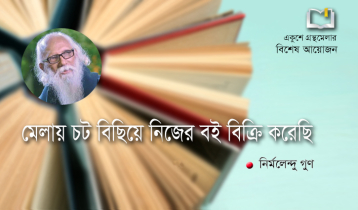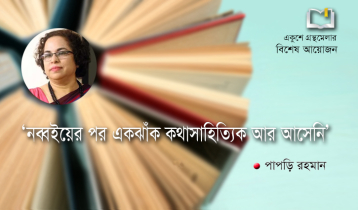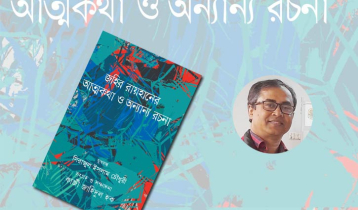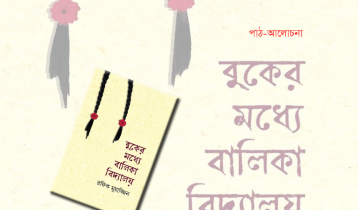রবীন্দ্র-গল্পে বাস্তবতার একদিক : প্রসঙ্গ ‘সমাপ্তি’

|| মোহাম্মদ আজম ||
‘সমাপ্তি’ গল্পের বাস্তবলিপ্ততা সম্পর্কে একটা দারুণ সাফাই-সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলছেন, অপূর্বের রুচি, চর্চা এবং সামগ্রিক মূল্যবোধকে আজকের দিনের অধিকাংশ পাঠক হয়ত কল্পলোকের আমদানিই মনে করবেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষাংশে এরকম যুবাপুরুষ বাংলা মুল্লুকে সত্যি সত্যি আবির্ভূত হয়েছিল। নীরদ চৌধুরীর জন্য মামলাটা অবশ্য গল্পপাঠ বা গল্পের বাস্তব-সম্পর্কিত নয়। তিনি উনিশ শতকের নবজন্মের এক নিষ্ঠাবান খাদেম। গভীরভাবে মনে করেন, কলকাতা পশ্চিমের সহযোগে এক নতুন বাঙালির জন্ম দিয়েছিল, যাকে হয়ত তাঁর নিজের আত্মপরিচয়মূলক ভাষ্য-অনুযায়ী বলা যায়, ‘একই সঙ্গে বাঙালি ও ইংরেজ’। উনিশ শতক সম্পর্কে অন্যরা কী মনে করেন আর তার সাথে এন সি চৌধুরীর অমিল কোথায় সে সম্পর্কে আলাপের জন্য এ মুহূর্তটা খুব প্রশস্ত নয়। তবে শুধু এ তথ্য দিয়ে রাখা যেতে পারে যে, তদীয় বন্ধু মোহিতলাল মজুমদার বা সুশীল কুমার দে-ও তাই মনে করতেন। শিথিলভাবে বললে বলা যায়, এটা খানিকটা ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকাগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ গোত্রের সখা ছিলেন। তবে এ সিদ্ধান্তে তাঁর বোধ হয় অতটা মর্জি ছিল না।
কথা হলো, নগর-নিবাসী অপূর্বের অপূর্ব রোমান্টিসিজম যদি উনিশ শতকের শেষাংশের কুললক্ষণ হয়, তাহলে ঘোর গ্রাম্য মেয়ে মৃন্ময়ীর জন্য তার প্রাণপাতও কোনো না কোনো বাস্তবে উনিশ শতকের কারবার হওয়ার কথা। বস্তুত নীরদের কথায় এ ব্যাপারে বাজি ধরা যায়। কারণ, উনিশ শতক সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক-না-হোক বিস্তর কল্প-বয়ানের বিপরীতে নীরদের বয়ানে পাই বলিষ্ঠ সব ঘোষণা আর বাস্তব। তিনি উনিশ শতকের বিবরণীকে বাঙালি বা বৃহৎ বাংলার কায়কারবার হিসেবে কখনো উপস্থাপন করেননি; কিংবা এ দাবিও করেননি যে, বাঙালির এ বিবরণী আবহমান কোনো বাঙালির চিত্র। তিনি জানতেন, এ এক নতুন বাঙালি, যেমন অংশত জানতেন বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ- স্থান-কাল-শ্রেণি-বর্ণ-শিক্ষা এবং এমনকি স্বভাব-চরিত্রে সম্পূর্ণ আলাদা ইংরেজি সাহিত্যের জঠর থেকে জন্ম নেয়া সে এক রকম বাঙালি মাত্র। অপূর্ব সত্যি সত্যি সেই নব্য বাঙালির অঙ্গীভূত নব্য যুবা।
এই যুবারাই কলকাতায় ‘নারীমুক্তি’র ব্যাপক আয়োজন করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী, তাতে নারীমুক্তি ঘটে নাই। ঘটার কথাও না। এ ধরনের কোনো মুক্তি যদি আলাদা করে থেকেও থাকে, তা নিশ্চয়ই গভীর সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই কেবল হতে পারত। কলকাতার সমাজে ঔপনিবেশিক শাসনের বালাই ছিল। তাদের সদর আর অন্দরের ভেদ ছিল। বৃহৎ সমাজের সাথে ‘আলোকপ্রাপ্ত’ লোকদের সংখ্যাসাম্য ছিল না। ফলে, ধরা যাক, ঠাকুরবাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে আলোকশিখার উদ্ভাসন যত সম্ভবপর ছিল, কলকাতার বিস্তীর্ণ সমাজদেহে তা পৌঁছানো অত সহজ ছিল না। কলকাতার সংস্কারবাদী নব্যদল সে চেষ্টাও বেশি করে নাই। ঔপনিবেশিক শাসন এবং উপনিবেশিতের মধ্যে জন্ম নেয়া সংস্কৃতি যতটা অনুমোদন করেছে, তার বাইরে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা নারীমুক্তির জন্য কাজ করেছে। এর মধ্যে বহুবিবাহ রোধের প্রকল্প বেশ অনেকদূর সফল হয়েছে। নতুন বিন্যাসে কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি এমনিতেই কোণঠাসা হয়ে ছিল। আইনি ব্যবস্থাপনায় তাকে ভালোমতোই সামলানো গেছে। কিন্তু বিধবা-বিবাহ চালুর আয়োজন শুরু থেকেই একটা ব্যর্থ প্রকল্প।
বলার কথাটা হলো, ইতিহাসের প্রায় সমস্ত বয়ানে ‘উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন’ বলে যে বস্তুর বিবরণী থাকে, একটু সীমিত করে এনে তাকে অনায়াসেই ‘ভদ্রলোক নারীর উন্নয়নে গৃহীত ভদ্রলোকদের উদ্যোগ’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বা নীরদচন্দ্র কথিত নব্য যুবাদের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ রীতিমতো দরকারি হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশিত সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিটির সদরে উপনিবেশায়নের নানা আয়োজন চলছিল। এ পশ্চিমায়নকেই আমরা আদর করে আধুনিকায়ন নামে ডেকে থাকি। কিন্তু নাম যাই হোক, বৃহৎ সমাজ দূরের কথা, ওই শ্রেণির অন্দরেই সে পশ্চিমায়নের ছটা প্রবেশের পথ পাচ্ছিল না। সারাদিনের কাজ সেরে স্নানের মধ্য দিয়ে বাবুটি ঘরের জন্য নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছেন, এ ধরনের বিস্তর বিবরণী সেকালের দ্বি-বিভাজিত জীবনের প্রতীকী বর্ণনা মাত্র। ইংরেজি সাহিত্য পড়ে জীবনের পাঠ নেয়া নব্য তরুণটির তো এ দ্বি-বিভাজনে চলতে পারে না। সে ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ আর জীবনচর্যাকে আদর্শ বলে শিখেছে। সে জীবনের সহচর হিসাবে স্ত্রীকে ভাবতে শিখেছে। নর-নারী সম্পর্কের যে ছকটিকে সে কল্পনার গাঢ় রঙে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, তার বাস্তবায়নের জন্য ‘মুক্তিপ্রাপ্ত’ নারী বিশেষ দরকার। নারীমুক্তির নানা উদ্যোগ-আয়োজন ছাড়া আসলে তার চলতেই পারে না। তাকে সরল চালু ভাষায় মাসিক পত্রিকা বের করতেই হবে, কারণ, বিদ্যায়তনে যে বিকট নতুন বাংলা তাকে নতুন মানুষ হওয়ার জন্য শিখতে হয়, ঘরের নারীদের তা শেখানোর কোনো কাঠামো সমাজে তখনো তৈয়ার হয় নাই। এত করেও উনিশ শতকে আসলে রোমান্স করার মতো তরুণী-সম্প্রদায় কলকাতা তৈরি করে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যস্থিত ‘নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ’ সেই করুণ বাস্তবতার মর্মান্তিক প্রকাশ। ‘সমাপ্তি’ গল্পে অপূর্ব-মৃন্ময়ীর আদিপর্বের আলাপের সাথে এ কবিতা মিলিয়ে পড়লে সে করুণ রোমান্সরসের ইতিহাস ও ভূগোল বেশ কতকটা উন্মোচিত হবে।
আমাদের অপূর্ব, গল্পের সাক্ষ্য মোতাবেক, এই নব্যতন্ত্রের বার্তাবাহক। সাময়িকপত্রের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা আর তোরঙ্গস্থিত রঙিন চিঠির কাগজ তার আংশিক সাক্ষ্য। বিয়ে তার কাছে সামাজিক যন্ত্রের অংশ হয়ে ওঠা নয়, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের সূত্রপাত বৈকি। কিন্তু কলকাতা, দেখা যাচ্ছে, তার জন্য অতটা অনুকূল হয়ে ওঠে নাই। বিয়ের এনতেজামটা সে কলকাতায় সারতে পারে নাই। গ্রামেই ফিরতে হয়েছে। এই বিয়েকে আমরা সাংস্কৃতিক-দার্শনিকভাবে অন্যরকম মহিমা দিতে পারতাম, যদি কোনো কারণে দুই আলাদা দুনিয়ার সংযোগ-সংঘাত গল্পের বিষয় হয়ে উঠত। তা হয় নাই। ইতিহাস বলছে, এরকম কিছু ঘটে নাই। কলকাতার নব্যরা এ ধরনের কোনো আকাঙ্ক্ষা রোমান্সমূলকভাবেও পোষণ করত না। আর রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও সেরকম কিছু ছিল না। নারী তাঁর কাছে ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের সমধর্মী সহচর মাত্র। পুরুষের সমান বা সক্রিয় এজেন্ট নয়। তাঁর নারীমূলকতা খুবই উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরুষের অস্তিত্বের বাইরে তা এমন কোনো সত্তা হাজির করে না, যা স্বাধীনভাবে সক্রিয় হবে। তাছাড়া সামাজিক পরিবর্তনে অ-আধুনিক গ্রামের কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তা-ও মনে করতেন না। তিনি গ্রামের উন্নতি চাইতেন। গ্রামবাসীর সক্রিয়তাও চাইতেন। কিন্তু যে কারণে বা যেভাবে তারা সক্রিয় হবে, তার নির্ধারণে গ্রামের হিস্যা নিশ্চিত করতে পারেননি। এরকম কোনো হিস্যা যে থাকতে পারে, তা-ও ভেবেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে অপূর্ব-মৃন্ময়ীর বিয়ে আসলে অপূর্বরই কারবার। মৃন্ময়ীর সর্বোত্তম বিকাশ সে পর্যন্তই হতে পারে, যতটুকু অপূর্বর আকাঙ্ক্ষার সীমা। যদি শুধু এটুকুতেই ‘সমাপ্তি’ শেষ হতো গল্প-রচনার যাবতীয় মুনশিয়ানা সত্ত্বেও আমরা তাকে অধিক মূল্য দিতে বোধ হয় পারতাম না। গল্পের নিপুণ বাজিকর রবীন্দ্রনাথ। দুনিয়ার সেরা লিবারেল হিউম্যানিস্ট সাহিত্যিকদের একজন তিনি। জীবন এবং মানুষ সম্পর্কে তাঁর ঝুলি নানা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ এবং আপনাতেই আবিষ্ট। তার দু-একটি মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করে তিনি গল্পটিকে শানিয়েছেন। তিনি গেছেন প্রকৃতির দিকে। এ প্রকৃতি সেই প্রকৃতি নয়। এটা শ্রেষ্ঠাংশে রাবীন্দ্রিক এবং কতকাংশে উনিশ শতকীয় কলকাত্তাই আমদানি।
এখানে আরেকবার নীরদ চৌধুরীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীরদের ‘বাঙালি জীবনে রমণী’ বইখানি যে উনিশ শতকীয় নব্যতন্ত্রের সাংস্কৃতিক আমলনামা তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। দোষের মধ্যে এই, ইনি বড্ড বেশি ত্যাড়া। তাঁর পক্ষপাত যেমন জোরালো, নাকচ করার ধরনও তেমনি তীব্র। উনিশ শতকের কলকাত্তাই সংস্কৃতিকে আবহমান বাঙালির সংস্কৃতি বলে চালিয়ে হাজার হাজার সন্দর্ভ রচিত হল। মিষ্টি করে আলগোছে এড়িয়ে যাবার এমন প্রতাপশালী রেটরিক দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বেচারা নীরদ স্বভাবদোষে তাতে শামিল হতে পারলেন না। তিনি কলকাত্তাই উনিশ শতককে আলাদা করে ফেললেন। ডায়াক্রনিকেলি বা খাড়াখাড়ি আলাদা করলেন। অর্থাৎ কালের দিক থেকে বিচ্যুতির ছবি আঁকলেন। সিনক্রনিকেলি বা আড়াআড়িও আলাদা করলেন। অর্থাৎ স্থানগতভাবে কলকাতা যে বাংলার অপরাপর অংশ থেকে বিচ্যুত হলো, তা জোরালোভাবে বললেন। তো, এই সংস্কৃতির সাথে বৃহৎ বাংলার কি সম্পর্ক নাই? সম্পর্ক যে আছে, সে কথাটা খোলাসা করে বলার জন্য বইটিতে লেখক আস্ত একটা অধ্যায় যোগ করলেন। বললেন, কলকাতার রূঢ় সংস্কৃতি যে অতটা মোহময় স্নেহাবেশ ধারণ করতে পারল, তার কারণ ওই বৃহৎ ‘অপর’- গ্রামবাংলার প্রকৃতি। নীরদ স্বভাবতই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পূর্ব বাংলার কথা বলেছেন। এখানকার পানি আর সবুজের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই পূর্ববঙ্গীয় সবুজ সজলতার প্রভাব বর্ণনা করে যথেষ্ট পরিমাণে সন্দর্ভ রচিত হয়েছে। ‘আধুনিক’ শাস্ত্রে ‘প্রকৃতি’কে ‘সংস্কৃতি’র বিপরীত শব্দ হিসেবে দেখা হলেও উক্ত কলকাত্তাই প্রকল্পে উহারা বিবাহসূত্রে পরস্পরের সন্নিহিত। যথাক্রমে নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে পরস্পরলগ্ন।
রবীন্দ্রসাহিত্যে, এবং ‘সমাপ্তি’ গল্পেও, প্রকৃতির বিচিত্র উপযোগ আছে। কতকাংশে তা দার্শনিক। আপাতত বলা যাক, ‘সমাপ্তি’ গল্প স্পষ্টতই উক্ত ‘সংস্কৃতি’ আর ‘প্রকৃতি’র সমন্বয়সূচক প্রকল্প। প্রকল্পটি কলকাতার নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে বাস্তব। কিন্তু বাস্তব স্থান আর কালের দিক থেকে কল্পিত। তাই এ গল্পের বাস্তবতায় একটা গভীর পরোক্ষতা আছে। এই পরোক্ষতা কলকাতার উনিশ শতকীয় সাহিত্যের সমধর্মী। মধুসূদনের পুরাণলিপ্ততা, বঙ্কিমের ইতিহাস-ভ্রমণ, আর রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকের প্রচণ্ডতায় উনিশ শতক বাংলা সাহিত্যে পরোক্ষ বাস্তবের যে স্বর্গরাজ্য তৈয়ার করেছিল, ‘সমাপ্তি’ আপাত ভিন্নতা সত্ত্বেও আসলে তারই সহোদর। একে আমরা বলতে পারি ‘গল্পের বাস্তব’। অন্যভাবে বলা যায়, বানানো বা বানোয়াট বাস্তব।
গল্পের রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সবচেয়ে বানোয়াট লেখক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফল রচনাগুলোর কোনো কোনোটি, যেমন চতুষ্কোণ, আরো বেশি বানোয়াট। তবে মানিকের বানানো গল্পে বাস্তবের অনুপুঙ্খ এতটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে যে, তাকে বাস্তবের গল্প বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ এমনকি তারও তোয়াক্কা করেন না। তাঁর বাস্তব ঠিক করাই থাকে। তিনি সেই বাস্তবের অনুকূলে পরিস্থিতি তৈয়ার করতে থাকেন। ‘বানোয়াট’ কথাটাকে নিত্য-প্রচলিত অর্থে না বুঝে এ লেখার বিশিষ্ট পরিভাষা হিসাবে বুঝলেই কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা যাবে। লেখকসত্তার অনুসন্ধানে শব্দটির তাৎপর্যও পরিষ্কার হবে।
মৃন্ময়ীর কথাই ধরা যাক। গল্পের জন্য মৃন্ময়ীকে মাটির মতো হতেই হবে। যে মাটিকে যত্নআত্তির দৌলতে ইচ্ছামতো- ‘মানবপ্রকৃতি’র বৃহৎ ছাঁচের মধ্যে অবশ্য গড়ে তোলা যাবে। সে হবে মাটিবর্তী, এবং প্রকৃতির মতো। সে অবশ্য খানিকটা বাঁকাও হবে। তাতে তাকে ‘সোজা’ করার বাড়তি গল্পরস পাওয়া যাবে। কিন্তু তার ‘বাঁকা’ হওয়াটা আরো দুই গভীর তাৎপর্য বহন করছে। একদিকে সে-যে সমাজের চাওয়া অনুযায়ী ছাঁচে গড়ে উঠেনি, সে সত্যটা খুব জরুরি। এই ছাঁচে পড়ে গেলে লেখকের কাঙ্ক্ষিত ক্ষত ছাঁচে পালটে নেয়া খুব সহজ হতো না। ভুললে চলবে না, মৃন্ময়ীর সমাজের ছাঁচ শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, অপূর্বর মনোলোকের বিরোধীও বটে। অন্যদিকে, সমাজসত্য মেনে না চলাটা মৃন্ময়ীর ওই অন্তর্নিহিত মনোগঠনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, যে মনের জোরে পরে তার বৃহৎ পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ, মৃন্ময়ী যে সমাজের মানুষ, সে সমাজের কাঠামোগত আর দশ উপাদানের সাথে তার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক কখনোই গড়ে ওঠেনি। লেখক তাকে আলাদা রেখেছেন। ওই সমাজ, ওই পরিবার আর ওই প্রকৃতি যৌথভাবে মৃন্ময়ীর জন্য ‘প্রকৃতি’র কাজই করেছে, সে নিজেই যে প্রকৃতির অংশ।
মৃন্ময়ী তুলনামূলক গরিব; সে কেবল এ কারণে যে, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের মেয়ে হলে তার দস্যিপনা কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু গরিবির আর কোনো ছাপ পুরো চরিত্রটির মধ্যে নাই। মৃন্ময়ী তার বয়সী মেয়েদের জন্য সমাজনির্দিষ্ট গতিবিধি মেনে চলে না বটে, কিন্তু তার এমন কোনো দোষের কথা বলা নাই, যা ভদ্রলোকের রুচির সীমা অতিক্রম করে যায়। তার সৌন্দর্যের কথাটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা হচ্ছে, ভালোমতো খেয়াল করলেই কেবল তার সৌন্দর্যের গভীরতা আবিষ্কার করা যায়। আবিষ্কারের জন্য যথাসময়ে অপূর্ব উপস্থিত হয়েছে। সমস্ত অন্তর্নিহিত সামর্থ্য নিয়ে মুক্তির যে অপেক্ষা সে অজ্ঞাতেই করছিল, তার অবসান ঘটেছে। সমাজ তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।
সময়মতো বিয়ে হলে বা বিয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকলে মৃন্ময়ীর মধ্যে চঞ্চলতার সাক্ষ্য পাওয়া যেত না। ফলে তার বাড়তি বয়সটা জরুরি। কিন্তু এজন্য তাকে কোনো ভার বইতে হয়নি। লেখক এ বাবদ দুপ্রস্থ কৈফিয়ত দিয়েছেন। এখানে রাবীন্দ্রিক কৌশল হিসাবে ‘হৈমন্তী’ গল্পের সাক্ষ্য নেয়া যেতে পারে। ওই তুরীয় গল্পে হৈমন্তীর বয়স বেশি হওয়া দরকার ছিল। লেখকের লক্ষ্য ছিল হৈমন্তীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। সেকালের সত্য অনুযায়ী কেবল ষোল পেরিয়ে গেলেই তা সম্ভব ছিল। এ বয়সী অনূঢ়ার জন্য লেখক কেবল দুটি কৈফিয়ত দিয়েই আমাদের- পাঠকদের বশে এনেছেন। বলেছেন, তারা ছিল পশ্চিমে। সেখানে সমাজের বালাই ছিল না। আর ঘরে মা-ও ছিল না। ফলে বয়সটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয় নাই। মৃন্ময়ীর ক্ষেত্রে রচনাকৌশলটা অনেকটা অনুরূপ। বলা হচ্ছে, তারা অন্য গাঁয়ের লোক। বছর দুতিন হলো এখানে এসে বসতি গেড়েছে। আর তার বাবা যেহেতু এখানে থাকে না, ফলে শাসন করার কেউ নাই। রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিটা বেশ মজার। বলেছেন, বাবা থাকলে শাসন করত না, এই ভেবে মা-ও তাকে যথেষ্ট ছাড় দিত। তো, এভাবে যে ‘অসামাজিক’ মৃন্ময়ী তৈরি হলো, তার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য উদার সমাজের ছবি এঁকেছেন। বলেছেন, এ মেয়েকে কেউ ঘরের বউ করার কথা ভাবেনি বটে, কিন্তু তার দস্যিপনাকে পাগলামি ভেবে তাকে স্নেহই করত। স্পষ্টতই সমাজ নামের কাঠামোটিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে বড্ড বেশি ছাড় দিয়েছেন। আসলে তিনি একে পাত্তাই দেননি। কারণ, এ সমাজ তাঁর নিজের সমাজ নয়। ‘হৈমন্তী’র সমাজ তাঁর কাছে এ ছাড় পায়নি। অন্য কারণটি অবশ্য এ গল্পের জন্য আরো বেশি জরুরি। তিনি সামাজিক বাস্তব বা অন্য কোনো বাস্তবের ছবি আঁকছেন না। বাস্তবায়ন করছেন তাঁর প্রকল্প। সামাজিক বাস্তবের ছবি সেখানে কেবল উৎপাতই তৈরি করত।
‘সমাপ্তি’র বিবরণ-কৌশল খুবই স্বতন্ত্র এবং খুবই রাবীন্দ্রিক। তার কারণ আগে বলেছি। এখানে আরেকবার বলা যেতে পারে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ কাজ করতেন, অন্তত গল্পে, প্রকল্পের বাস্তব নিয়ে, বাস্তবের প্রকল্প নিয়ে নয়। দ্বিতীয়ত, মানুষ সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা তা কিছুতেই পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বাস্তবতা বদলালে তাঁর মানুষদের বাইরের দিকটা পরিবর্তিত হয় কেবল, গভীর বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশেষ হেরফের হয় না। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বহুস্বরতা এত কম। এ কারণেই তিনি লেখক হিসাবে প্রায় সকল চরিত্রের পক্ষ হয়েই বাতচিত করতে পারেন। এ বিবরণ-কৌশলের সুলুক সন্ধানের জন্য অপূর্বর কনে-দেখা দৃশ্যের শরণ নেয়া যাক।
অপূর্ব বিয়ের পাত্রী দেখতে গেছে বাড়ির পাশেই। হিন্দুসমাজের পুরানা এবং নতুন নথিপত্র বলছে, এরকম খুব কমই ঘটে। সাধারণত পাঁজি-পুঁথি মিলিয়ে বিয়েটা দূরের সমাজেই হয়ে থাকে। কম ঘটে, কিন্তু এরকম ঘটা অসম্ভব নয়। যেমন অসম্ভব নয়, দুতিন বছর আগে কোনোপ্রকার পূর্বযোগ ছাড়াই অপূর্বদের বাড়ির পাশে এসে মৃন্ময়ীর বাবার বসতি স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ আসলে পুরো গল্পটি সাজিয়েছেন এরকম ঘটা-অসম্ভব-নয় ধরনের ঘটনার সহযোগে। কনে-দেখা দৃশ্যে লেখকের লক্ষ্য ছিল একটাই- পুত্তলিবৎ মেয়েটির পাশে চিত্তচাঞ্চল্যকর মৃন্ময়ীকে হাজির করে অপূর্বর পণকে পোক্ত করা। পণটা পোক্ত হওয়া দরকার। কারণ, তার মা কিছুতেই এ মেয়েকে ঘরে আনতে সম্মত হবে না। আবার মৃন্ময়ী অকস্মাৎ ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেই পারে, যেহেতু সম্ভাব্য পাত্রীটি রাখালের বোন। প্রথা ভেঙে অপূর্ব ও বাড়ি যাবে একা; কারণ ফেরার পথে তার একা থাকা দরকার। রাস্তাটি তখন জনবিরল থাকবে, গাছ-গাছালিতে সমাকীর্ণ থাকবে, অদ্ভুত হাস্যকরভাবে চলার মতো কর্দমাক্ত থাকবে। প্রকৃতির কন্যা মৃন্ময়ী প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে অকস্মাৎ কর্দমাক্ত রাস্তায় উপস্থিত হবে। অপূর্ব তাকে ধরেও ফেলবে। এবং তখন মেঘ-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সূর্যের একফালি আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মৃন্ময়ীর মুখে পড়ে তার ভিতরদেশ পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় প্রাণবন্ত করে তুলবে।
‘সমাপ্তি’ গল্পের বয়ানকৌশল সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, প্রকল্পের বাস্তবসম্মিতির জন্য এতে যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তা-ও প্রকল্পিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসও বাস্তবের গল্প নয়, গল্পের বাস্তব। কিন্তু সেই বাস্তব প্রকল্পিত নয়। মেলা থেকে ফেরার পথে রাতে তেঁতুলতলার আঁধারে কুবের ও কপিলাকে খানিক নিরিবিলি সময় দেয়ার জন্য মানিকের যে এনতেজাম, তার সাথে অপূর্ব-মৃন্ময়ীর পূর্বোক্ত সাক্ষাৎপর্বের তুলনা করলেই পার্থক্যটা বোঝা যাবে। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছিলেন, এ গল্পের কল্পনাও কল্পলোকের আমদানি। কথাটা গভীর অর্থে আসলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প সম্পর্কে সত্য।
শৈলির ভিতরকাঠামোর তল্লাশে এবার গল্পটির ‘বাবা’ প্রসঙ্গ টানব। ‘বাবা’ কথাটার নানা প্রতীকী তাৎপর্য আছে; সমাজবিদ্যা আর মনোবিদ্যায় এর নানারকম ব্যবহার আছে। আমরা সেগুলো আংশিকভাবে ছুঁয়ে যাব। আমরা দেখব, গল্পটিতে আমাদের বড় পিতা রাষ্ট্র হাজির নাই। তখন হয়ত আমাদের মনে পড়বে, উপনিবেশিত কলকাতার সাহিত্যে প্রতাপশালী বাবা চরিত্রের খুবই অভাব। যে সমাজের কর্তৃত্ব পশ্চিমায়িত নবীন যুবাদের হাতে, তার বাবা চরিত্র দুর্বলই হওয়ার কথা। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার কথা। রাষ্ট্রের জায়গা নেয়ার কথা সমাজ। এবং প্রায় যে কোনো উপস্থাপনায় সমাজের হওয়ার কথা প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ, ক্রিয়া চলে গেছে অন্যের হাতে। আর এ বাস্তবতার প্রভাব পড়ার কথা বাস্তবের বাবা চরিত্রের উপর। অথবা অন্য সবকিছু বাদ রেখে কেবল অপূর্বর বাবাকেও খোঁজা যেতে পারে। দেখা যাবে, অপূর্বর বাবা নেই। প্রত্যক্ষভাবেও নাই, পরোক্ষভাবেও নাই। বাবা যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পরিবারটির কোনো আর্থিক টানাপড়েন নাই। বাবার দিনের বিষয়-আশয় নিশ্চয়ই ওই সচ্ছলতার উৎস। কিন্তু এখন যখন অপূর্ব সমাজের চাল ভাঙতে উদ্যত, তখন সমাজের পক্ষ হয়ে বাবার বিরোধটুকুও তাকে সামলাতে হয় না। বিস্তারে না গিয়ে এখানে শুধু ইঙ্গিত দিয়ে রাখি, উপনিবেশিত সমাজের কাঠামোগত সংস্কার বাপ-বেটার সম্পর্কহীনতার কারণেই সম্ভবপর হয় না। বাপের সাথে সম্পর্ক যদি হয় ঘৃণার তাহলেও পুত্রের ব্যক্তিগত মুক্তি সম্ভব। পশ্চিমাগত আলো সে মুক্তির উৎস। কিন্তু পিতা-পুত্র বিরোধের সিনথেসিসে পিতার ন্যায্য হিস্যা যদি না থাকে তাহলে সামষ্টিক মুক্তি অসম্ভব। ‘সমাপ্তি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পের সাথে মৃন্ময়ীর সমাজের কোনো যোগ ছিল না। এ কারণে তিনি এই সমাজকে এমনকি ভিলেন হবার সম্মানটুকুও দিতে চাননি। অপূর্বর মা পিতার পক্ষ হয়ে বা সমাজের পক্ষ হয়ে খানিকটা লড়েই হার মানেন। গভীরভাবে প্রবেশ করেন পারিবারিক সম্পর্কে- আবেগই যে সম্পর্কের মূলকথা। আর মৃন্ময়ীকে তো সমাজে প্রবেশই করতে হয়নি। তার নিরীহ পিতা বাড়ি বদল করেই সমাজের গ্রাস এড়াতে পেরেছেন। মা এড়িয়েছেন পিতার বরাতে। সমাজ-পিতার অনুপস্থিতিতে মৃন্ময়ী অরক্ষিতই ছিল। অরক্ষিত মৃন্ময়ীকে অপূর্ব ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে গেল কলকাতায়। ছিনিয়ে নিতে গেলে সমাজে যে কাঁপন উঠত, এ গল্পের জন্য তার কোনো দরকার ছিল না।
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিলিপ্ততা দার্শনিক মেজাজের; রোমান্টিক আন্দোলনের দার্শনিক উপলব্ধি তাতে প্রবল। তাঁর প্রকৃতি বিশেষ রূপে মূর্ত হয় না, নির্বিশেষ অস্তিত্বে কার্যকর হয়। কনে দেখে ফেরার পথে অপূর্বর সাথে মৃন্ময়ীর দেখা হয়েছিল যেখানে, সে পথটির আবরুর জন্য গাছ-গাছালির সম্মিলন দরকার ছিল, কিন্তু বিশেষ কোনো গাছ বা গাছ-গাছালির বিশিষ্ট কোনো বিন্যাসের প্রয়োজন হয় নাই। অপূর্ব মৃন্ময়ীকে নিয়ে নৌকাভ্রমণের সময়ে মৃন্ময়ীর কৌতূহলের জবাব দিচ্ছিল। লেখক বলছেন, অপূর্ব তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা বলেছে; মুনশেফ আদালতকে জমিদারি কাছারি বলেছে। এতে এ গল্পের ভাবগত ক্ষতি হয় নাই। কারণ, মৃন্ময়ীর উল্লাস আর অপূর্বর লিপ্ততা প্রকাশের জন্য ওই নির্বিশেষ সক্রিয়তাই যথেষ্ট ও যথার্থ ছিল।
দেখা যাচ্ছে, বাস্তবরসের দিক থেকে প্রকল্পিত বাস্তবের অসামান্য ব্যবহার সত্ত্বেও ‘সমাপ্তি’ গল্পের আয়োজনে ঘাটতি আছে। কিন্তু গল্পরসের জোগানে তার সিদ্ধি অসাধারণ। ভাষার লাবণ্য এর এক কারণ। সে লাবণ্যেরও উৎস আইডিয়া বা ভাবের সমুন্নতি। বস্তুত লিবারেল হিউম্যানিস্ট চর্চায় মানুষ সম্পর্কে যেসব ধারণা গড়ে উঠেছিল তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেছিলেন, নব্য কলকাতার প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা করেছিলেন, এবং বৃহৎ বাংলার প্রকল্পিত বাস্তবে নিপুণভাবে স্থাপন করেছিলেন। ‘সমাপ্তি’ তার একটি নমুনা মাত্র।
রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, মানুষ প্রাকৃতিক অস্তিত্ব। মানুষের সম্ভাবনা অসীম। প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হলে তার সেই অসীম সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। অথচ তাকে সামাজিক ভাষা রপ্ত করে সাংস্কৃতিক হয়ে উঠতে হয়। এই ভাষা স্বভাবতই জবরদস্তিমূলক। পারিবারিক সম্মতির মধ্যে কমবয়সীরা সেই জবরদস্তি থেকে কিছুটা রেহাই পেতে পারে। বিয়ের মধ্য দিয়ে, প্রধানত মেয়েদের, সামাজিকায়নের একটা অচেনা পর্ব শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ায় পারিবারিক সম্পর্কের আবেগ ও আনুকূল্য সাধারণত অনুপস্থিত থাকে বলে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে। মৃন্ময়ীর বিকাশ এদিক থেকে আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে। তার শৈশব সামাজিক ভাষা রপ্ত করার জবরদস্তি থেকে মুক্ত ছিল। ফলে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো সতেজ ছিল। সামাজিক ভাষার ফরমায়েশ অনুযায়ী সেগুলো নিজের ইচ্ছা ও মর্জি-নিরপেক্ষভাবে গড়াপেটা হয়নি। অবস্থাটা বিবাহ-পরবর্তী সামাজিকায়নের জন্য বিপজ্জনক হতে পারত। অপূর্বর জীবনবোধের ঔদার্যের কারণে তা হয়নি। অপূর্ব ধৈর্য্য, সহমর্মিতা এবং আনুকূল্য দেখিয়েছে। এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার, অপূর্ব মৃন্ময়ীকে শিক্ষা দেয়নি। সমস্ত সম্ভাবনা মৃন্ময়ীর মধ্যেই ছিল। আনুকূল্য পেয়ে যথাকালে মৃন্ময়ী প্রাকৃতিক দশা থেকে সাংস্কৃতিক দশায় উপনীত হলো। তার এ বদল নিপীড়নমূলক না হয়ে সম্মতিমূলক হয়েছিল।
মৃন্ময়ীর এই রূপান্তরই ‘সমাপ্তি’র মূল গল্প। বাকি অংশ গল্প শেষ করার মুনশিয়ানা মাত্র। তার আয়োজনটিও হয়েছে সাজানো-গুছানো। একটি চুম্বনের আবদার অসমাপ্ত ছিল। নীরব অভিমান আর স্থানগত দূরত্ব ছিল। ছিল ভগ্নি আর ভগ্নিপতি, যাদেরকে এমনকি অপূর্বর বিয়ের আয়োজনেও দেখা যায়নি। আর সেরাতে ঝড়বৃষ্টি ছিল, অন্ধকারের আড়াল ছিল। তার মধ্যেই বহিরঙ্গীয় হাসির বদলে অন্তরঙ্গ কান্নার মধ্যে গল্পটি শেষ হলো। বলা যায়, এ বাস্তবের সামঞ্জস্য নয়, বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ নিটোল বাস্তব।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/৮ মে ২০১৮/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন