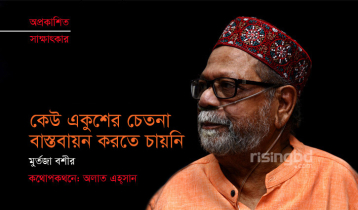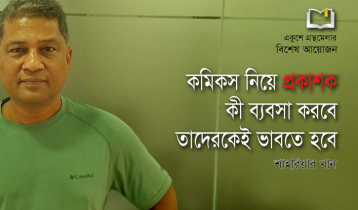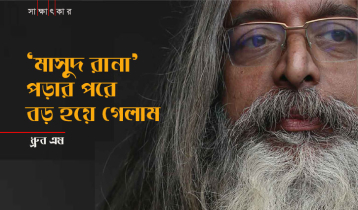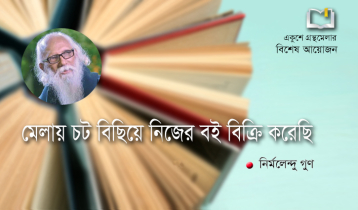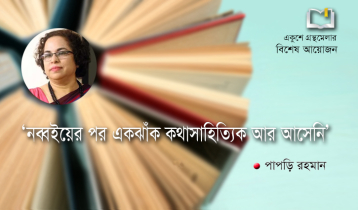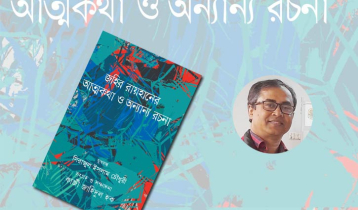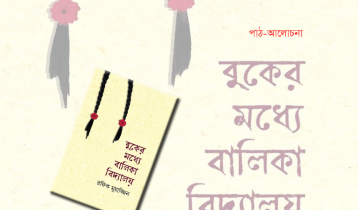আমার মা শুকতারা জলদাসী || হরিশংকর জলদাস
হরিশংকর জলদাস || রাইজিংবিডি.কম

আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে- আমার মাকে নিয়ে আমি তেমন কিছু লিখিনি। আমার ঠাকুমা, ঠাকুরদা বা বাবাকে নিয়ে যেরকমভাবে লিখেছি আমি, সেরকম করে মায়ের প্রসঙ্গ আসেনি আমার লেখাজোখায়। অর্থাৎ আমার লেখায় পিতামহ, বাবা এবং ঠাকুমা যে প্রত্যক্ষতায় উপস্থাপিত হয়েছেন, সে তুলনায় মা অপ্রত্যক্ষ রয়ে গেছে।
এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয়। তবে এটাও সত্য নয় যে, মাকে নিয়ে আমি কিছু লিখিনি। এটা সত্য যে, মা প্রত্যক্ষভাবে মানে স্বনামে আমার গল্প-উপন্যাসে স্থান পায়নি। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ অন্য নামে আমার কথাসাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে আমার মা বিপুলভাবে আছে। ‘জলপুত্রে’র সুমিত্রা আর ‘দহনকালে’র বসুমতী চরিত্র দুটো তো আমার মায়ের আদলে তৈরি করেছি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই আমার বাপের বিয়ে হয়। বাবা যুধিষ্ঠিরের বয়স তখন বাইশ কি তেইশ। আর মা শুকতারা তখন দশ ছুঁইছুঁইয়ের বালিকা। কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, বিয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স বাইশ বছর সাত মাস আর ভবতারিণী দেবীর নয় বছর নয় মাস। এটা কোনো তুলনা নয়, শুধু বয়সের সাজুয্যের হিসেব।
বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবার পর যুধিষ্ঠির এবং শুকতারার বিয়ে হয়েছিল। জেলেসমাজে ছেলের বিয়ে হতো আঠারো থেকে বিশের মধ্যে আর কন্যাদের নয় বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়ে যেত। শুকতারা এবং যুধিষ্ঠির উভয়ের দেরিতে বিয়ে হবার কারণ ছিল।
কক্সবাজার থেকে মিরসরাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে জেলেপল্লি। কর্ণফুলী এই জেলেপল্লিগুলোর মধ্যে বিভাজন এনেছে। উত্তরভাগ আর দক্ষিণভাগ। কর্ণফুলীর মোহনার উত্তর অংশে পড়ে পতেঙ্গা থেকে মিরসরাইয়ের জেলেপাড়াগুলো। আর দক্ষিণাংশে টেকনাফ থেকে আনোয়ারার জেলেপল্লিগুলো পতেঙ্গার পাঁচ গ্রাম পরেই উত্তর কাট্টলি গ্রাম। এই গ্রামের কৈর্বতপাড়াটি জনসংখ্যায় এবং আয়তনে বিশাল। এই পাড়ারই বহদ্দার রসিকচন্দ্র পাতর। তাঁর স্ত্রী চন্দ্রকলা পাতর। ছয়জন সন্তান তাঁদের ঘরে- তিন পুত্র, তিন কন্যা। পুত্ররা হলেন- যোগেশচন্দ্র, শোগেন্দ্র ও মহিমচন্দ্র। মেয়েদের নাম বিমলা, উত্তরা এবং শুকতারা। শুকতারা রসিকচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। শুকতারার বয়সী পাড়ার অন্যান্য কুমারী মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেও শুকতারার বিয়ে হয় না। শুকতারার বয়স নয় পেরিয়ে দশ ছুঁইছুঁই। এত বয়সী মেয়ের বিয়ে হয় না, এ বড় লজ্জার ব্যাপার। রসিকচন্দ্র আর চন্দ্রকলার মুখ-লুকানোর মতো অবস্থা। বরপক্ষ আসে আর যায়। বাপের নাও-জাল আছে, কালি দইজ্যার নৌকা আছে, সাগরের ঢেউ ধরে রাখার হিম্মতওয়ালা তিন তিনটা ভাই আছে শুকতারার, তারপরও তার বিয়ে হয় না। বরপক্ষের সবকিছু পছন্দ- রসিকচন্দ্রের ঘরবাড়ি পছন্দ, অর্থনৈতিক অবস্থা পছন্দ, কন্যাকেও পছন্দ, তারপরও তারা ফিরে যায়।
কেন? পাকা কথা দেওয়ার আগে আগে ভাবি বউদি বা শাশুড়ির চোখ পড়ে যে, শুকতারার শরীরের বিশেষ একটা স্থানে! ওই খুঁতটা দেখেই বরপক্ষের ইতস্ততা শুরু হয় এবং আস্তে করে সটকে পড়ে তারা রসিকচন্দ্রের বাড়ি থেকে। শুকতারার শরীরে এমন কী খুঁত যে, সবকিছু পছন্দের হওয়া সত্ত্বেও বরপক্ষ পিছিয়ে যায়?
শুকতারার গলায়, ঠিক কণ্ঠের নিচ-বরাবর, একটা বৃত্তাকার পোড়া দাগ। এ কিসের দাগ! এ দাগ যে দৃশ্যমান! শরীরের অন্য কোথাও এ দাগ হলে মেনে নেওয়া যেত, চোখের আড়ালেই থাকত। বিয়ের পর পাড়াপড়শিরা বলবে- অমুকের বাপ ছেলের জন্য একটা পোড়াবউ এনেছে। তাছাড়া এ কিসের দাগরে বাবা! জেলেসমাজে দুর্মুখের তো অভাব নেই! তাই সব বরপক্ষ পিছু হাঁটে। কিন্তু পরানেশ্বরী আর জগৎহরি পিছু হাঁটলেন না। সবকিছু দেখে-শুনে তাঁরা যুধিষ্ঠিরের জন্য শুকতারাকে নির্বাচিত করলেন।
কিন্তু জগৎহরির স্ত্রী জগতেশ্বরী ননদিনী পরানেশ্বরীর কানে মুখ চেপে বললেন, ‘আঁর একখান কথা আছে অ বদ্দি। মাইয়াপোয়া হিবার গলার নিচে পোড়া দাগ!’
কনে দেখতে বের হবার সময় জগতেশ্বরী পরানেশ্বরীদের সঙ্গে এসেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ভাইনার বউ চাইতা যাইবা, আঁরে ছাড়া!’
শুকতারার মা চন্দ্রকলা সামনে ছিলেন। তিনি জগতেশ্বরীর দেহভঙ্গি বুঝলেন। এতদিনের বেদনা মনের মধ্যে গুমরে মরছিল চন্দ্রকলার। আজকে সেই হাহাকারটা বের করে দেওয়ার সুযোগ পেলেন তিনি। সবাইকে উদ্দেশ্য করে করুণ কণ্ঠে বললেন, ‘আঁর মাইয়ারে বিয়া গরাও নো গরাও, হিয়ান তোঁয়ারার বেপার। কিন্তুক আঁর মাইয়ার গলার দাগর বিবরণ আঁই ইক্কিনি তোঁয়ারার কাছে দিতাম চাইর।’
আগতরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন।
বিবরণটা এরকম। চন্দ্রকলা পাতর বহুপ্রসবা। একটার পর একটা সন্তান আসে। ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত মন চন্দ্রকলার। শুকতারা জন্মাল। শীতের দিনেই জন্মেছিল শুকতারা। মাঘের শীত অসহনীয়। শুকতারার বয়স মাস তিনেক চলছে। রাতে শীত দুঃসহ হয়ে উঠলে চন্দ্রকলা শুকতারাকে কোলে নিয়ে মালসায় আগুন পোহাতে বসলেন। মালসায় গনগনে আগুন। শিরীষকাঠের আগুন বড্ড বেশি তাপ দেয়। একটা সময়ে চন্দ্রকলার চোখে ঝিমুনি এল। ঝিমুনি থেকে গাঢ় ঘুম। চন্দ্রকলার দেহ অবশ হল। এই ফাঁকে শুকতারা ঝুপ করে চন্দ্রকলার কোল থেকে মালসায় পড়ে গেল। চন্দ্রকলা সংবিতে ফিরে দেখলেন- শুকতারা মালসাতে মোচড়ামুচড়ি করছে। ভাগ্যিস গায়ে-গতরে কাঁথা জড়ানো ছিল! গা পুড়ল না। কিন্তু একটা জ্বলন্ত কয়লা শুকতারার গলাটা ছুঁয়ে দিল। অগ্নিদেবতার ছোঁয়া বলে কথা। বহুদিন কষ্ট পেল কোমল শিশুটি। সেরে উঠল একদিন। কিন্তু গলার নিচে পোড়া দাগটা থেকে গেল সারা জীবনের জন্য।
চন্দ্রকলার সব কথা শুনে পরানেশ্বরী বললেন, আমার বাপমরা ছেলে। অনেক কষ্টে ভাই জগৎহরির সহযোগিতায় যুধিষ্ঠিরকে বড় করেছি। নিজেদের ঘরবাড়ি থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ডামাডোলে এখন আমরা বাস্তুহারা। গাঁ ছেড়ে বাপের বাড়িতে থাকছি তোমরা। তোমাদের তুলনায় আমরা নিতান্ত গরিব। তারপরও মেয়ে দিতে রাজি হয়েছো, এতেই আমরা খুশি। তা বেয়াইন, বিয়েটা কবে নাগাদ হতে পারে?
রসিকচন্দ্র বললেন, ছেলের মতামত...।
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পরানেশ্বরী বললেন, ছেলে আমার বড়ই ভালো। আমার কথা সে ফেলবে না।
জগৎহরিও দিদির কথায় সায় দিলেন। এই-ই হল শুকতারার দেরিতে বিয়ে হবার কাহিনী।
১৯৪৫-এর সামান্য আগুপিছু সময়ে যুধিষ্ঠির-শুকতারার বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল। আমার জন্মের আগে এই দম্পতির দুটো সন্তান জন্মেছিল- একটা ছেলে, অন্যটা মেয়ে। ছেলের নাম হরিপদ আর মেয়ের নাম ইন্দ্রবালা। চট্টগ্রাম শহরের মাইজপাড়াতেই জন্মেছিল তারা। কিন্তু তারা বেশিদিন বাঁচেনি, অকালে মরেছিল। জগৎ সংসারে যুধিষ্ঠির-শুকতারা দম্পতি হরিপদর বাপ আর মা নামে খ্যাত হয়েছিল।
নাতি-নাতনিকে হারিয়ে পরানেশ্বরী তো উন্মাদপ্রায়। তাঁর বিশ্বাস জন্মাল- মাইজপাড়াটা অলক্ষুণে। এখানে থাকলে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের কেউ-ই বাঁচবে না। সিদ্ধান্ত নিলেন, ছেলে আর ছেলেবউ নিয়ে স্বামীর ভিটায় ফিরে যাবেন। যুদ্ধশেষে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার প্রায় সবাই ফিরে এসেছে, শুধু তাঁরা বাকি ছিলেন।
একদিন শুকতারা তার শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করল। এটাই শ্বশুরবাড়িতে শুকতারার প্রথম আসা।
১৯৫৩ সালের ৪ মে আমি জন্মালাম এবং টিকে গেলাম। বুদ্ধি হবার পর আমি দেখেছি- আমার গলায়-কোমরে-বাহুতে নানা মন্ত্রপূত দড়িদড়া, তাবিজ-মাদুলি। শুধু তা-ই নয়, আমার ডানকানের লতি ফুঁড়িয়ে সেখানে সোনার বালি লাগিয়ে মা-বাবা ক্ষান্ত হয়েছিল। এর কারণ মাকে জিজ্ঞেস করলে মা বলেছিল, ওসব তুমি বুঝবে না। আমার চাপাচাপিতে মা একদিন মুখ খুলেছিল- শনির দৃষ্টি তোমার ওপর না পড়ার জন্যই ওসব করানো হয়েছে। মৃত্যুর দেবতা যে শনি নন, যম; সেদিন আমি যেমন জানতাম না, আমার মা-বাবা-ঠাকুমাও নিশ্চয়ই জানতেন না। সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাবা ছিল অনাধুনিক। একের পর এক করে এগারোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে বাবা মায়ের গর্ভে। তিনজন মরেছিল, আমরা আটজন বেঁচে ছিলাম। জীবিতদের মধ্যে আমি বড়। জীবনের অনেকটা দিন মায়ের আতুড়ঘরে কেটেছে।
সন্তান-সম্ভবা অবস্থাতেও দুহাতে সংসারের নিত্যদিনের কাজ সম্পন্ন করে গেছে মা। মা খুব ভোরে উঠত। অনেক বড় উঠান আমাদের। মায়ের দিনের প্রথম কাজ ছিল ওই মস্তবড় উঠানটি ঝাঁট দেওয়া। তারপর জল ছিটিয়ে উঠানটি আধ-ভেজা করে দেওয়া, কুড়ানো জঞ্জালগুলো খালের ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলা, উঠানের চুলাটি গোবর-মাটিতে লেপা- এসব আমার মা শুকতারাকে বাচ্চাকাচ্চা জেগে উঠার আগেই সেরে ফেলতে হতো। বাপের তাগিদে তাকে তখন তখনই রান্নাঘরের দিকে ছুটতে হতো। পান্তাভাত না হলে যে যুধিষ্ঠির সমুদ্রের দিকে রওনা দিতে পারছে না!
আমরা বিছানা ছেড়ে উঠার পর দেখতাম- মা পুকুরঘাটে বাসনকোসন মাজছে। হাঁড়ি-পাতিল-ডেকচি-গেলাস- এসব মাজা শেষ করে মা যখন ফিরত, মা তখন আধ-ভেজা। এরপর ছোটছাটকাদের হাতমুখ ধোয়াতে ধোয়াতে, তাদের দাঁত মাজাতে মাজাতে, পিঁচুটি-সর্দি পরিষ্কার করে মাথায় একটু চিরুনি বুলিয়ে দিতে দিতে পুবাকাশে সূর্য দুই বাঁশ পরিমাণ উঠে যেত। আমাদের সামনে পান্তাভাতের থালা এগিয়ে দিতে না দিতেই শাশুড়ি পরানেশ্বরীর তাগাদা কানে যেত শুকতারার, ‘ও বউ, খাড়াং আর তক্তাঘান দও। পাইল্যে দুয়া পানিভাত দও। দইজ্যাত্ যাওনর সময় অইয়ে।’
ঠাকুমা আমার সমুদ্রকূলে গিয়ে অন্য বহদ্দারের কাছ থেকে মাছ কিনে মাথায় করে পাড়ায়-মহল্লায়-হাটে-বাজারে বেচতেন। বাবা এগারোজন মানুষের হাঁ-করা মুখে অন্ন জোগানোর হিম্মত রাখত না। বাবার কোনো নৌকা-বিহিন্দি জাল ছিল না। ওগুলোর মালিক পয়সাওয়ালা জেলেরা। বাবা ছিল নিতান্ত দরিদ্র জেলে। তার বেঁচে থাকার সম্বল ছিল টাউঙ্গা জাল আর হুরিজাল। সমুদ্রকূলে আর খালে-বিলে ওই জাল ঠেলে ঠেলে মাছ ধরত বাবা। এই মাছের পরিমাণ কম। কম মাছের টাকা দিয়ে সংসার চলত না।
আমার মা রূপসী ছিল না। তবে একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো চেহারাও ছিল না মায়ের। মাঝারি হাইট, মাথাভর্তি চুল। চোখ দুটো প্রখর নয়। তবে ভালোবাসার গভীর একটা ছায়া মায়ের দু’চোখের তারায় তারায় খেলা করত দেখতাম আমি। একটু ফর্সার দিকেই গায়ের রং ছিল মায়ের। তবে তার ত্বকে লাবণ্য দেখিনি কোনোদিন। স্বামীঘরের অভাব তার দেহলাবণ্যকে চুষে নিয়েছিল। এত বড় বহদ্দারের মেয়ে শ্বশুরবাড়ির দারিদ্রকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল।
১৯৭৪-এ আমাদের পরিবারে চরম দারিদ্র নেমে এসেছিল। এর বছর দুয়েক আগে মায়ের একমাত্র অলঙ্কার গলার হারটি পাঁচশ টাকায় বেচে একটা আধ-পুরনো বিহিন্দি জালের মালিক হয়েছে বাবা। মনোরঞ্জন বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা নাইয়াও হয়েছে। আমরা ভাইবোনেরা দুইবেলা পেট পুরে ভাত খেতে পারছি।
১৯৭৪-এর এক সকালে কাঁদতে কাঁদতে বাবা সমুদ্র থেকে ফিরল। উঠানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, ‘মা, মারে! আঁরার সর্বনাশ অইয়ে। আঁরার বিহিন্দি জাল চোরে লই গেইয়ে গই।’
বাপ যুধিষ্ঠিরের কাঁধে আবার হুরিজাল উঠল। ঠাকুমা সকাল-সন্ধ্যা-দুপুরে মাছের খাড়াং মাথায় চাপিয়ে আবার বলতে শুরু করল- মাছ লইবা না মাছ? এরপর এল ১৯৭৫। খাদ্যাভাব আমাদের পরিবার নয় শুধু, গোটা জেলেপাড়ার ওপর জগদ্দল পাথরের ভার নিয়ে চেপে বসল। সমুদ্রেও মাছ কমে গেল। বহদ্দাররা দুবেলা কোনোরকমে খেতে পেলেও সাধারণ জেলেদের উনুন জ্বলে না। অনেক জেলেনারী, যারা কোনোদিন পাড়ার বাইরে বের হয়নি, তারা মাছবেচায় নেমে পড়ল। বাপ আর ঠাকুমার আয়ে পরিবার আর চলে না। এই সময় মা একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়ে বসল। ঠাকুমাকে বলল, ‘মা, সংসার তো অচল অই যার গই। আষ্টজন পোয়া-মাইয়া ঘরত্। আঁই অ বাইর অই মা মাছ বেইচত্তাম?’
বাবাও উপস্থিত ছিল সেখানে। বাবা চুপ মেরে থাকলেও ঠাকুমা ঝরঝর করে কেঁদে দিলেন। বললেন, ‘তুই আঁর বউ নো, আঁর মাইয়া। এই কণ্ঠত্ পরাণ থাইকতে আঁই আঁর মাইয়ারে বাজারত্ পাডাইতাম নো। দরকার অইলে নো খাই মইয্যম। দরকার অইলে ভিক্ষা গইয্যম।’
ঠাকুমার অবস্থা দেখে মা সেদিন পিছু হটেছিল। ওই দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের প্রতিবেলা চাল লাগত আড়াই সের। কিন্তু দুর্মূল্যের বাজারে আড়াই সের চাল জোগাড় করার হিম্মত ছিল না বাপ আর ঠাকুমার। কোনোবেলা এক সের, কোনো বেলা দেড় সের চাল জোগাড় হতো।
সকালের ঘরকন্নার কাজ সেরে মা একটা টুকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। টুকরিকে জেলেরা বলে ভাইর। ঘণ্টাখানেক দেড়েকের চেষ্টায় মা পুকুর পাড় থেকে হিলঞ্চি শাক তুলে ভাইরটা ভর্তি করে ফেলত। দুপুরে সব ভাইবোন দাওয়ায় সারি করে বসতাম ভাত খাওয়ার জন্য। মা পাতে এক মুষ্টি দুই দুষ্টি করে ভাত দিয়ে যেত। ছোট যারা তাদের ভাগে ভাতের পরিমাণ বেশি থাকত। তারপর ভাতের পাশে শাক দিয়ে যেত মা। শাকের পরিমাণ ভাতের চেয়ে ৩/৪ গুণ বেশি। আমরা ভাত দিয়ে শাক খেতাম না, শাক দিয়ে ভাত খেতাম। মাঝেমধ্যে পাতে এক চামচ পাতলা ডালও পড়ত। খেসারির ডাল খাওয়া হতো আমাদের বাড়িতে। খেসারি ডালের দাম তখন সের প্রতি বারো টাকা। শাশুড়ি-স্বামীকে খাওয়াতে খাওয়াতে বেলা গড়িয়ে যেত পশ্চিমে। সবার শেষে মা খেতে বসত। খেতে মা খুব বেশি সময় নিত না। খাওয়া শেষে মুখে একটা পান পুরে চিবাতে চিবাতে হাসিমুখে উঠানে এসে দাঁড়াত।
এইভাবেই চলেছিল অনেকদিন। একদিন আমার সন্দেহ হলো- মা এত তাড়াতাড়ি খায় কী করে! আর খায়ই বা কী! মায়ের সামনে এক বিকেলে কথাটা পাড়লাম। মা প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, তোরা যা খাস, তা-ই খাই বাপ। বলতে গিয়ে মায়ের মুখটা কি একটু ম্লান হয়েছিল, নইলে আমার সন্দেহ হয়েছিল কেন? আমি তখন বলেছিলাম, মা সত্যি করে বল তো, তুমি পেট পুরে খাও?
মা চুপ মেরে থেকেছিল। ওইদিন আমি আর কথা বাড়াইনি। পরদিন মা খেতে বসলে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। দেখেছিলাম, চামচের আগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মা ভাতের ডেকচির তলা থেকে এক মুষ্টি পোড়া ভাত বের করল আর পাতিল থেকে নিল শাক। ওগুলো তাড়াতাড়ি মুখে গুঁজে দিয়ে এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। খাওয়া শেষ হলে হঠাৎ আমার ওপর চোখ পড়ল মায়ের। মা চমকে উঠল। তারপর ভেবাচেকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মা শুকতারা। করুণ কণ্ঠে মাকে বললাম, মা, তাহলে এই-ই তোমার পেট পুরে ভাত খাওয়া!
কোনোদিন মাকে ভালো শাড়ি পরতে দেখিনি আমি। আমি যখন আয়-সক্ষম হলাম, মাকে ভালো শাড়ি কিনে দেওয়ার ক্ষমতা হল আমার, তখন বাপ মারা গেছে। মা তখন রঙিনপাড়ের ধুতিপরা শুরু করেছে। ভালো দামি শাড়ি পরার সাধ মায়ের সারাজীবন অপূর্ণই থেকে গেছে। তবে পুজোপার্বণে বিশেষ করে দুর্গাপুজোয় মা নতুন শাড়ি পরত। তবে তা দামি নয় মোটেই। এতগুলো ভাইবোনকে জামাকাপড় কিনে দেওয়ার পর অবশিষ্ট যা টাকা থাকত সেই টাকা থেকে নিজের মায়ের জন্য ধুতি কিনত যুধিষ্ঠির, অবশিষ্টাংশ দিয়ে শুকতারার শাড়ি এবং নিজের জন্য যা একটা কিছু। দুদিনেই মায়ের ওই শাড়ির রং চটে যেত। সস্তা শাড়ির রং আর কতটুকুই বা পাকা।
সেসময় বাজারে তিব্বত স্নোর খুব চল ছিল। লাক্স সাবান কেনার ক্ষমতা বাবার না থাকলেও কোনো কোনো জেলেবধূ আমাদের পুকুরঘাটে লাক্স সাবান নিয়ে আসত। অন্যান্য নারীদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওই বধূটি জালিতে লাক্স সাবান মেখে গা-গতর রগড়াতো। সাধারণ জেলেনারীদের চোখ চকচক করত তখন। ওসব দেখে মাকে কোনোদিন আফসোস করতে শুনিনি। মা সারাজীবন ক্ষারযুক্ত বাংলা সাবান দিয়ে কাপড়চোপড় ধুয়েছে, শরীর মার্জন করেছে। মাকে কোনোদিন মুখে স্নো-পাউডার মাখতে দেখিনি আমি। বাপের ওসব কিনে দেওয়ার শক্তিও ছিল না। তবে মা প্রতি বিকেলে চুল আঁচড়িয়ে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিত। কী অপরূপ যে লাগত তখন মাকে! মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, যখন মায়ের বাপের বাড়িতে যাওয়ার আয়োজন হতো। রসিকচন্দ্র মারা যাওয়ার পর মামাদের মধ্যে বিভক্তি নেমে আসে। রসিকচন্দ্র নিজের মৃত্যুর আগে ছেলেদের বিয়ে করিয়ে গেছেন। মায়ের মা তখন এছেলে ওছেলে করে করে বেঁচে আছেন। মা শুকতারার ভাইয়েরা তখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছেন। বোনদের খোঁজ নেওয়ার বা তাঁদের নাইয়র আনার ইচ্ছা তাঁদের তেমন নেই। কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। মায়ের মেজভাই শোগেন্দ্র। গ্রাম্য-চৌকিদার ছিলেন তিনি। আমার মেজমামা আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। ওঁরই আহ্বানে মা আমার বাপের বাড়িতে যেত বছরে দুই একবার। বাবা কিন্তু মায়ের বাপের বাড়িতে যাওয়া তেমন পছন্দ করত না। মামাদের সঙ্গে বাবার তখন শিথিল সম্পর্ক। বাবা মনে করত, তার সম্বন্ধীরা তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করে না। অন্যান্য বোনজামাইদের সঙ্গে এক কাতারে বিবেচনা করেন তাকে। বাবা সেটা মেনে নিতে পারত না। বাবা ছিল শিক্ষিত- ফাইভ পাস। আর অন্যান্য জামাইরা ছিল নিরক্ষর।
মায়ের আবদারে তাকে বাপের বাড়িতে যেতে দিতে বাবা সম্মত হতো, কিন্তু মায়ের সঙ্গে নিজে যেত না কখনো। মা তার দু’তিনজন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সকালের দিকে বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিত। আগেই বলেছি, আমাদের গাঁ থেকে পাঁচ গ্রাম পরে মামাবাড়ি। হাঁটাপথেই মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ি যেতাম আমরা। তখন আমাদের গাঁয়ে গাড়ি-ঘোড়ার প্রচলন ছিল না। গরুর গাড়ির চলাচল ছিল বটে, কিন্তু গরুগাড়ির ভাড়া গোণার ক্ষমতা বাপের ছিল না।
বাপের বাড়িতে যাওয়ার পথে কোনোদিন মায়ের মুখে ক্লান্তির ছাপ দেখিনি। অদ্ভুত এক অলৌকিক হাসি মায়ের সারা মুখে ছড়িয়ে থাকত সেসময়। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে সন্তানরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে মা কোনো একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, তোরা এইখানে একটু জিরিয়ে নে বাপধনরা।
মায়ের বাপের বাড়িতে ঢুকবার মুখে বিরাট এক কালীবাড়ি। জেলেরা বলে রক্ষাকালীর মন্দির। ওই মন্দিরে বিরাট একটা পাথুরে কালীমূর্তি। করালগ্রাসী, লোলজিহ্বার কালীটি দুদিকে চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জিহ্বা বিগতখানেক বের করা। জিহ্বা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে। পায়ের নিচে ভোলাভালা স্বামী মহাদেব। মহাদেবের চোখে বিস্ময়। কালীর এক হাতে মানুষের রক্তাক্ত কাটা মুণ্ড, আরেক হাতে রক্তরঞ্জিত খড়গ। মা-কালীর চক্ষু বেরিয়ে আসবে আসবে অবস্থা। মা শুকতারা তার সন্তানদের কালীদেবীর সামনে দাঁড় করিয়ে বলত, ‘নমস্কার গর নমস্কার গর। মা-কালী দয়া গইল্যে তোরা বউত্ বড় অইবি পুতরা।’
অন্যান্য সন্তানরা অবাক চোখে মা-কালীকে দেখতে থাকলেও আমি চোখ বন্ধ করে প্রণাম সেরে প্রতিমার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তাম। বড় ভয় লাগত আমার মা-কালীর মূর্তিকে। সেই বালকবেলায় কালীমূর্তি বিষয়ে যে ভয়টা আমার মনে ঢুকেছিল, আজও, এই চৌষট্টি বছর বয়সেও, সেই ভয়টি দূরীভূত হয়নি। মা যে ক’দিন বাপের বাড়িতে থাকত, বড় আনন্দে থাকত। বউদিদের সঙ্গে নানা আলাপে, মায়ের সঙ্গসুখ নিতে নিতে শুকতারার বাপের বাড়িতে থাকার সময় একদিন ফুরিয়ে যেত। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এক সকালে মা আবার রওনা দিত শ্বশুরবাড়ির দিকে। শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছেও বাপের বাড়ির আনন্দ বেশ ক’দিন মায়ের মুখ জুড়ে খেলা করত।
একবার বাপের বাড়ি থেকে ফিরে মা ভীষণ একটা অপমানের মুখোমুখি হলো। এই অপমানের উদ্যোক্তা আমার বাবা যুধিষ্ঠির। পুজো-পার্বণে মামারা আমাদের তেমন করে কোনোদিন জামাকাপড় দিতেন না। সেবার হলো কী, মামাবাড়ি থেকে ফেরার সময় মেজমামা আমাকে একজোড়া শার্ট-প্যান্ট দিলেন। টকটকে লাল হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট। আমাদের বাড়িতে ফিরে মা সোহাগিগলায় বাপকে বলল, দেখ দেখ। তোমার বড়ছেলেকে আমার মেজদা জামাজোড়া দিয়েছে। বাবা বলল, কই দেখি।
মা জামাজোড়াটি বের করে দিলে বাপ তা আমাকে পরাতে চাইল। কিন্তু পরাতে পারল না। আমি ছিলাম একটু নাদুসনুদুস ধরনের। আর জামা-প্যান্ট ছিল ছোট। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পরও যখন বাবা আমাকে জামাজোড়া পরাতে পারল না, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সেদিন বাবা নীরবে ঘরে ঢুকে কেরোসিনের বোতলটা খুঁজে নিয়েছিল। আমার হাত ধরে ঘাটার আগার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এবং জামাজোড়ার ওপর কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মুখে বলেছিল, ‘চেঁডের বালর কাওড়, পুড়ি ছাই অই যাউক।’
মা ভীষণ কেঁদেছিল সেবেলা। তাই বলে বাপের সঙ্গে ঝগড়াতে জড়ায়নি মা। মা কোনোভাবেই ঝগড়াটে ছিল না। কত কত দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করে নিয়েছে মা, কিন্তু কোনোদিন স্বামী বা শাশুড়ির সঙ্গে চোখ তুলে ঝগড়া করেনি। মায়ের হাতে কষ্ট কমানোর একটা অস্ত্র ছিল, সে একান্তে বসে চোখের জল ফেলা। গভীর কষ্ট পেলে বা বাপের হাতে মার খেলে মাথায় ডানহাতটা রেখে কাঁদত মা।
আমার বাবা যুধিষ্ঠির ভীষণ বদরাগী ছিল। কথায় কথায় রেগে যেত বাবা। এমনিতে যুধিষ্ঠির ধীর-স্থির। ন্যায়বানও। সর্দার না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম্যশালিসে বাবাকে খুব মর্যাদা দিত জেলেরা। এই যুধিষ্ঠির যখন ক্ষেপে যেত, নিজের হাত নিজে কামড়াতো। কোনো কারণে মায়ের ওপর ক্ষুব্ধ হলে মুখে সাবধান করত না যুধিষ্ঠির। হাতের কাছে যা পেত, তা দিয়ে মারতে শুরু করত মাকে এবং হয়রান না হওয়া পর্যন্ত মারা থামাত না। মায়ের মুখ দিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য বের হতো না তখন। শুধু নীরবে অশ্রুপাত করত।
তাই বলে দীর্ঘদিন মা বাপের সঙ্গে কথা বলছে না, তা দেখিনি। একবেলায় কী দুইবেলায় উভয়ের মন কষাকষি কেটে যেত। মা গলা উঁচিয়ে বলত, ‘ভাত দি। খাত খাইতা আইও।’
আধুনিককালের দম্পতির মতো পাশাপাশি বসে মিষ্টি আলাপ করতে দেখিনি মা-বাবাকে। তবে মুখোমুখি বসে কথা বলতে দেখেছি অনেকবার। বাবা-মায়ের সেই আলাপে সংসারের দারিদ্র, সন্তানদের লেখাপড়া, ওদের ভাত-কাপড়ের সমস্যার কথাই থাকত। আমার বালকবয়সে বা তরুণবেলায় এমনকি এই প্রবীণ-বয়সে আমার বারবার মনে হয়েছে এবং মনে হয়- আমার প্রতি মায়ের পক্ষপাতিত্ব ছিল। সংসারের অবস্থার যখন একটু পরিবর্তন হলো, আমার ছোটভাই শশাঙ্ক যখন বাপের সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়া শুরু করল, তখন আমরা দুইবেলা ভালোমন্দ খেতে পেতে লাগলাম। তখন দেখতাম, মা আমার পাতে মাছের ভালো টুকরাটি, বড় তপসে ভাজাটি তুলে দিচ্ছে। আমার জ্বরজারি হলে মায়েরও যেন জ্বরজারি হতো। কী অস্থির তখন মা! সংসারের কাজটাজ ফেলে রেখে আমার শিয়রে বসে কপালে জলপট্টি লাগিয়ে যেত।
মা শুকতারা তার প্রিয়তম পুত্রকে লাথি মারল একদিন। তখন আমার ১১/১২। পড়শি মহিন্দ্রের ছেলেমেয়েগুলো ছিল বেয়াড়া ধরনের। পায়ে পা ঠেকিয়ে ঝগড়া বাধাত। তাদের মা ঝগড়া মিটিয়ে না দিয়ে ঝগড়ায় ফুঁ দিত। ফলে তিলের ঝগড়া তাল হয়ে যেত। এক বিকেলে মহিন্দ্রের ছেলেমেয়েরা আমাকে বেদম পিটাল। মার খেয়ে ঘরে আসার পর মা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকে উঠানে চিৎ করে ফেলে দিল এবং ডান পা দিয়ে আমার গায়ে লাথি মারল কয়েকটা। আর মুখে বলতে লাগল, তুই মর, মর তুই! খারাপ ছেলেমেয়ের সাথে মিশে মিশে নষ্ট হয়ে গেছিস তুই। নষ্টদের হাতে মার খেয়ে আসিস তুই!
আমি তখন কাঁদব কী, বিস্ফারিত চোখে শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলাম। এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক পর মা কাঁদতে বসল। যে সে কান্না নয়, একেবারে বিলাপ ধরে কান্না। বিলাপে বিলাপে মা বলতে থাকল- আমি পাপী, মহাপাপী। মহাপাপী যদি না হই, তাহলে নিজের গর্ভজাত সন্তানকে লাথি মারি কেন? হা ঈশ্বর, এই মুহূর্তে তুমি আমার কাছে যমদূত পাঠাও। আমি আর বাঁচতে চাই না। এই আফসোস, বড়ছেলের গায়ে পা তোলার বেদনা শেষজীবন পর্যন্ত মায়ের মন থেকে যায়নি। তখন আমি সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। এক বিকেলে মায়ের কাছে বসে আছি। উঠানভরা তার নাতি-নাতনিরা। ঘরে ছয় পুত্রের বউয়েরা। মা হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বলল, ‘অপুত, তুঁই আঁরে মাফ গরি দও।’
আমি অবাক চোখে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী জন্য একথা বলছ মা?
মা বলল, ‘তোঁয়ারে একদিন আঁই লাথি মায্যিলাম অপুত। গত চল্লিশ বৎসর আঁই তিলে তিলে কষ্ট পাইর। অপুত, আঁই তো আর বেশিদিন বাঁইচতাম নো। তুঁই আঁরে মাফ গরি দিও- হিয়ান জানিত্ পাইল্যে আঁই শান্তিতে মরিত্ পাইয্যম।’
বহুদিন পরে গলা ছেড়ে কেঁদেছিলাম আমি। মাকে জড়িয়ে ধরেই কেঁদেছিলাম। আমার এই মা-টি যতদিন বাঁচার ততদিন বাঁচেনি। তার পরোপকার প্রবৃত্তি ও কৌতূহলই তাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।
পাড়ার নিকুঞ্জ বহদ্দারের দুই বউ। বড় বউ মারা যাবার পর অন্য এক বয়সী-মেয়েকে বিয়ে করেছিল বহদ্দার। আগের ঘরের ছেলে সুনীল জলদাস। পরের ঘরে সুধাম। একটা সময়ে চোখ বুজল নিকুঞ্জ। সম্পত্তি নিয়ে সুনীল-সুধামে লাঠালাঠি। উভয়েই মারমুখী। সুযোগ পেলে খুনই করে বসে। গোটা পাড়া জুড়ে হট্টগোল। সবাই তামাশা দেখছে, ঝগড়া মিটাতে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না। ঝগড়ার আওয়াজ মায়ের কানে গেল। মা এগিয়ে গেল বিবাদস্থলে। আমার বাপ তখন মারা গেছে, আমি কলেজে, অন্যান্য ছেলেরা যার যার কর্মস্থলে। গিয়েই মা উভয়পক্ষের মাঝখানে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, তোরা ঝগড়া করিস না। এই সময় সুনীলের ছোড়া একটা ইটের টুকরা মায়ের কপালে এসে লাগল। করোটি দাবিয়ে ইটের টুকরাটি বসে গেল। আমি যখন ফিরলাম, মা তখন বেহুঁশ, কপালে ব্যান্ডেজ, সারা শরীর রক্তে ভেজা।
মা এক সময় সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আগের মতো শরীরটা আর তার কব্জায় থাকেনি। বিপুল রক্তক্ষরণের ফলে শুকতারার শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুনীল-সুধাম পায়ে এসে পড়েছিল মায়ের। মাফ চেয়েছিল মায়ের কাছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মিটমাটও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা শুকতারার জীবনের বিনিময়ে। কোনোদিন প্রাণ খুলে হাসতে দেখিনি মাকে। কিন্তু সন্তানদের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য, স্বামীর একটু স্বস্তির জন্য, শাশুড়ির একটু আরামের জন্য অবিরত চেষ্টা করে যেত মা। মা কোনোদিন আমার বাপের বাড়িতে স্বাচ্ছন্দ্য পায়নি। কিন্তু স্বস্তি দিয়ে যদি সন্তানদের মানুষ করা বোঝায়, উঠানভরা নাতি-নাতনিদের হই চই বোঝায়, বউদের সেবাযত্ন বোঝায়, তাহলে শেষজীবনে মা স্বস্তির আনন্দটুকু পেয়েছিল। লিভার সিরোসিসে মা পরলোকে গিয়েছিল।
আমি ব্যক্তিগতভাবে জন্মান্তরে বিশ্বাস করি না। তারপরও আমার যদি কখনো জন্মান্তর হয়, তাহলে আমি আবার শুকতারা নামের নিরক্ষর, সর্বংসহা জেলেনিটির গর্ভে জন্মাতে চাই। জন্মাতেই চাই।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/১৩ মে ২০১৮/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন