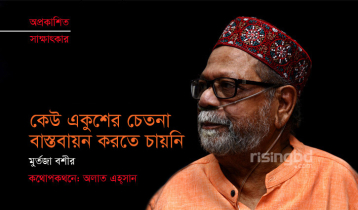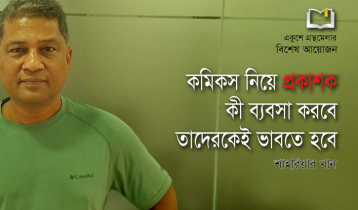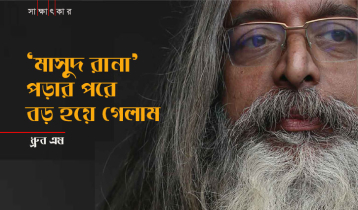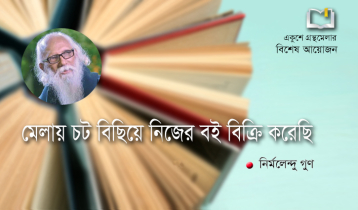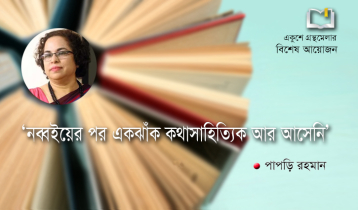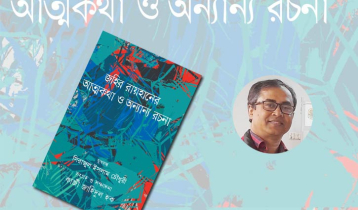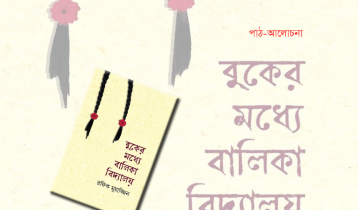আনন্দ আর বিপত্তির বৈশাখ
আহমাদ মোস্তফা কামাল || রাইজিংবিডি.কম

আমার ছোটবেলা কেটেছে গ্রাম আর শহর দু’ জায়গাতেই। দু’মাস এখানে তো দু’মাস ওখানে। আমার সেই সময়কার স্মৃতিও তাই মিশ্র। তবে শহরের স্মৃতির চেয়ে গ্রামের স্মৃতি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। তখন যদিও ঢাকা শহর এতো ঘিঞ্জি ছিল না, পরস্পরের সঙ্গে এতো বিচ্ছিন্নতাও ছিল না, মহল্লার সবাই সবাইকে চিনতো, বাচ্চারা বিকেলে দল বেঁধে খেলতে নামতো গলির ভেতরে, তবু শহরের চেয়ে গ্রাম ছিল আমার প্রিয়। গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তর, বিশাল বাড়ি, পুকুর, নদী, অজস্র গাছপালা আর পশুপাখি- এ সব কিছুর সঙ্গে আমার ছিল দারুণ সখ্য। সেসব অনেক কথা, আজকে লিখতে বসেছি বৈশাখের স্মৃতি, সেটিই বরং লিখি।
গ্রামে বৈশাখ বরণের উৎসব শুরু হতো দু’দিন আগেই, চৈত্রসংক্রান্তির মেলা দিয়ে। মেলা হতো দু’দিন ধরে, বাড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরের আন্ধারমানিক বাজারে। সাজ-সাজ রব পড়ে যেত কয়েক গ্রামজুড়ে। আর সবার মতো আমিও মেলায় যাওয়ার জন্য বায়না ধরতাম, কিন্তু দু’দিন যাওয়ার অনুমতি মিলতো না, যেতে পারতাম একদিন; বড়দের সঙ্গে। আমাদের যৌথ-পরিবারে তখন অনেক ভাইবোন, বিভিন্ন বয়সের। হাই স্কুলে যারা পড়ে তারাই বড়, তাদের হাত ধরে যেতে হতো। সারাবছর ধরে মাটির ব্যাংকে পয়সা জমাতাম সেই মেলার জন্য, যাওয়ার সময় বাবার কাছ থেকে পাওয়া যেত পাঁচ টাকা, মায়ের কাছে দুই টাকা, স্কুলপড়ুয়া বড় ভাইয়ের কাছে এক টাকা, আর নিজের জমানো গোটাপাঁচেক। রীতিমতো বিশাল বড়লোক বনে যেতাম এক মুহূর্তে। পকেট ‘ভরতি’ টাকা নিয়ে মেলায় যেতাম। গিয়ে চোখে ধাঁধা লাগতো। এতো মানুষ, এতো রং-বেরঙের জিনিসপত্র, খেলনা, খাবার, আর এতো বড় মেলা! মনে হতো এতো বড় মেলা পৃথিবীর আর কোথাও হয় না! বড়রা ছোটদের একটা জায়গা চিনিয়ে দিয়ে বলতো, হারিয়ে গেলে কাউকে জিজ্ঞেস করে এখানে এসে দাঁড়াবে। তারপর ছেড়ে দিতো। আর আমরা ‘স্বাধীনভাবে’ ঘুরে ঘুরে মেলা দেখতাম। নানারকম খেলনার ছড়াছড়ি, অনেক রঙের অনেক ঢঙের ঘুড়ি, রং-বেরঙের ছোট ছোট মূর্তি, চিনির সন্দেশ, কদমা, মুড়ালি- কত কত লোভনীয় খাবার ছড়িয়ে আছে, আহ! খাবার দোকানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় ছিল মিষ্টির দোকান। বাজারের চেনা ময়রারাই মিষ্টির পসরা সাজিয়ে বসতেন। হরেক রকমের মিষ্টি। রসগোল্লা, কালোজাম, চমচম, লালমোহন, পান্তুয়া, আমৃত্তি এইসব আরো কতো কি! লোভে জিভে জল এসে যেত বটে কিন্তু মিষ্টি খেলে খেলনা কেনার টাকায় টান পড়ে যাবে বলে লোভ সংবরণ করতে হতো। অবশ্য একেবারেই যে খালিমুখে ফিরতাম তা নয়। দোকানিরা যে চেনা, আর এটা মেলা, বছরের এক বিশেষ উৎসব, তারা কি আর আমাদের খালিমুখে ফিরতে দেবেন? ‘আসো দাদারা, একটা মিষ্টি খায়া যাও’- বলে আদর করে বসাতেন, তারপর যার যার পছন্দের মিষ্টি এনে দিতেন। বড় মায়া ছিল তাদের, বড় যত্ন। এখনো মনে পড়ে, কখনো হাতের মধ্যে মিষ্টি দিতেন না তারা। টিনের পিরিচে একটা চামচসহ এনে দিতেন মিষ্টি, সঙ্গে এক গ্লাস পানি। কোনোদিন আমাদের কাছ থেকে পয়সা নেননি তারা, এমনিতেই খাওয়াতেন। যদিও বিনা পয়সায় কিছু খাওয়া বা নেয়া নিষেধ ছিল আমাদের, কিন্তু মেলায় গিয়ে ওসব নিষেধাজ্ঞা কে মানে? খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে শুরু হতো সম্পদ সংগ্রহের কাজ, মানে খেলনা কেনা। ঘুড়ি কেনা ছিল অনিবার্য। বাড়িতেও ঘুড়ি বানানো হতো বটে, বড় ভাইয়েরা বানাতো, রাখালরাও বানাতো, কিন্তু সেগুলো সাধারণ কাগজের সাদামাটা ঘুড়ি। মেলার ঘুড়িগুলো তো তা নয়, কী সুন্দর রঙিন কাগজ, আর কতো কতো রং! খেলনা লঞ্চ ছিল আরেক পছন্দের জিনিস। ছোট্ট আকার, ভেতরে একটা অতি ছোট ‘ট্যাংক’, তার মধ্যে একটা সলতে বসানো। ট্যাংকে কেরোসিন ভরে সলতেতে আগুন ধরিয়ে পানিতে ছেড়ে দিলে বেশ শব্দ তুলে সেগুলো চলতে শুরু করতো। কী যে আনন্দ পেতাম! তো, এইসব হরেক রকমের খেলনা কিনে বাড়ি ফিরে মেলায় যেতে না-পারা বোনদের কাছে কতো যে সত্যি-মিথ্যে রঙিন গল্প ফাঁদতাম, তার ইয়ত্তা নেই। তারপর শুরু হতো ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। কাটাকুটি খেলা আমরা খেলতাম না, আমাদের নাটাইও ছিল না, নিজের ঘুড়িকে কে কতো উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই ছিল প্রতিযোগিতার বিষয়। এবং আমার কাছে পরমাশ্চর্যের বিষয় ছিল, ঘুড়ি ওড়ানোর সময় বাবা এসে হাজির হতেন। উৎসাহ দিতেন, কখনো কখনো নিজেও ওড়াতেন। আশ্চর্য, কারণ, বাবা ছিলেন সংসার-উদাসীন মানুষ। জগতের কোনো ব্যাপারেই কোনো খোঁজ রাখতেন না, সব কিছুর দেখভাল করতেন আমার মা। আমাদের ছোটবেলায় বাবারা ছিলেন দূরের মানুষ, শ্রদ্ধা আর ভয় যুগপৎ কাজ করতো, এমনকি সারা বছরেও তেমন একটা কথা হতো না। সেই বাবা এসে ঘুড়ি ওড়ালে অবাক হবো না?
ওই একটা দিন যেন সারা বছরের সবচেয়ে আনন্দময় দিন ছিল। দিনটা পার হয়ে গেলে মনটা হুহু করে উঠতো, শুরু হতো আবার এক বছরের অপেক্ষা। আর দু’দিনের যে-দিনটাতে যেতে পারতাম না, সেদিন দিনমান দাঁড়িয়ে থাকতাম বাহির-বাড়ির আঙিনায়! কতো মানুষ যাচ্ছে! কোথায় যাচ্ছ? মেলায়। আমাকে নেবে? দিনটা পার হলে এক ধরনের স্বস্তিও মিলতো তখন- মেলাও নেই, আমার না যেতে পারার কষ্টও নেই।
এই মেলার রেশ সহজে কাটতো না। যতদিন খেলনার আয়ু, ততদিনই মেলার রেশ। উৎসবের শেষে যেমন একটা বিষাদ আর অবসাদ নেমে আসে, তেমনটি কখনো ঘটতে দেখিনি। পয়লা বৈশাখ থেকেই বাজারের দোকানগুলোতে শুরু হয়ে যেত হালখাতার উৎসব। হালখাতার ব্যাপারটা অবশ্য বুঝতাম না তখন, তবে দোকানগুলোর সাজসজ্জা বেশ চোখে পড়তো। সাজসজ্জা বলতে রঙিন কাগজ কেটে কেটে সাজানো। দোকানিরা ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেন, লোকজন যথাসম্ভব সেজেগুজে হাজির হতো, চলতো গল্পগুজব, হাসি-তামাশা। এই উৎসব এক দিনে শেষ হতো না, চলতো সপ্তাহজুড়ে, বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে। কারণ সব দোকানে একই দিনে হালখাতা হলে হ-য-ব-র-ল লেগে যাওয়ার কথা। নিমন্ত্রিত অতিথিরা ক’বার খাবে? একটু বড় হওয়ার পর যখন হালখাতার মানে বুঝেছি, তখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। দোকান থাকবে আর সেখানে বাকিতে জিনিস কিনবে না লোকেরা, তাই কি হয়? দোকানিরা সেইসব বাকির হিসাব একটা খাতায় লিখে রাখতেন। হালখাতার মানে হলো- ওই দিন দেনাদাররা তাদের বাকি পরিশোধ করবেন আর দোকানিরা পুরনো খাতা সরিয়ে নতুন বছরে নতুন খাতায় নতুন হিসাব খুলবেন। তবে বাকির টাকা ফেরত চাওয়া তো একটু ইয়ে, তাই অমন একটা উৎসবের আয়োজন করে গ্রাহকের কাছ থেকে বাকি আদায় করতেন তারা। যেন বাকি আদায়টা মূল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য নববর্ষকে উপলক্ষ্য করে সারা বছরের নিয়মিত ক্রেতাদের একদিন একটু ভালো-মন্দ খাওয়ানো! কী সুন্দর এই আড়ালটুকু, কী অপরূপ সৌজন্যে ভরা! এই উৎসবটি শহরে খুব একটা হতে দেখিনি। অবশ্য শুনেছি পুরনো ঢাকায় খুব জাঁকজমক করে উৎসবটি হতো। আমরা তো পুরনো ঢাকায় থাকতাম না, তাই দেখাও হয়নি।
বৈশাখ যে শুধু এই উৎসব নিয়ে আসতো, তা নয়। আনতো বিপত্তিও। যেমন খরা। তখন দীর্ঘস্থায়ী খরা হতো, প্রায় তিন-চার মাসব্যাপী। ফসলের মাঠগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যেত, ধানগাছের পাতাগুলো লালচে হয়ে যেত, পুকুরে-খালে-বিলে-নদীতে পানি শুকিয়ে যেত। তখনও দেশে শ্যালো পাম্পের প্রচলন হয়নি, সেচের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে বৃষ্টির জন্য কাতর অপেক্ষা, প্রার্থনা, বৃষ্টির নামাজ, পূজা, মাজারে পানি বা দুধ ঢালা, কত কি যে করতো লোকজন! মানুষ, গাছ আর অন্যান্য প্রাণীরা যেন হাঁপিয়ে উঠতো। তারপর একদিন আকাশ কালো করে আসতো কালবৈশাখী ঝড়। সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টি। শিলাবৃষ্টিও হতো কখনো কখনো। তখন ঝড়ও হতো ব্যাপক মাত্রায়। আমরা যদিও আম কুড়ানো আর ‘শিল’ খাওয়ার আনন্দে ভাসতাম, ওদিকে গরিব পাড়ার ঘরগুলো ঝড়ের তোপে ভেঙে পড়তো। ও পাড়ায় টিনের ঘর প্রায় ছিলোই না, দালান তো দূরের কথা, শন দিয়ে ছাউনি তৈরি করে পাটখড়ির বেড়া দিয়ে বাঁশের খুঁটি লাগিয়ে কোনোরকমে ঘরগুলো তৈরি করা হতো। ওরকম প্রমত্ত ঝড়ের কাছে ওই পলকা ঘর টেকে কীভাবে? ঝড় শেষ হলে আমরা দেখতে যেতাম- কার কার ঘর পড়লো! তাদের কোনো উৎসব ছিল না, ছিল না আনন্দ। তিন বেলা দূরের কথা, দু’বেলার খাবারই জোগাড় করতে পারতো না তারা। সর্বত্র ছিল অভাবের অমোচনীয় চিহ্ন। বেঁচে থাকাটাই ছিল তাদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তারপর বিরাট এক দুর্যোগ হিসেবে হাজির হতো কালবৈশাখী, ভেঙে দিতো তাদের ঠুনকো ঘরগুলো। ঘরহীন মানুষগুলোর শূন্য চোখের ভাষা পড়ার মতো চোখ বা মন কোনোটাই আমাদের তখন ছিল না। আমরা যে ছোট ছিলাম! এখনো কি সেই চোখ আর মন তৈরি হয়েছে? গৃহহীন-আশ্রয়হীন-ঠিকানাবিহীন অসহায় মানুষদের চোখের ভাষা কি পড়তে শিখেছি? মনে হয় না।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/২২ এপ্রিল ২০১৯/তারা
রাইজিংবিডি.কম
আরো পড়ুন