কাহিনির পর কাহিনিরা ভিড় করে
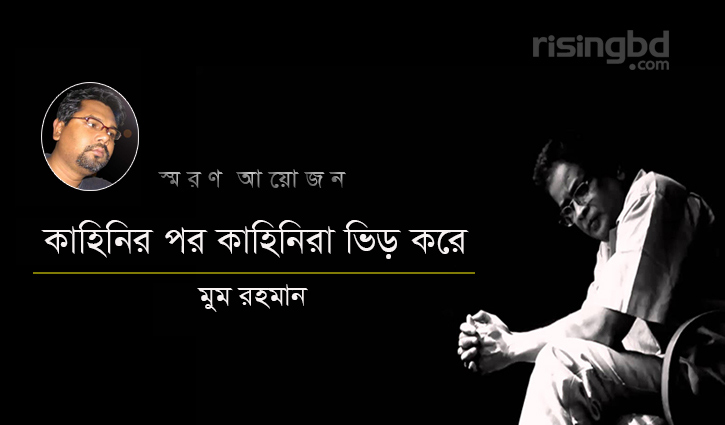
মানুষের জীবনের দিন-রাতগুলোই গল্পে ভরপুর। আদতে মানুষের জীবন মানেই; ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- ছোটগল্প সর্বত্র বিরাজমান। মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি তখনও গল্প বলেছে। বিশ্বাস না-হলে আদিম গুহাচিত্রগুলো দেখুন। প্রাচীন উপকথা, পুরাণ, লোককাহিনি, মহাকাব্য, নীতিকথা- সবখানে গল্প আর গল্পের ছড়াছড়ি। জাতকের গল্প থেকে শুরু করে চসারের ক্যান্টাবেরি টেলস, বোকাচ্চিওর ডেকারম্যান- গল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ‘মার্জিনে মন্তব্যে’ উল্লেখ করেন: ‘গল্প বলার ক্ষেত্রে মানুষ প্রথমে ছোটগল্পই রচনা করেছে। স্মরণ করতে পারি ঈশপের গল্প, জাতকের গল্প।’ তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, সাহিত্যের সবচেয়ে নবীনতম প্রকরণ মাধ্যম হলো ছোটগল্প। বিষয়টা খটকার মনে হয়? আসলে খটকার কিছু নেই। গল্প, আখ্যান, কাহিনি ইত্যাদি যুগে যুগেই বিরাজমান ছিলো। কিন্তু তার শৈল্পিক মান ও আঙ্গিক কাঠামো তৈরি হতে অপেক্ষা করতে হয়েছে বহুকাল। মুখে মুখে বলা গল্প, হাটে-বাজারের গল্প, দৈনন্দিন দিন গুজরানের গল্প কিংবা উপদেশ বা নীতিকথা বিতরণের গল্পের সঙ্গে শিল্পগত ফারাকের কারণেই ছোটগল্প হয়ে উঠেছে সবচেয়ে আধুনিক সাহিত্য মাধ্যম।
আধুনিক ছোটগল্প এলান পো, আন্তত শেখভ, গী দ্য মোঁপাসা’র মতো বিরাট প্রতিভার পরশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যথার্থ বাংলা ছোটগল্প একই সঙ্গে সূচনা, বিস্তার ও পরিণতি পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। ছোটগল্পের সংজ্ঞা, ভাষা, আঙ্গিক, কাঠামো, বিষয়- সব কিছুর মানদণ্ড তিনি একাই তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ‘রবীন্দ্রনাথের মোট ১১৯টি গল্প লেখা হয়েছে ১২৯১ (১৮৮৪) থেকে ১৩৪৮ (১৯৪১) এই মোট সাতান্ন বছর সময়ে।’ (পবিত্র সরকার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি)। এই দীর্ঘ সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্প ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছেন তা পরবর্তীকালের বাংলার ছোটগল্পকারদের জন্যে মানদণ্ড হয়ে আছে। শতাব্দী পেরিয়েও এখনও বাংলা ছোটগল্প মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই এগিয়ে চলছে। বিভূতি, মানিক, তারাশঙ্কর, ওয়ালীউল্লাহ, শাহেদ আলী প্রমুখের যুগ পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ছোটগল্পের একটা নিজস্ব শক্তিশালী বলয় তৈরি হয়েছে। এই বলয়ের অন্যতম কারিগর হুমায়ূন আহমেদ।
সৈয়দ শামসুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হকের পরে লেখালেখিতে এলেও পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে তিনি একই পাটাতনে পরিভ্রমণ করেছেন এবং জনপ্রিয়তায় সকলকে অতিক্রম করেছেন। মূলত ঔপন্যাসিক হিসাবেই হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয় হন। তবে ঔপন্যাসিক, টিভি নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার ইত্যাদি প্রবল জনপ্রিয় পরিচয়ের আড়ালে ছোটগল্পকার হুমায়ূন আহমেদকে আমরা যেন অবহেলাই করেছি। হুমায়ূন আহমেদের প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ ‘নিশিকাব্য’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। অথচ প্রথম গ্রন্থেই অনুধাবন করা গিয়েছিলো যে, হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের সেই গল্পকার যিনি নিজস্ব গল্পভাষা, বিষয়, চরিত্র ও বর্ণনাভঙ্গি আয়ত্ব করেছেন। তিনি একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, মানিক-বিভূতি-তারাশঙ্করের ধারাবাহিকতা গ্রহণ করেন, আবার অন্যদিকে ছোটগল্পের নতুন ভাষ্য-পাঠও নির্মাণ করেন। স্বল্প পরিসরে কেবলমাত্র তার প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থের ১১টি গল্প নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই আমরা দেখতে পাবো বাংলাদেশের ছোটগল্প ধারায় হুমায়ূন আহমেদ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বটে।
‘নিশিকাব্য’ গল্পগ্রন্থের শিরোনাম গল্পটি বিস্ময়কর সরল একটি গল্প। ছোটগল্পের কথিত নাটকীয় প্যাঁচ এতে নেই, নেই আহামরি চমক সৃষ্টিকারী কোন ঘটনা। খুব ঘরোয়া একটি চিত্র এঁকেছেন হুমায়ূন। কিন্তু গল্পের নামকরণের মতোই এ চিত্র কাব্যিক। এক রাতের গল্প এটি। পরিবারের উপার্জনক্ষম সন্তান আনিস ঢাকায় চাকরি করে। চাকরি সূত্রেই তাকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। আনিসের ছোটবোন রুনু’র ভাষায়, ‘ভাইজানের চাকরিটা বাজে। বৎসরে দশটা দিন ছুটি নেই। গত ঈদে পর্যন্ত আসল না।’ সেই আনিস চারমাস পর হুট একরাতে বাড়ি আসে। ময়মনসিংহে কোম্পানির একটা কাজ নিয়ে এলে সকাল সকাল কাজটা শেষ হয়ে যেতেই সে বাড়ি আসে। আবার সকালের ট্রেনেই ফিরতে হবে তাকে। এক রাতের জন্যে আনিসকে কেন্দ্র করে পুরো পরিবারটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই এক রাতের মধ্যেই পুকুরে গোসল করা, পিঠা বানানো, ভাত খাওয়া, মেয়ে টুকুনের একটি দাঁত আবিষ্কার, স্ত্রী পরীর সঙ্গ, বৃদ্ধ বাবা-মার সাক্ষাৎ, ছোট বোনের বিয়ের কথা- ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটে আনিসের। আনিসের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল এই ছোট্ট পরিবারটির সুখ-দুঃখ যথার্থই কাব্যিক দক্ষতায় এঁকেছেন হুমায়ূন। গল্পের শুরুটা হুমায়ূনের প্রিয় প্রসঙ্গ চাঁদ দিয়ে হয়, শেষভাগেও চাঁদ আর জোছনার কথা। চাঁদ আর জোছনা যেন ‘নিশিকাব্য’র নেপথ্য চরিত্র। ‘পরী মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে এসে দেখে চমৎকার জোৎস্না হয়েছে। চিকমিক জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হয়ে যায়।’ এমন মন খারাপ জোৎস্নাতেই কুয়োতলার কাছ দিয়ে শিরীষ গাছের ঘন অন্ধকারে আনন্দের প্রতীক হিসাবে অকস্মাৎ আনিস এসে দাঁড়ায়। পরিবারের সবার ভিড়ে আনিসকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কাছে পায় পরী। পরীর জন্যে একটি শাড়ি এনেছে আনিস। কিন্তু পরী সে শাড়িটি ভাঁজ না-ভেঙে রেখে দেয় আনিসের ছোট বোন রুনুর জন্যে। আর নিজে সে রাতের জন্যে পরে বিয়ের শাড়িটি। বিদায়ের সময় আধো-ঘুম চোখে আনিসের সবার ছোট বোন ঝুনু জানতে চায় ভাবী কেন আজ বিয়ের শাড়ি পরেছে? ‘কিন্তু কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলে।’ চাঁদ আর জোছনার পরিপ্রেক্ষিতে আনিসের বাড়ি আসা আর বিদায় নেয়ার মধ্য দিয়ে একটা চকিত মুহূর্ত নিয়ে রচিত হয়েছে শাশ্বত গল্প ‘নিশিকাব্য’।
নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনের ছোটখাটো ঘটনার চিত্রায়নে হুমায়ূন এক কূশলী। ‘নিশিকাব্য’র মতোই ‘ফেরা’ গল্পেও আসলে তেমন কোন ঘটনাই নেই। একরাতে এক পরিবারের ভাত খাওয়ার সাধারণ চিত্র। এই পরিবারটি ভালো মতো খেতে পায় না। জরী, পরী, দিপুকে নিয়ে হাসিনার সংসার। জরী প্রতিদিন এক জিনিস দিয়ে ভাত খেতে চায় না, একটা ডিম ভাজি হলেও সে খুশি, তার সাথে ছোট ভাই দিপুও খেতে চায় না। ভাত নিয়ে রাগ করে। অন্যদিকে অসুস্থ পরী মরিচ দিয়ে হলেও একটু ভাত খেতে চায়। কিন্তু তাকে দুধ দেয়া হয়। এরমধ্যে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দিপুর বাবা সুখবর নিয়ে আসে, তার বেতন বেড়েছে চল্লিশ টাকা। সেই খুশিতে সে একটি মাছ নিয়ে এসেছে।
‘ফেরা’ গল্পে বাড়ির গৃহকর্তা বেশ রাত্রিতে একটি বড় রুইমাছ নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দারিদ্র্য-জর্জর নিম্নবিত্ত এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছেই রাতটি আনন্দময় হয়ে ওঠে। এই আনন্দময় অনুভবের রূপায়ন ঘটে গৃহকর্তী হাসিনার দৃষ্টিকোণ থেকে:
‘বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জোছনা উঠেছে। বৃষ্টিভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জোছনা। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকেই। অকারণেই তার চোখে জল এসে যায়।’
নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে একটিমাত্র রুইমাছ আনন্দধারা বইয়ে দেয়, এক মুহূর্তে দারিদ্র্য ও বেদনা কাটিয়ে জোছনার আলো প্রকটিত হয়ে ওঠে। একটু আগেও হাসিনার কাছে অভাব জর্জরিত যে জীবন বিষাদময় ছিলো সে হাসিনা এখন চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে প্রকৃতির এ এক নিদারুণ বন্ধন। গল্পগুচ্ছ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি ‘মানব জীবন বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত’- মন্তব্যটি এ গল্পের সাথেও মিলে যায়।
‘শ্যামল ছায়া’ শিরোনামে হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প, উপন্যাস এবং চলচ্চিত্রও আছে। কিন্তু শিরোনাম একই হলেও একটির সঙ্গে আরেকটির কোন সংযোগ নেই। মাতৃস্নেহের অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হুমায়ূন আহমেদের এই গল্পটিতে। ‘শ্যামল ছায়া’ গল্পে মূর্খ বাবা-মার ছেলে মজিদ এমএ পাস করে। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই ট্রেড ইউনিয়ন, মৎস সমবায় সমিতির মিটিং বসে। শিখা নামে একটি মেয়েও আসে। মজিদের মা রহিমা কল্পনা করে শিখার সঙ্গে ছেলের বিয়ে হবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মজিদ ক্র্যাচে ভর দিয়ে বাড়ি ফেরে, শিখার বিয়ে হয়ে গেছে। ‘স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য’ কিন্তু মজিদের মতো করে রহিমা ভাবতে পারেনি। জীবন তার সুবিশাল বাহু তার দিকে প্রসারিত করেনি। রাতে তার ঘুম হয় না। ছেলের জন্য ভাবেন। ‘শেষ রাতে যখন চাঁদ ডুবে গিয়ে নক্ষত্রের আলোয় চারদিক অন্য রকম হয় তখন সে চুপিচুপি মজিদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা গলায় ডেকে ওঠে: ‘ও মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া। সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মজিদের ঘুম ভাঙে না।’ দেশ-মাতৃকার জন্যে যুদ্ধ করে পা আর প্রেমিকা খোয়ায় মজিদ। কিন্তু মজিদের মা পুত্রের এই ক্ষতি মেনে নিতে পারে না। এই গল্পেও শেষ রাত, ডুবে যাওয়া চাঁদ, নক্ষত্রের আলো যেন চরিত্রের সহচর হয়ে ওঠে। প্রকৃতি ঘনিষ্ঠতা হুমায়ূনের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
মুক্তিযুদ্ধ শুধু লক্ষ প্রাণ হারানোর গল্প নয়, বহু ভালবাসার মৃত্যুরও গল্প। ‘নন্দিনী’ গল্পে তেমনি এক ভালবাসা হননের চিত্র ফুটে উঠেছে। হিন্দু তরুণী নন্দিনীকে জোর করে বিয়ে করেছিলো দালাল আজিজ খাঁ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আজিজ খাঁ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। কিন্তু নন্দিনীর যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে না। সে বৃদ্ধ শ্বশুর আর এই পুরনো ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকে। এককালে যারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো, মজিদ তাদের একজন। সে নন্দিনীর আরেক অনুরক্তকে নিয়ে আসে নদী পারের পুরনো বাড়িতে। ক্ষুব্ধভাবে জানায়, আজিজ খাঁর বাড়িতে নন্দিনীর পড়ে থাকা তার সহ্য হয় না। এমনকি নন্দিনীকে বিয়েও করতে চায় সে। কিন্তু নন্দিনী এসব শোনে না। তবু বারবার নন্দিনীর কাছে ফিরে আসে মজিদ। অন্তর্লীন বেদনার বুনোটে গেঁথে তোলা মধুর এক উপাখ্যান ‘নন্দিনী’। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নতর কিছু ছোটগল্প আমরা পেয়েছি হুমায়ূন আহমেদের লেখনিতেই।
পৃথিবীর সব প্রেম সফল হয় না, সব প্রেমিক সাহসী হয় না। এমনি এক ভীরু প্রেমিকের গল্প ‘একজন ক্রীতদাস’। পারুলকে ভালবেসেছিলো গল্পকথক। কিন্তু পারুলের সাথে বিয়ে হয়নি। এ জন্য তার আর্থিক দুর্দশাই দায়ী। পারুল যোগ্য পাত্রকে বিয়ে করে সুখে আছে। আর গল্পের ক্রীতদাস ক্রমাগত ব্যবসায় ব্যর্থ হতে থাকে, ব্যক্তি জীবনেও পারুলের কাছে প্রত্যাখ্যানের গ্লানিতে জর্জরিত সে। ভীতু বলেই তার আর আত্মহত্যা করা হয় না। নিজেকে ক্রমশ সে এতো বদলে ফেলে যাতে কোথাও পারুলের সাথে দেখা হয়ে গেলেও তাকে চিনতে না-পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর চোখাচোখি হতে পারুল তাকে আশ্চর্য করুণ চোখে বলে, ‘তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?’ এমনকি পারুলের চোখে পানিও চলে আসে। কথিত ‘ক্রীতদাস’ এর জবানিতে আমরা শুনি: ‘পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করলো। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।’ ভালোবাসা কী কেবল চোখের জলেই লুকানো থাকে! ‘বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়।’ শরৎচন্দ্রীয় এমন ভাবনা হুমায়ূনের একাধিক ছোটগল্পে পাই।
‘শঙ্খমালা’ ও ভালোবাসা না-পাওয়ার গল্প। বেদনা বিধুর এ গল্পে ভালোবাসা, প্রত্যাখান আর ক্ষমার এক অদ্ভূত সম্মিলন দেখতে পাই। পরীকে ভালবাসতো বড় খোকা। কিন্তু পরীকে পায়নি। তাই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে পরিবারের বড় ছেলেটি। বড় ছেলের আত্মহননের বেদনা ভার বুকে নিয়ে বৃদ্ধা মা আর অন্ধ বাবা দিনরাত্রি গুলো পার করে। এমন সময় পরী বাড়ি ফেরে, কোলে তার ফুটফুটে সন্তান। বাবা-মা ছোট ছেলে ছোটনকে পাঠায় পরীকে দেখে আসার জন্য। ছোটন ফিরে এলে বাবা জানতে চায়, পরী কিছু বলেছে কি-না। ছোটন বলে, না। মা বিলাপ করে কাঁদে।
‘এনড্রিন খেয়ে মরা আমার অভিমানী দাদা যে প্রগাঢ় ভালবাসা পরী আপার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তার সবটুকু দিয়ে বাবা আমার মাকে কাছে টানলেন। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন মার কুঞ্চিত কপালে। ফিসফিস করে বললেন, ‘কাঁদে না, কাঁদে না।’
ভালবাসার সেই অপূর্ব দৃশ্যে আমার চোখে জল আসল। আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললুম, ‘পরী আপা, আজ তোমাকে ক্ষমা করেছি।’
বেদনা ও ক্ষমার মিথস্ক্রিয়ায় হুমায়ূন আহমেদ এমন এক অদ্ভুত প্রেমের গল্প সৃষ্টি করেন যেখানে প্রেমিক পুরুষটি না-থেকেও গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে যান। সন্তানের ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে আকড়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতা জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যান পরম মমতায়।
‘অসময়’ গল্পেও কেন্দ্রীয় চরিত্রটি আড়ালে থেকে যায়। এই গল্পের মূল কাঠামোতে মিনু উপস্থিত নয়। অথচ মিনুকে ছাড়া এই গল্পটি কোন মানেই হয় না। মিনুর সরাসরি উপস্থিতি গল্পে নেই। তবু মিনুকেই কেন্দ্র করেই এ গল্প। গল্পকথকের বাড়িতে প্রায় এগার বছর পর এসে হাজির হন হাসু চাচা। তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। গল্পকার তার বাড়িতে থেকেই মেট্রিক পাস করেছিলেন। তার শারীরিক অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে রেখে আসা হয়। গল্পকারের স্ত্রী জরী বলে, হাসু চাচার মিনু নামে একটি মেয়ে ছিলো এটি কখনো তাকে বলা হয়নি। লেখকের ভাষ্য, এটা দরকারি কোনো কথা না।
‘জরী অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ বলল, ‘মাঝে মাঝে তুমি যখন আমাকে খুব আদর করো তখন কিন্তু আমাকে ‘মিনু’ নামে ডাকো।
আমি কোনো জবাব দিলাম না। জরী বলল, ‘হাসু চাচার মেয়েটি কখন মারা গিয়েছিল?’
‘ক্লাস নাইনে পড়ার সময়।’
‘মেয়েটি কেমন ছিল দেখতে?’
আমি জবাব দিলাম। দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে জরী আমার হাত ধরল। ভালোবাসার গাঢ় স্পর্শ। বাইরের অস্পষ্ট আলোয় জরীর মুখ অবিকল সেই বালিকা মিনুর মুখের মতো দেখাতে লাগল। সেই মুখ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।’’
গল্পের শেষে এসে মিনু প্রসঙ্গটি পুরো গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অন্যদিকে মৃত এবং অনুপস্থিত একটা চরিত্র গল্পে কতোটা প্রভাব ফেলতে পারে তা আমরা অনুধাবন করি এই গল্পের মাধ্যমে। মিনু চরিত্রের অবতারণার মাধ্যমে আমরা জরী চরিত্রের মমতাময় দিকটি অবলোকনের সুযোগ পাই। মিলনে নয়, বিরহ আর উদারতায় ভরে ওঠে হুমায়ূনের প্রেমের গল্পগুলো।
ভালোবাসা, প্রত্যাখান, বিরহ, হারানোর বেদনাকে উপচে ওঠে মানবিক ঔদার্যে। তেমনি এক গল্প ‘কল্যাণীয়াসু’। গল্প কথক প্রেটয়াকভ আর্ট গ্যালারিতে প্রিন্সেস তারাকনোভার পেইন্টিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নস্টালজিক হন। তার মনে পড়ে যায় জরীকে। গল্প কথক একজন চিত্রশিল্পী। তিনি জরীকে বিয়ে করে সুখি হতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীকে তীব্র ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী জরী ভালোবাসতো তার শিক্ষককে। অথচ সেই শিক্ষক সাধকের মতোই নির্লিপ্ত। জরীর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে আসলে জরীর প্রতি তার মন নেই। কিন্তু জরী তার দিকেই মন-প্রাণ দিয়ে বসে আছে। কথকের ভাষায়, ‘জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোনো পিছুটান থাকে না। নিজ স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ক্লাস নিতে আসে তাকে কি আর ভালোবাসার শিকলে বাঁধা যায়?’
ভালোবাসার প্রত্যাখানে আহত জরী শেষপর্যন্ত তার স্বামীকেই বিষ খাওয়ানো চেষ্টা করে। কথক বেঁচে যায়। জরীর সঙ্গে তার আর সম্পর্ক থাকে না। সে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু জরীকে ভুলতেও পারে না। সে বলে, ‘আবার হয়তো কোনো এক পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা মনে পড়বে। আবার এরকম লম্বা চিঠি লিখব। কিন্তু সেসব চিঠি কখনো পাঠাব না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আজ কি আর তা পারবে? কেই আর মিছে চেষ্টা।’
কিন্তু ভালোবাসা পাওয়ার চেষ্টা মানুষ করেই যায়। অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতার চেয়েও নিশি শেষে ভালোবাসাই মানুষের আরাধ্য। দিন যাপনের রুঢ়তায় অধিকাংশ সময় মানুষ ব্যর্থ হয় অমোঘ ভালোবাসার স্পর্শ পেতে। তবু চেষ্টাটা নিরন্তর। ‘ভালোবাসার গল্প’ শিরোনামের ছোটগল্পতেও আমরা এমন দেখি। নীলু রঞ্জুকে ভালোবাসে। রঞ্জুর চাকরি নেই। কোনো রকমে ছাত্র পড়িয়ে চলে। নিলুর বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। পাত্রপক্ষ তাকে পছন্দ করে। এদিকে রঞ্জুর সামর্থ নেই নিলুকে নিয়ে সংসার করার। মেজাজি বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকে নিলু। সে ভাবীকে অনুরোধ করে ভাইকে বোঝানোর জন্য যে, এ বিয়ে সে করবে না। কিন্তু ভাবীর কিছু বলার সাহস হয় না। নিলু তীব্র কষ্ট নিয়ে দাদা ভাইয়ের দরজায় ধাক্কা দেয়। গভীর রাতে অবাক হয়ে দাদা জানতে চান কী হয়েছে? নিলু আর কিচ্ছু বলতে পারে না। ‘তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।’ গল্পটি এখানে শেষ হলেও আমরা জানি না এই জল পড়ার শেষ কোথায়। ভালোবাসার মানুষকে না-পাওয়ার বেদনা দৈনন্দিন জীবনের যাতাকলে কতোদিনে প্রশমিত হয় সেই সমীকরণ আমাদের কারো জানা নেই।
সন্তানের প্রতি ভালোবাসার এক বিস্ময়কর স্পর্শকাতর গল্প ‘সৌরভ’। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র আজহার খাঁ সংসারের খরচ চালিয়ে ছেলেমেয়েদের কোনো সখই প্রায় পূরণ করতে পারেন না। বড়ো মেয়ে লিলি একটা জিনিস এনে দেওয়ার জন্যে পিতাকে অনেক দিন ধরেই বলছে। পিতার আয়ের কথা জেনেও মেয়ের এই অহেতুক আব্দার তাকে বিরক্ত করে। অভিমানী মেয়ে একদিন তার জমানো তিনটা দশ টাকার নোট দিয়ে পিতাকে জিনিসটা এনে দেয়ার জন্য বললো। লজ্জা ও হতাশার এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো লিলি যেন তাঁকে লজ্জা দেয়ার জন্যেই তিনটা দশ টাকার নোট দিয়ে জিনিসটা এনে দিতে বললো। তাঁর আরো মনে হলো তিনি কুকুরের জীবন অতিবাহিত করছেন। তখন ঝপ্ ঝপ্ করে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টির ধারা ঝরছে। এক দোকানে গিয়ে মেয়ের আব্দার করা ‘ইভিনিং ইন প্যারিস’ নামের সেন্টের শিশিটা খুঁজে পান, কিন্তু ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দাম দিতে গিয়ে দেখেন তাঁর পকেটে লিলির দেয়া টাকাগুলো নেই, পড়ে গেছে, অন্য পকেটে মাত্র আড়াই টাকা আছে। নির্বিকার দোকানী যথাস্থানে জিনিসটা রেখে দেয়। আজহার খাঁ খুবই ব্যথিত হন। মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে, তার দেয়ার সামর্থ নেই, মেয়ে টাকা জমিয়ে দিয়েছে, সে টাকা তিনি হারিয়ে ফেললেন। উদভ্রান্তের মতো তিনি রাতের রাজপথ বেয়ে ছুটে চলেন। পিতার বেদনার সাথে মিলিয়ে তখন প্রবল বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টিতে ভিজে তিনি বন্ধু রফিকের কাছে টাকা ধার করার জন্যে গেলেন। যেমন করেই হোক মেয়ের জন্যে জিনিসটা কিনতেই হবে। তিনি তখন অনুভব করলেন তাঁর জ্বর এসে গেছে। বন্ধুর সহানুভূতি ও টাকা নিয়ে তিনি দোকানীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে সেন্টের শিশিটা যখন জোগাড় করলেন তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে। রিকশায় করে বাসার কাছে আসতেই তিনি লক্ষ্য করেন হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর লিলির মা তাঁর জন্যে উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রিকশা থেকে নামতে গিয়ে আজহার খাঁ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে শিশিটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। চারদিকে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।
‘তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি তোর শিশিটা ভেঙ্গে গেছে রে। লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, ‘আমার শিশি লাগবে না। তোমার কি হয়েছে বাবা?’
বাবা ঘরে ঢুকলেন। গভীর রাতে তিনি জ্বরে আচ্ছন্ন। হারিকেনের রহস্যময় আলো জ্বেলে উৎকন্ঠিত মেয়ে লিলি আর লিলির মা জেগে আছেন। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ‘আর সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।’
গল্প এখানে শেষ হলেও এই সৌরভ পাঠকের মনে ছড়িয়ে থাকে দীর্ঘকাল। সেন্টের শিশির এই সৌরভ যেন প্রকারান্তরে পিতা ও কন্যার ভালবাসার সৌরভ, দরিদ্র পরিবারে ভালবাসার সৌরভ।
সমালোচক আজহার ইসলাম ‘বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য’ গ্রন্থে, লিখেছেন, ‘সংসারের অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও বাৎসল্যের এই ছোঁয়াটুকু না থাকলে তো পুরো সংসারটিই মিছে হয়ে যায়। হুমায়ুন আহমেদ অদ্ভুত কৌশলে কন্যার প্রতি যেমন পিতার বাৎসল্যের ছবি অঙ্কন করেছেন তেমনি সংসারের ভারে ন্যুব্জ পিতার প্রতিও উৎকন্ঠিত কন্যার, যেন ছেলের প্রতি এক মায়ের, বাৎসল্য সঞ্চার করে মায়া আর মমতার এক অপরূপ ছবি পাঠককে উপহার দিয়েছেন। উল্লেখ্য ‘সৌরভ’ শিরোনামের উপন্যাসের সঙ্গে এ ছোটগল্পের কোন মিল নেই।
‘নিশিকাব্য’ গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই পারিবারিক সুখ-দুঃখ কিংবা ভালোবাসার আনন্দ-বেদনার ছবি। এ গ্রন্থের ‘বান’ গল্পটি গ্রামীণ জীবনের রুঢ় চিত্র। গল্প নয়, বরং এটিকে বলা যায় আকস্মিক দূর্যোগের এক স্থিরচিত্র। রহমান, বাতাসী, তাদের সন্তান কাদের আলী ও পুতি ও রহমানের বৃদ্ধা মা রাতের অন্ধকারে আকস্মিক বন্যার পানির ঢল নামতে থাকলে দিশেহারা হয়ে ওঠে। দ্রুত জিনিসপত্র গোছাতে থাকে। সকালের রেল সড়কের উঁচু জায়গায় যেতে হবে। একসময় বুড়ি কেঁদে ওঠে। তার সাথে রহমানও। ছোটবোন পুতির খুব ইচ্ছা করে দাদার পাশে বসে, কিন্তু দাদাকে ভয় পায়। এ গল্পে সে অর্থে ছোটগল্পের কাহিনি বিস্তার নেই। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার যথাযোগ্য ব্যবহার এখানে দেখা যায়। ‘কুপি ধরাও গো মা, ভেন্দার মত চাইয়া থাইক্য ন।... আরে বেকুব বেটি বুদ্ধি-শুদ্ধি ছটাকটাও নাই।’ দুযোর্গের সময় মানুষের মুখের ভাষা অসংযত হয়ে যায় তার নমুনা এখানে প্রকট। অন্যদিকে হাসু চাচা কলা গাছের ভেলায় এগিয়ে এলে, তাকে বলে, ‘তামুক খাইবেন চাচা?’ গ্রামীণ মানুষের আন্তরিকতার চিত্রটি ফুটে ওঠে এ সংলাপে। একে অপরকে সহায়তার চেষ্টাটি এখানে অকৃত্রিম। অন্যদিকে এই দুর্যোগেও রহমান সাহস রাখে। ছোট বোন পুতির চোখে কান্না, সে নিচু গলায় জানায় তার ভয় করছে। জবাবে রহমানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ় উত্তর, ‘ডর লাগনের কিছু নাই। কাম কর।’ আবার বাতাসী যখন আক্ষেপ করে বলে, ধান-চাল সবই যাচ্ছে তখন সে আবার ধমক দেয়, ‘খবরদার প্যান প্যান করবা না।’
‘নিশিকাব্য’ গল্পগ্রন্থের ১১টি গল্পে আমরা এক মানবিক দরদী কথাকারকে পাই। ‘শ্যামল ছায়া’, ‘নন্দিনী’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক ভালোবাসার গল্প বলেছেন, যে ভালোবাসা হারানো এখানে যুদ্ধের জাগতিক সকল ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বেশিও বেদনার সৃষ্টি করে। না-পাওয়ার বেদনা ঘিরে থাকে ‘কল্যাণীয়াসু’, ‘একজন ক্রীতদাস’, ‘শঙ্খমালা’, ‘ভালবাসার গল্প’ এবং ‘অসময়’ গল্পসমূহে। এর মধ্যে ‘শঙ্খমালা’ ও ‘অসময়’ গল্পে ভালোবাসা যেন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠে। সকল অপ্রাপ্তির পর ভালোবাসার জয় হয় ‘কল্যাণীয়াসু’ গল্পে।
‘নিশিকাব্য’, ‘ফেরা’ আর ‘সৌরভ’ গল্পের মূল সুরটিই পারিবারিক বন্ধনের মাধুর্য। তিনটি গল্পই অভাবগ্রস্থ নিন্মমধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের চিত্র। অবশ্য গল্পত্রয় শেষ পর্যন্ত অভাব-অনটনকে ছাড়িয়ে এক মধুর পারিবারিক বন্ধনকেই তুলে ধরে। দুর্যোগের মাঝে পারিবারিক নিরাপত্তা রক্ষার চিত্রও আমরা পাই ‘বান’ গল্পে। শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা আর পারিবারিক বন্ধনই হয়ে ওঠে হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের অন্যতম প্রণোদনা।
রাইজিংবিডি/ঢাকা/১৮ জুলাই ২০১৯/তারা
রাইজিংবিডি.কম



































