বাঙালির মনে যেন সীমান্ত তৈরি না হয়
জাকির তালুকদার || রাইজিংবিডি.কম
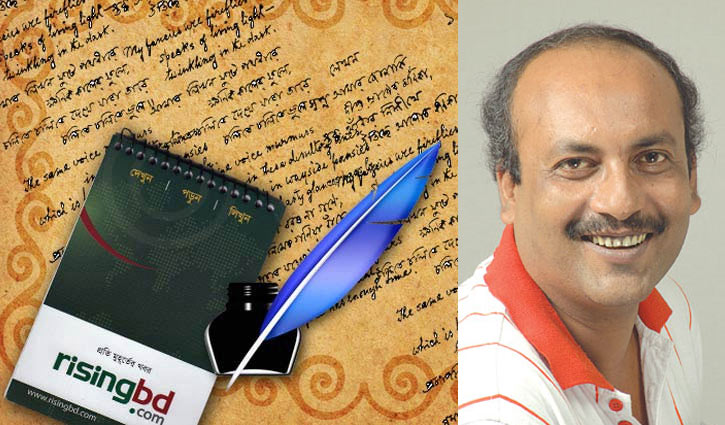
এই রকমই একটি সংকর ও স্বয়ম্ভু জাতির বর্তমান নাম বাঙালি। ব্যক্তি যেমন নিজস্ব অস্তিত্ব এবং কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে সত্তাবান হয়ে থাকে, জাতির ক্ষেত্রেও প্রায় কাছাকাছি কথা প্রযোজ্য। সেই সত্তানির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন তাকে অন্য জাতি থেকে আলাদা করে, তেমনই একই জাতির সকল সদস্যের মধ্যে সম-অস্তিত্বের অনুভূতি এবং সম-পথচলার প্রেরণা জোগায়।
জাতিসত্তা হঠাৎ আরোপিত বা হঠাৎ গড়ে ওঠা কোনো বিষয় নয়। ঐক্য-বিচ্ছেদ-মিলন-ভাঙন এবং পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রপঞ্চ হচ্ছে জাতিসত্তা। কোনো কোনো জাতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে জাতিসত্তা গড়ে উঠতে সময় লেগেছে শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর পর্যন্ত। আমাদের এই বাঙালি জাতিসত্তা বর্তমান জীবিত-প্রজন্মের কাছে আলো-বাতাসের মতো স্বাভাবিক একটি ব্যাপার বলে মনে হলেও এটি গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস, রয়েছে অনেক ভাঙন-মিলন, রয়েছে অনেক গ্রহণ-বর্জনের অমোঘ পথরেখা।
তেরোশত নদীর বয়ে আনা পলির দাক্ষিণ্যে নির্মিত এই ব-দ্বীপে, যা আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত, হাজার বছর আগে পদচারণা করেছে আদি-অস্ট্রেলিয় বা অস্ট্রিক জাতির মানুষরা। পদচারণা করেছে দ্রাবিড় জনজাতির মানুষ। নিগ্রোবটু এই জনজাতির মানুষদের মধ্যে ছিল কোল, ভীল, কোচ, রাজবংশী, কৈবর্ত, ভূমিজ এবং এখন হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন নামের কৌমগোষ্ঠী।
তারা পেয়েছে এই তেরোশত নদীর উদার দাক্ষিণ্য, পেয়েছে পলিমাটির অকৃপণ স্নেহ, পেয়েছে অনার্য সূর্যের আলো ও উত্তাপের অবিরল দানের প্রবাহ, পেয়েছে মৌসুমী বাতাসের সাথে সাথে ঋতুচক্রের অনন্ত বৈচিত্র্য। তাদের কৌমজীবন একের সাথে অপরকে সংযুক্তি দিয়েছে স্বার্থ নয়, ভালোবাসার বন্ধনে। তারা নিজেদের কৌমের মধ্যে অনুভূতির আদান-প্রদান করেছে দেহভাষা এবং মুখ-নিঃসৃত ভাষার মধ্যে। অপর কৌমের সাথে যোগাযোগের জন্য, সমন্বয়ের জন্য পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে উভয় কৌমের মুখের ভাষা এবং উচ্চারণবিধি। এইভাবে কৌমের ভাষা হাজার বছরের পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে বর্তমানের বাংলা ভাষার দিকে। সেই প্রকৃতি-সন্তানরা ফসল ফলিয়েছে মাঠে, তার জন্য উদ্ভাবন করেছে খুরপি এবং লাঙল; নদী থেকে ছেঁকে এনেছে জীবন্ত আমিষ, তার জন্য তৈরি করেছে নানাধরনের জাল-পলো-বড়শি; নিজেদের লজ্জা নিবারণ এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য উদ্ভাবন করেছে নানা ধরনের বস্ত্র, সেই বস্ত্রের উপাদান হিসেবে মাঠে মাঠে ফুটিয়েছে কার্পাসের সমারোহ, নারীদের সৌন্দর্যচর্চার জন্য বীজ পিষে নির্যাস হিসেবে বের করে এনেছে করঞ্জের তেল, সংগ্রহ করে এনেছে গুঞ্জার-মালা, জমি এবং সন্তানের মঙ্গলকামনায় উদ্ভাবন করেছে নানা ব্রতপালা। অনুশীলন করেছে অল্পে সন্তুষ্টির, অভাবে-অনুযোগে-বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর, অতিথিকে অভ্যর্থনার, নিজের ভূমিকে নিজের অস্তিত্বের সাথে সমার্থক ভাবার। বাতাস এসে ধানচাড়ার গায়ে আছড়ে পড়লে যে মূর্ছনার সৃষ্টি হয়, নদীর প্রবহমান জলের সাথে মিলিত হলে যে মূর্ছনার সৃষ্টি হয়, তা থেকে এই মানুষ শিখেছে সংগীত এবং নৃত্যের ছন্দ। তার সাথে সঙ্গত দেবার জন্য তারা উদ্ভাবন করেছে ধামসা-মাদল।
এইসব অর্জনের সাথে মিশেছে অন্যভূমি থেকে আসা নানা জাতির মানুষের নানা ধরনের প্রথা-কথা-চলন। কেউ এসেছে আশ্রয়ের জন্য, কেউ এসেছে অতিথিরূপে, কেউ এসেছে আগ্রাসী লুণ্ঠক হিসেবে। এসেছে বটে, কিন্তু চলে যেতে আর পারেনি। হাজার বছর ধরে এসেছে এইরকম বাইরের মানুষ। কিন্তু তারা আর বাইরের মানুষ হয়ে থাকতে পারেনি। কত রকম মানুষ এসেছে! তাদের সবাকার পূর্বজাতিত্বের কোনো হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষেই। সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষেও, যারা এসেছে। তাই তারা মিশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে পুরোপুরি। নিঃশেষ বিলীন হয়েছে আদি এবং অপরাজেয় এই ভূমির ধর্মের মাঝে। তাই আজকের বাঙালি-সংস্কৃতি এবং বাঙালি-সত্তায় তিনটি প্রবল ধারার সমাবেশ ঘটেছে। অন্যকথায় বলা চলে তিনটি প্রবল ধারার সমাবেশ নিয়ে আজকের বাঙালি জাতিসত্তা। প্রথমটি এই ভূমির আদি-ধর্ম। দ্বিতীয়টি বৈদিক আর্যধর্মের নতুন-পুরাতন নানা সংস্করণ এবং তৃতীয়টি বাঙলায়িত-ইসলাম। তাই বাঙালির সত্তায় রয়েছে আদি ভূমিপুত্রের সহিঞ্চুতা, শ্রমশীলতা, প্রশ্নাতীত ভূমিলগ্নতা, অল্পে সন্তুষ্টি, বাগানে এবং পথের ধারে ফুল ফোটাবার প্রবণতা, অন্যকে সহজে অভ্যর্থনার মনোভঙ্গি, সহাবস্থানের অনুকূল অনাগ্রাসী মানসিকতা, কিন্তু আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা। রয়েছে কোনো কোনো বিষয়ে আর্যসুলভ দৃঢ়তা, অনুসন্ধিৎসা, শুদ্ধকরণের প্রবণতা। রয়েছে সুফি-সহজিয়া ইসলামের উদার সৌভ্রাতৃত্ব, অতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ের প্রতি স্বাভাবিক বৈরাগ্য, নির্বিকারত্ব, সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখার উদার প্রবণতা, স্রষ্টার জমিন-নদী-বাতাস-আকাশ-বৃষ্টি প্রভৃতিকে সর্বজনীন সম্পদ হিসেবে দেখতে শেখার মানসিকতা। এই সবকিছুই বাঙালি-সত্তার অমোচনীয় উপাদান, অপরিহার্য মানস-সম্পদ।
২.
হাজার বছরে অনেকবার খাত বদলেছে তেরোশত নদী। অনেকবার পরিবর্তিত হয়ে গেছে ভূমির বিন্যাস। অনেকবার স্থান ত্যাগ করেছে একাধিক কওমের মানুষ। অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছে স্থাননাম, দেশনাম, রাষ্ট্রনাম, ভূগোলনাম। অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়, পুন্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্র, সমতট এইসব একাধিক নামে অভিহিত হয়েছে বাঙালি হয়ে ওঠা জাতিসত্তাটির ভৌগলিক চৌহদ্দি। বর্ণগত, ধর্মগত, বৃত্তিগত কারণে এই জাতির একাধিক অংশকে বিভিন্ন সময়ে বৃহৎ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির বিন্যাস স্থিরিকৃত হয়েছে ১৯৪৭ সালে। ঘটনাক্রমে তখন এই পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে বাঙালি জাতির যে অংশটির বসবাস, তারা ছিলেন প্রধানত কৃষিজীবী, কেতাবি শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা, প্রাতিষ্ঠানিকতার সাথে পরিচয়হীন, ক্ষমতার বলয় থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী, রাজনৈতিক পাশাখেলায় সবচেয়ে অপারদর্শী, কুল-কৌলিণ্যহীন আতরাফ গোত্রের মুসলমান। তাদের সাথে কিছুসংখ্যক নমঃশূদ্র হিন্দু। বর্ণগর্বী, শিক্ষাগর্বী, চাকরিগর্বী, ধনগর্বী, আভিজাত্যগর্বী, বংশগর্বী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ নামের ভাগীরথী তীরের ভূখণ্ডটি।
হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে উঠলেও সেই জাতিসত্তা বিষয়ে এই ভূখণ্ডের মানুষকে প্রথম সক্রিয় সচেতনা দেখাতে হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে। তার আগে, সেই হাজার বছর আগে একবারই মাত্র এ দেশের ভূমিপুত্রদের নিজেদের অধিকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে লড়তে হয়েছিল। সেই ৯৮০ থেকে ১০১৭ সাল অব্দি ৩৭ বছরই কেবল আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের ভূমির শাসনযন্ত্র নিজেদের হাতে ধরে রাখার জন্য লড়াই চালিয়েছিল। তবে সে লড়াই যতটা না ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার, তার চাইতে বেশি ছিল ভূমি এবং অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে। তারপর থেকে ইংরেজ আগ্রাসনের আগ পর্যন্ত বাঙালিকে নিজের জাতিসত্তা নিয়ে স্পর্শকাতরতায় ভুগতে হয়নি। রাজশক্তি পরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্বে এভাবে কখনো নিজের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে পড়তে দেখেনি বাঙালি। তার কারণ হচ্ছে, বাঙালির ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ। স্বয়ংসম্পূর্ণতার চাইতে সার্বভৌম আর কী হতে পারে! বাঙালি তাই শত শত বছর ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। তাই তার প্রয়োজন পড়েনি রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদলের দিকে আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকানোর।
ইংরেজরা এ দেশে আগমনের পরে এই গ্রামসমাজের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। ১৮১২ সালে ব্রিটিশ কমন সভার রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের একটি চমৎকার বিবরণ। সেখানে বলা হচ্ছে:
‘গলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হলো কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদি বা পতিত জমির একেকটি অঞ্চল; রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা করপোরেশন বা পৌরগোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক বা সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরনের- প্রধান মণ্ডল, তার উপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থা তদারক করবার ভার, অধিবাসীদের মধ্যকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিশের কাজ দেখে এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে কর-সংগ্রহের কাজ চালায়- ব্যক্তিগত প্রভাব ও গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। আরেকজন চাষের হিসাব রাখে এবং চাষসংক্রান্ত সবকিছু নথিবদ্ধ করে। আছে আরো দুই মণ্ডল। প্রথমজনের কাজ অপরাধীদের সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা। অপরজনের এখতিয়ার গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হলো শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। সীমানাদার- তার কাজ গ্রামের সীমানা রক্ষা করা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্য জলের বিলিব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পূজা-অর্চনা। গুরু মহাশয়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির ওপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন; পঞ্জিকা-ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষ ইত্যাদি। এসব পরিচালক এবং সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা। কিন্তু দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সে ব্যবস্থা এতটা প্রসারিত নয়। সেখানে উপরিকথিত দায়দায়িত্বের কতকগুলো একই ব্যক্তি পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে উপরিকথিত লোক ছাড়াও অনেক বেশি লোক দেখা যায়। এই সরল ধরনের পৌর-শাসনের আওতায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে এই দেশের মানুষ বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে ক্বচিৎ; এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা মারিমড়কে গ্রামগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমনকি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগ-বিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না, গ্রামটি অখণ্ড থাকলেই হলো। কোন শক্তির কাছে তা গেল বা কোন সম্রাটের তা করায়ত্ত হলো এ নিয়ে ভাবে না। গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে।’
ব্রিটিশরা দুইশ’ বছর অসংখ্য ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এই ভূখণ্ডে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ হচ্ছে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ধ্বংস করে দেওয়া। এর ফলেই বাঙালি জাতি সত্যিকারের সার্বভৌমত্ব হারায়। নিজের জাতিসত্তাকে ধ্বংসের মুখে পড়তে দেখে। আর সেই কারণেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়েছে এই বাংলায়। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সমশের গাজীর বিদ্রোহ, সন্দ্বীপের বিদ্রোহ, কৃষক-তন্তুবায়দের আন্দোলন, নীলবিদ্রোহ, মালঙ্গীদের সংগ্রাম, রেশম-চাষীদের বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, যশোর-খুলনার প্রজাবিদ্রোহ, বরিশালের সুবান্দিয়া বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ, টিপু পাগলার নেতৃত্বে পাগলপন্থিদের বিদ্রোহ, ফরাজি বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহসহ অসংখ্য আন্দোলন-সংগ্রামে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে এই বাংলার মাটি। সেগুলো একদিকে যেমন ছিল শস্য এবং ভূমির জন্য সংগ্রাম; আবার একই সাথে ছিল জাতিসত্তার স্পর্শকাতর প্রত্যাঘাতও বটে।
তবে সত্যিকারের সচেতন বাঙালি জাতিসত্তার উদ্বোধক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এই সময়েই বাঙালি সর্বাত্মকভাবে উপলদ্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তার একটি নিজস্ব সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রয়োজন।
৩.
বাংলা ভাষাকে তার উন্মেষলগ্ন থেকেই ব্যাপক বৈরিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বাংলা ভাষা এবং বাঙালি নিজেদের মতো করে সেই বৈরিতার মুখোমুখি হয়েছে, এবং অস্তিত্ব বজায় রেখে বিকশিত হয়েছে। শুরুর দিকে বাংলার প্রতিপক্ষ ছিল সংস্কৃত। যেহেতু সংস্কৃত ছিল রাজভাষা, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ভাষা; তাছাড়া ভদ্রজনের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সাহিত্যের ভাষা তো বটেই। একই সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালিত হতো যে বৈদিক ধর্মানুসারী আর্যদের দ্বারা, তাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষাও ছিল সংস্কৃত। হোম, স্তোত্র, যাগযজ্ঞের ভাষাও সংস্কৃত। ফলে বাংলা ভাষার মতো বাংলা ভাষাভাষী এবং এই ভাষার চর্চাকারীরাও ছিল অচ্ছ্যুৎ, সমাজের প্রান্তবাসী। এই ধর্মীয় কারণেই পালি ভাষাও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বাংলা ভাষার সামনে। কারণ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পালি ভাষাতেই লিখিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সহাবস্থান ছিল প্রাচীন বাংলার রাজসভাতে। বিশেষ করে পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর্য এবং ক্ষত্রিয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের যেমন চেষ্টা করা হচ্ছিল, তেমনই চেষ্টা করা হচ্ছিল সেইসব ধর্মগ্রন্থের ভাষাকেও ছড়িয়ে দেবার। সারস্বত সমাজের অন্তর্র্ভুক্ত হতে হলে এই দুই ভাষার শরণ নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু অদ্ভুত প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছিল উন্মেষলগ্নের বাঙালি এবং বাংলা ভাষা। তাদের হাতে সৃষ্টি হয়েছিল চর্যাপদের মতো ঈর্ষণীয় সাহিত্যকীর্তি। হিন্দুত্ব এবং বৌদ্ধত্বের চাপ বাঙালি প্রতিহত করেছিল সেই ধর্মগুলিকে বাঙালিকরণের মাধ্যমে। বৌদ্ধ ধর্মকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে এনে তান্ত্রিক মহাযান রূপ দিয়েছিল বাঙালি নাথপন্থিরা। আর বৈদিক হিন্দুত্ব? দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কালী, চণ্ডী, সরস্বতী, রাধা, মনসা, শীতলা নামের যেসব দেবীদের নামে পূজা-অর্চনা বাঙালি চালু করেছিল, সেগুলির সাথে বৈদিক ধর্মের কোনো সম্পর্কই নাই। বাংলা ছাড়া অন্য কোনো অঞ্চলের হিন্দুরা এদের চেনেই না।
বিনয় সরকার সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন: ‘এই সকল দেবীরা আসলে সবাই বাঙালী নারী- বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজিত মা বোন, স্ত্রী বা মেয়ে। বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাশক্তি, মানবপ্রীতি ও সৃষ্টিপ্রতিভা এই সকল বাঙালী মেয়েকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে। আবার শিব, কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবতা আসলে বাঙালী পুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা বাঙালীর প্রতি গৃহের বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলে। বাঙালীরা যখন নানা প্রকার স্তবস্তুতি ও অবোধ্য সংস্কৃত মন্তর আওড়াইয়া এই সকল দেবদেবীর পূজা করে, তখন তাহারা বাঙালী ছেলেমেয়েদেরই তারিফ করে।’
নিজের চিরায়ত ও লোকায়ত ধর্মদর্শন দিয়ে বাঙালি যেমন নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, তেমনই রাজকীয় সম্মান মুদ্রা-সহযোগিতা ছাড়াই শত শত বছর ধরে চর্চার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করে এসেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের।
পরবর্তীতে বাংলাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে ফারসি, আরবি এবং তুর্র্কি ভাষার। ফারসি ছিল এই তিনের মধ্যে প্রবলতর প্রতিপক্ষ। ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয়ের পরবর্তী সাতশ’ বছর ফারসি ছিল রাজভাষা, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ভাষা। একথা বলা হয় যে, বাংলার স্বাধীন পাঠান সুলতানরা ছিলেন বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সেই পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট ছিল না একটি ভাষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য। ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় উপাসনার ভাষা হিসেবে আরবি যত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে, যত মক্তব, মাদ্রাসা, ওস্তাদ পেয়েছে, বাংলা ভাষা তার শতাংশও পায়নি কোনোদিন। সেই প্রবল ফারসি ভাষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা জন্ম দিয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তায় ভরপুর পুঁথি সাহিত্যের। সেই বিরুদ্ধ রাজকীয় স্রোতের মুখোমুখি বাংলা ভাষা এগিয়ে যেতে পেরেছে জনগণের মুখের এবং বুকের ভালোবাসাকে অবলম্বন করে।
কিন্তু ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে উর্দুর আগ্রাসন প্রতিরোধে বাঙালি যে অকুতোভয় অটল পর্বতের মতো দাঁড়িয়েছিল, তা ছাপিয়ে গেছে ইতিহাসের সকল অধ্যায়কে। মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের জন্মের সময় এই ভূখণ্ডের বাঙালিরা ইসলাম ধর্মকেই জাতিসত্তার প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সমর্থন করেছিল পাকিস্তানকে। বলা চলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল এই ভূখণ্ডের বাঙালিদের সমর্থনই। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই বাঙালি মুক্ত হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান-মোহ থেকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এই ভূখণ্ডের মানুষ গণতন্ত্রের সাধারণ ও মোটা দাগের সূত্রগুলির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পেরেছিল। সেই সরল তত্ত্ব অনুসারে তাদের ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষাই পাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে-পরে সেই বিষয়টি নিষ্পত্তির আহ্বানও জানানো হয়েছিল বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি অংশের পক্ষ থেকে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে অবাঙালি পাকিস্তানি নেতারা সেই বিবেচনা থেকে সরে এলেন।
রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বাঙালি জাতির মধ্যে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম নেবে, তা বোধহয় চিন্তাও করতে পারেনি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে ছাত্রদের দ্বারা। আরো সুস্পষ্ট করে বললে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা। কিন্তু সেই আন্দোলনে সমবেত হন গ্রাম-শহরের সকল স্তরের মানুষ। কারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষার সাথে অর্থনীতির সম্পর্কটি তখন কিছুটা হলেও পরিষ্কার হতে শুরু করেছে সাধারণ বাঙালির কাছে। জমি চাষ করে, জমি বিক্রি করে, হাল-লাঙল-বলদ বিক্রি করে যে কৃষক তার সন্তানকে পাঠিয়েছে লেখাপড়া শিখতে, বাংলার পরিবর্তে রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের ভাষা উর্দু হলে সেই সন্তানের যে কোনো উচ্চপদ জুটবে না, এটি বুঝতে বেশি সময় লাগেনি বাঙালি কৃষকের। রাষ্ট্রের দলিল-দস্তাবেজের ভাষা বাংলা না হয়ে উর্দু হলে জমিদার-জোতদারের শোষণ এবং তাদের কাছে ক্ষুদ্র কৃষকের জমি হারানোর আশঙ্কা যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে, সেটি নিজেদের জীবনের পূর্ব ইতিহাস থেকেই শিখে নিয়েছিল বাংলার গ্রামের মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্য যে পুরোপুরি চলে যাবে অবাঙালিদের হাতে, সেটি তাদেরকে যুক্তি বা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন পড়েনি। নিজের ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না পেলে বাঙালিদের যে নিজেদের ভোটে অর্জন করা পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, সেটিও বুঝতে সময় লাগেনি সমাজের কোনো স্তরের মানুষেরই।
এইসব সমীকরণ থেকে তৎকালীন বাংলার অধিবাসীরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন, সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে এই উপলদ্ধি যে, জাতি হিসেবে আমরা বাঙালি। আমাদের জাতিসত্তার প্রধানতম উপাদান হচ্ছে আমাদের বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতিসত্তা রক্ষা করতে হলে, বিকশিত করতে হলে, বাঙালির নিজস্ব একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।
৪.
রাষ্ট্রের বাইরে আরেক রাষ্ট্রে রয়েছেন কোটি কোটি বাঙালি। সেটিও বাঙালিরই উপরাষ্ট্র। দুই রাষ্ট্রের মধ্যখানে আছে সীমানা-দেয়াল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সীমান্ত চিরকালই কৃত্রিম, অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। এই ভৌগলিক সীমান্ত আজ বাস্তব হলেও আগামী দিনে বাস্তব না-ও থাকতে পারে। কিন্তু মনের মধ্যে সীমান্তরেখা তৈরি হলে তার কোনো মোচন প্রায় অসম্ভব। তা হবে না। হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস আমাদের সেই আশা জোগায়।
লেখক: কথাসাহিত্যিক
তারা//




































